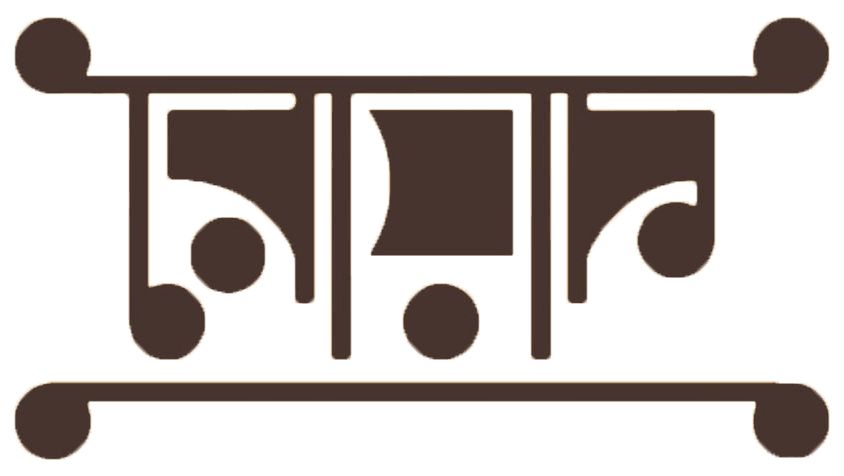চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা- সমালোচনা
ভালো_পড়া
বিদিশা নাথ ভৌমিক
পাঠ প্রতিক্রিয়া
বই: যা ভূতীয় কিছু গল্প যা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো
প্রকাশন: Smell of Books Publication
মূল্য: ৫৯৯
“ভয়ের চেয়ে বড় কোনো কিছু এই পৃথিবীতে আর নেই।”
-লাওজি
প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো ভয়ের গল্পের রুচি পছন্দ প্রত্যেকের আলাদা, কারোর ভালো লাগে তন্ত্র ভিত্তিক হরর,কারোর আবার ক্রিচার হরর,কারোর লাভ ক্র্যাফটিয়ান হরর,কারোর একদম গুড ওল্ড ভয়ের গল্প: আত্মার প্রতিশোধ ,কারোর সাইকোলজিক্যাল হরর। আমার এসব ব্যাপারে গু খাই না গন্ধ বলে,লোহা খাই না শক্ত বলে। মানে সব চলে।
কিন্তু বেশিরভাগ সময় যা ভালো লাগে তা হল আদি অকৃত্রিম ভয়ের গল্প আর তার মধ্যে এক চিমটি রাঁধুনি মশলার মতো সাইকোলজিক্যাল হরর মিশে থাকলে লা জবাব।
2024 এ হাতে এসেচিল ‘যা ভূতীয়’ নামক বইটি। 2025-এর প্রথম মাসে পড়ে শেষ করেছিলাম এক নিঃশ্বাসে ই বলা যায়। রিভিউ সাধারণত সব কিছুর লিখি না ,এটা নিয়ে লিখব ভেবে রাখলেও সময় হয়নি।
বইটির প্রচ্ছদ,বাঁধাই, চেহারা অনবদ্য। একদম আলাদা,খানিকটা রহস্যের। ভিতরে রয়েছে নানা স্বাদের তেরো টি গল্প সাথে গল্পে ব্যবহৃত ভৌতিক বা ফ্যান্টাসি ক্যারেক্টার গুলোর সম্পর্কে নন ফিকশন বা তথ্য ভিত্তিক লেখা।
গল্পের প্রথমে রয়েছে সম্পাদক বর্ষীয়ান লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়- এর একটি অপ্রকাশিত লেখা। ওনার বিশেষত্ব অর্থাৎ হিউমর মেশানো ও চমক দিয়ে লেখা একটু অন্য স্বাদের ভুতের গল্প।যা মজার খানিকটা আর খানিকটা অতিরিক্ত ভালোবাসার ভয়ঙ্কর পরিণতি যুক্ত।
যে গল্প গুলো নিয়ে না বললেই নয় সেগুলো আগে বলব।
নিশি নিয়ে লেখা ‘এই শহরের অলিতে গলিতে’আমার প্রিয় লেখিকা মীনাক্ষী সেনশর্মার লেখা। ওনার নিজস্ব স্টাইলে মনস্তাত্বিক ভয় নিয়ে লেখা এই গল্প পড়তে পড়তে মনে হবে এই শহরে আমাদের পঞ্চেন্দ্রীয়র বাইরে অনবরত হয়ে চলেছে শিকার। নিশি শিকার ধরছে তার নিঃশব্দে। তার ডাক এড়ানো যাবে না,সম্ভব না। যাকে ডাকবে যেতেই হবে।এই ভয়ঙ্কর নিয়তির সামনে মানুষ অসহায়।
‘মেছো ভূত’ গল্পটা একদম অন্য আঙ্গিকে লেখা। কারখানা এলাকায় ষড়যন্ত্র,মালিক পক্ষের অত্যাচার, পরিবেশ দূষণ ,রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপানউতোরকে এসব কে ব্যাক ড্রপ করে এক গা শিরশির করা পরিণতি সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন লেখক রজত শুভ্র কর্মকার।
“লোকায়ত’ গল্পটি পিয়া সরকারের লেখা। শরীরের চামড়া ভেদ করলে আসে রক্ত ,মাংস, চর্বি ,হাড়,শিরা। আর থাকে ভয়। সেই চামড়া ভেদ করে একজন মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলে তার ভয় টা ও যেন নষ্ট হয়ে যায়। শিকার হয় শিকারি।গল্পটা সেটার ই। পরিবেশন অসাধারণ। পড়তে পড়তে রাগ হবে,ভয় লাগবে। হাতের পায়ের আঙ্গুল কুঁকড়ে যাওয়া একটা কষ্ট হবে।
নিখাদ বাঙালির গল্প ‘শাঁকচুন্নি’
বোধহয় এই বইয়ের অন্যতম সেরা গল্প। টাইম লুপ,আলাদা টাইমলাইন, মানুষের অতিলৌকিক কিছুতে রূপান্তর,হোমফোবিয়া এসব কিছু মিলেমিশে তৈরি করেছে একটা অসম্ভব ইউনিভার্স। যে ইউনিভার্সে মিশে গেছে শালু, শিখা। কিছু কিছু জায়গা মনের মধ্যে এমন চাপ সৃষ্টি করে দেবে কিছু দৃশ্য এমন ভাবে এঁকেছেন লেখক যে আপনি পড়ার পর বেশ কিছুদিন ভুলতে পারবেন না। গা গুলিয়ে উঠবে। জানতে পারলাম দেউলা গ্রামের শাঁকচুন্নির মেলা সম্পর্কে। জানি না সত্যি কিনা। তবে সত্যি হলে বোধহয় সেটা দর্শনীয় কিছু একটা হবেই।
সবথেকে ভয়ঙ্কর এবং বিষণ্ণ সুন্দর বোধহয় শেষের অংশ যেখানে এক মানবী পরিণত হয় শাঁকচুন্নিতে।
এরপর বলব দ্বিতীয় সেরা গল্প ‘ঘুল’ নিয়ে। নির্বান রায়ের লেখা।
গ্রামের বাঁশ ঝাড়, পুকুরের পাড়, বৃষ্টির শব্দ,প্রায় লোকশূন্য এলাকা আর একাকীত্ব তৈরি করে নিকষ কালো এক আঁধার। সেই আঁধার শুধু আমাদের চারপাশে আমাদের ভিতরেও। কিছু মানুষ(?) আসলে মানুষ হয় না। জন্ম থেকেই তারা অপবিত্র। তারাই ঘুল। সময় ,পরিস্থিতি তাদের ভিতর থেকে ঘুল কে টেনে এনে বাইরে ফেলে দেয়। যে ঘুল পোকা খায়,মাংস খায় পশু পাখির আবার সুযোগ হলে মানুষেরও।
নারী দেহ ও তো এক ধরনের খাবার তাই নয় কি?শেষে এসে ভয়ে চমকে উঠবেন। চমকে উঠবেন মানুষের ভিতরে লুকিয়ে থাকা নৃশংস মাংসখোর রাক্ষসকে দেখে।
যে গল্পগুলো বেশ ভালো লেগেছে
তা হল ‘খুঁট’ ডাইনি মিথ এর উপর লেখা। সুপর্ণা চ্যাটার্জী ঘোষাল এর লেখা।
‘ব্রহ্মরাক্ষস’ গল্পটি ইতিহাস,পুরানো সময় কে নিয়ে সুন্দরভাবে ভয়ের ছোঁয়া দিয়ে লিখেছেন। প্ৰচলিত ভয়ের গল্পের চেয়ে আলাদা বলতেই হবে। তমোঘ্ন নস্করের লেখা।
‘জলপিশাচ’ গল্পটি বৈশালী দাশগুপ্ত নন্দীর লেখা। একজন পিশাচ কতটা হিংস্র,প্রতিশোধপরায়ণ হতে পারে গল্পটা সেটা নিয়ে। শেষে ভালো মতো একটা চমক আছে সেটা খুব ভালো লেগেছে। গ্রাম বাংলার ভূতের গল্পের স্পর্শ রয়েছে গল্পটাতে।
মোটামুটি লেগেছে ‘আদমখোর হায়না’। বেশ প্রেডিক্টবল। বোঝাই যাচ্ছিল কী হতে চলেছে, ‘খিদে’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে কোনোদিন সাড়া দেননি’ আরও ভালো হতে পারত । ‘স্কন্ধকাটা’ গল্পটা সুন্দর শুরু হয়েছিল শেষ টা বড্ড ম্যাড়মেড়ে লেগেছে।
সব মিলিয়ে জমজমাট একটা ভালো ভয়ের গল্প সংকলন পেলাম অনেকদিন বাদে। 2024 এর অন্যতম ভয়ের গল্পের বই বলা যায়।সহ সম্পাদক অভীক পোদ্দার মশাইকে ও স্মেল অফ বুকসকে অনেক ধন্যবাদ এমন একটা বই আনার জন্য।
এড়িয়ে যেতে বললেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না।
দ্য ম্যাজিশিয়ান : হেরে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া নয়, পর্দা উঠবেই…
— সৌরভ মাহান্তী
ম্যাজিশিয়ান। হাজাররকম ম্যাজিক যার হাতে। ছোটবেলা থেকে ম্যাজিসিয়ান মানেই আমাদের কাছে যারা অন্য গ্রহের এক মানুষ। মানুষ নয় যেন দেবতা। মুহূর্তে শূন্য ঝোলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পায়রা, ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে হাতের পয়সা। আবার ফিরেও আসছে কোন কোন সময়। এই ম্যাজিশিয়ানদের জীবন ঠিক কেমন হয়? কীভাবে বাঁচেন তারা? তাদের জীবনটাও কি এরকম ম্যাজিকের মতোই? এই সমস্ত প্রশ্ন মাথার মধ্যে নানান সময় ঘুরতে থাকে। তুষার কান্তি মাহাতোর দ্য ম্যাজিশিয়ান উপন্যাস পড়লাম।
উপন্যাসটির বিষয়বস্তু খানিকটা এরকমই। ম্যাজিশিয়ানের জীবন। জীবন মানেই শিল্প। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র — দুই দম্পতি, আনন্দ এবং ছবি; অপরদিকে নবীন এবং রত্না।
লেখক দেখাতে চাননি, ঝাঁ চকচকে মঞ্চের আলোয় আলোকিত ম্যাজিশিয়ানকে। তাই তিনি পথ নিয়েছেন অন্য। নবীন আসলে হাতের জাদুকর। উপচে পড়া ভিড় বাসে কিংবা ট্রেনে অনায়াসে পকেট কাটতে পারে সে, এক কথায় পকেটমার। কিন্তু নাহ! পকেটমার বলে তাকে হেয় করা যাচ্ছে না মোটেই। নবীন, নবীন মাস্টার। জীবনে হতে চেয়েছিল অনেক কিছুই, কিন্তু শেষমেষ হতে পারল না তেমন কিছু তাই এই পথ। এই পথে প্রতিনিয়ত নানান বাধা, ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে সে প্রতিনিয়ত পকেট মারে এবং একটা দ্বিধা কাজ করে তার মধ্যে তার কাজ সম্পর্কে তার অতীত সম্পর্কে। জীবনটাকে ঠিকমত গুছিয়ে নেওয়া হলো না তার। লেখক চমৎকারভাবে তার জীবনটাকে বর্ণনা করেছেন। সে আদর্শ প্রেমিক হতে পারেনি, হতে পারিনি আদর্শ পকেটমার কিংবা আদর্শ মানুষ। আর তাই বিবাহিত মহিলা রত্নার সঙ্গে প্রেম করার পরেও সে টুম্পা বৌদির প্রেমে পড়ে। প্রেম নাকি শরীরী মায়াজাল — এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। পকেটমারি করে কারো গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট পেলে সেই সার্টিফিকেট সে ফিরিয়ে দেয়। অপরদিকে মন খুলে কাঁদতে পারেনা সে। এই উপন্যাসের সবচাইতে নিখুঁত চরিত্র এই নবীন মাস্টার। কেন নিখুঁত বললাম তার পরিচয় অবশ্য পরে দেব। অন্যান্য চরিত্র গুলোর কথা বলা যাক।
আনন্দ। আনন্দ জাদুকর। জাদুকর বলতে যা বুঝি আমরা, আনন্দ ঠিক তাই। মেলার মাঠে জাদু দেখায় সে। জাদু দেখায় ট্রেনের কামরায়। তবে বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না সে। এ পথে আরও অনেক নতুন নতুন জাদুকররা এসে যা চকচক মঞ্চ বানিয়ে আলো এবং শব্দের খেলাতে জাদুকে যেন হারিয়ে দেয়। তাদের কাছে জাদু নেই ভেলকি আছে, আর মানুষ সেই সবই দেখছে। আনন্দ এ জন্যই প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে প্রতিদিন। তবে নিজেকে হেরো বলে মেনে নিতে সে রাজি নয়। তার জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠলো চালচুলোহীন ছবিরানী। ছবিরানীকে ঠিক চালচুলাহীন বলা যেতে পারে না, কেননা তার বাপ রয়েছে। কিন্তু সে বাবা মাতাল। তাই এই পথ। পালিয়ে যাওয়ার পথ।
এই উপন্যাসটির অদ্ভুত এক বাস্তবতা হলো — উপন্যাসিক প্রতিটি পাতায় পাতায় জীবনের বাস্তবতা কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আর তাই আনন্দ কিংবা ছবি দুজনের জীবনের তুমুল বাস্তবতা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। জীবন সংগ্রামে কেউ হেরে যেতে রাজি নয়। নিজের সঙ্গে ‘হেরো’ ট্যাগ লাগাতে রাজি নয় কেউ। তাই দাঁতে দাঁত টিপে লড়ে যাওয়া। আনন্দ লড়তে চায়। কিন্তু শেষমেষ জীবন তাকে হারিয়ে দেয়।
উপন্যাসটি পাশাপাশি দুটি চরিত্রকে সামনে রেখে এগিয়েছে — নবীন এবং আনন্দ। একজন পকেটমার এবং একজন জাদুকর। আসলে দুজনেই ম্যাজিশিয়ান। দুজনের মধ্যেই রয়েছে চরম মেধা। হাতের খেলা জানে দুজনেই। এরা দুজন বন্ধু। জীবন তাদের আলাদা করে দিয়েছে। নবীনের ঘর বাঁধা হয়নি, আনন্দের হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হেরে গেছে তারা। আনন্দ অনেক দূরে চলে গেছে। নবীনকে একলা করে। নবীন ফিনিক্স পাখির মত তার জাদু দেখানোর প্রয়াস জারি রেখেছে।
অদেখাকে দেখা অচেনাকে চেনার আনন্দ অনেকখানি। যা পাইনি তা পাওয়ার আনন্দ অনেক খানি। যে আলো সবাই দেখে, তার অন্তরের অন্ধকারকে সবাই দেখেনা। উপন্যাসিক চেষ্টা করেছেন সেই অন্ধকারকে সামনে আনতে। তাই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের কথা এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের যে সমস্ত গৌণ চরিত্র রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। নবীনকে কেন্দ্র করে ঘিরে থাকা তার সাঙ্গোপাঙ্গ, কিংবা ভিখারি স্বপ্নাসুন্দরী, গনেশ কাকা, গবেষক চিত্তপাল, টুম্পা বৌদি, মলয় হাজরা — এরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র নায়ক। কেন স্বতন্ত্র বললাম? একটি উদাহরণ দিই।
গবেষক চিত্ত পাল পকেটমারদের নিয়ে গবেষণা করতে চায় আর সেই সূত্রেই তার পরিচয় নবীন মাস্টারের সঙ্গে। নবীন মাস্টার বিদেশি মালের পরিবর্তে পকেটমারি শিল্পের আপাদমস্তক জানায় তাকে। গবেষকের সঙ্গে তার বাড়ি যায় নবীন মাস্টার। গবেষকের এলাকাকে হাওর বলা হয়। এই হাওরে এসে নবীন যেন নিজেকে খুঁজে পায়। এখানকার পরিবেশ তাকে উতলা করে তোলে। একজন পকেট মারকে হিজল ছায়া বড় অদ্ভুতভাবে একলা এবং নিঃসঙ্গ করে তোলে। হিজল ছায়ায় তার অতীতকে খুঁজে পায় মনে করে সবকিছু ছেড়েছুড়ে একলা কাঁদে। এইখানেই গনেশ কাকা চরিত্রের আবির্ভাব। গণেশ কাকা একজন সন্তান হারা পিতা। সন্তান হারার শোক তার বুকে, এই শোক নিয়ে কাঁদতে থাকে সে। নবীনের ইচ্ছে হয় গণেশ কাকার মত প্রাণ খুলেছে সে যেন কাঁদতে পারে। আর এই গণেশ কাকার শোককে সে যেন বুকের মধ্যে সঙ্গী করে আজীবন ভেসে বেড়ায়।
লেখক বেশ কিছু চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। ম্যাজিক রিয়েলিজম ও সুরাইয়ালিজম এর নানান উপাদান এই উপন্যাসে লুকিয়ে রয়েছে। বউ কথা কও পাখির সঙ্গে নবীন মাস্টারের একাকীত্ব এবং যন্ত্রণাকে তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন।
দা ম্যাজিসিয়ান আসলে একটি ক্লাসিক ধর্মী রচনা। যেখানে উপন্যাসিক জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। যে ছয়টি উপাদান নিয়ে উপন্যাস গড়ে ওঠে, সেই ছয়টি উপাদানের মধ্যে অন্যতম প্লট এবং লেখকের মনস্তত্ত্ব। প্লট নির্মাণের চমৎকার দক্ষতা দেখিয়েছেন লেখক, কিন্তু পাঠক হিসেবে একটি বিষয়ে আমার চোখে লেগেছে তা হল লেখক কাহিনীকে ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন এমন একটি রীতি, যেখানে তিনি আগেকার ঘটনার টুকরো টুকরো অংশ পুনরায় ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটি অবশ্য অমনোযোগী পাঠকের জন্য উপকারী কিন্তু কেউ কেউ বিরক্ত হতে পারেন। উপন্যাসের মধ্যে লেখক এর মনস্তত্ত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। একটি চরিত্র নির্মাণে তিনি অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। উপন্যাসটি আসলে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া নানান অদেখাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দেখিয়ে দেয় নবীন মাস্টার আসলে আমাদেরই চারপাশে ঘুরে ফেরা হেরে যাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। এই মানুষগুলো আমাদের পৃথিবীতে রয়েছে, আমাদের সমাজে রয়েছে। প্রতিযোগিতায় হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যায়নি তাঁরা। তাই নবীনকে সকলে ছেড়ে গেলেও সে নিজের রাস্তা ছাড়েনি সে আমাদের শিখিয়েছে — জীবন সংগ্রাম। আর তাই দ্য ম্যাজিশিয়ান আসলে জীবন সংগ্রামের উপন্যাস। লেখক কে অনেক শুভেচ্ছা রইল অপেক্ষা থাকলো পরবর্তী উপন্যাসের…
বই : দ্য ম্যাজিশিয়ান
লেখক : তুষারকান্তি মাহাতো
জ্যঁর : সামাজিক- ক্ল্যাসিকধর্মী
প্রকাশক : বিভা পাবলিকেশন
মুদ্রিত মূল্য : ২৫৫/-
পুতুল নাচের ইতিকথাঃ একুশ শতকের বিবেক দর্শন
সোহম দত্ত গুপ্ত
“জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেবার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়) । কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে।“(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কেন লিখি’ নামক সংকলন) ।
‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে আমরা জীবনকে যেভাবে দেখতে পাই তার অনেকগুলো মুখ আছে। শশী যেই জীবনের ধারক কুমুদ সেটাকে বয়ে নিয়ে চলে না। আবার, কুসুমের জীবনদর্শন আর সেনদিদির জীবনকে চেনা আলাদা। আমাদের জীবনের এই বৈচিত্রের নীচে এনে দাঁড় করায় গ্রামের আমতলায়। যেখান থেকে ভুতো পড়ে গিয়ে মারা যায়। সিনেমা এবং উপন্যাস দুইই হারুর মৃত্যু দিয়ে শুরু হলেও, শশীর জীবন এবং তার প্রবাহমানতার দোটানার সাথে পরিচিত হতে থাকি সেই আমগাছটির নীচ থেকে। শশী ও ভুতোর বাড়ি থেকে ফেরার পথে সে গাছতলায় একবার থমকে দাঁড়ায়। উপন্যাসের জীবনদর্শনের মুখ অনেকহলেও, ছবিতে আমরা জীবনকে দেখি শশীর চোখ দিয়ে। উপন্যাসের শুরুতেই লেখক শশীর চরিত্রের দুই দিক স্পষ্ট করে দেন। এক তার কল্পনা, ভাবাবেগ দুই, তার সাংসারিক বুদ্ধি এবং ধনসম্পদের প্রতি মমতা। মমতাই বটে, লোভ নয়। শশী তার ভিসিটের টাকা তাগিদা করতে গিয়ে গায়ে হাত তোলে কিন্তু পরক্ষণে তার চোখেমুখে অনুতাপ ও জন্মে। মায়ের মতোই। যদিও এ অনেক পরের কথা।
ছবি এবং উপন্যাস দুইই শুরু হয় মৃত্যু দিয়ে। হারু খুড়োর বাজ পড়া মৃতদেহ দেখতে পায় শশী। দেহ নৌকায় তুলে আনার সময় চালক শশীকে জিজ্ঞেস করে অপঘাতে মরা মুক্তি পাবে কিনা। অর্থাৎ মৃত্যুর পাশাপাশি মুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তাও দোসর হয়ে যায়, যা শশীর জীবনের চিরসত্য। সে মুক্তি মরোণত্তোর আত্মারই হোক কিংবা এই গ্রাম থেকে শশীর। শশীর কাল্পনিক সত্ত্বা তাকে বারবার বিশ্বাস করায় এ গ্রাম ছেড়ে বিলেত গিয়ে ডাক্তারি করতে কিন্তু যা কিছু উপন্যাসের অন্যান্য স্বাধীন চরিত্র তা ছবিতে শশীর জীবনের ঘটনাক্রমের কারণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসে শশীর জীবনে যা কিছু সমস্যা তার প্রভাব অসংলগ্ন বলে মনে হলেও, পরিচালক তার চিত্রনাট্যে ঘটনাগুলিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে তা আর অসংলগ্ন বলে মনে হয় না। তবে, যদি আমরা গভীরে দেখি উপন্যাসেও তা ঠিক অসংলগ্ন নয়। ঘটনাক্রমের বিন্যাস তাকে অসংলগ্ন করে তুলেলেও আমরা বাস্তবেও আদপেই কি বুঝতে পারি কোন ঘটনার ফলে আমাদের জীবন কোন বাঁকটি নেয়!এই ছবিটি পুরোটাই শশী-কেন্দ্রিক যেখানে শশী মূলত থাকে সেন্টার ফ্রেমে। তাকে ঘিরে বসে মানুষ, তার চলনে চলে ক্যামেরা, তার স্তব্ধতায় আমরা দেখি নেকড়ে কে। যা কোথাও গিয়ে সবশেষে শশীর লোন উলফ হয়ে থেকে যাওয়ারও ইঙ্গিত বহন করে।শশীর জীবনে এক প্রধান সমস্যা, সমস্যা বলা ভুল বরং উপজীব্য কুসুমের তার প্রতি তীব্র টান। কুসুমকে আমরা দেখতে পাই পিঠ থেকে, যা কুসুমের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি প্রত্যাখানের দৃঢ়তা, যৌনতা এবং কুসুমের নদীমাফিক প্রবাহমান জীবনকে শুরু থেকেই ঈঙ্গিত করে। কুসুমের সঙ্গে হাঁসের উপস্থিতি আমাদের লিডিয়া আর সোয়ানের গল্পকে মনে করায়, যেখানে ঈশ্বর যে সৌন্দর্যের কাছে উপনীত হতে চান, শশী সেই আকর্ষনবোধ নিয়ে হেলায় খেলা করেছে বহুকাল। কুসুমের চলে যাওয়ার সময় তার মনে হয়, গ্রামে পড়ে থাকার শেষ অবলম্বনটাও হারিয়ে যাচ্ছে। তবু, তপ্ত লোহা ফেলে রাখলে তা ঠান্ডা হয়ে যাবেই। কুসুমকে যদি শুধুমাত্র যৌনতা দিয়ে দেখা হয় তা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজটির জন্য খুবই অনুচিত। সুমন মুখোপাধ্যায় তার ছবিতে এই কথাটি হয়তো আরও স্পষ্ট করে বলেন। উপন্যাস থেকে ছবি হয়ে উঠতে পুতুলনাচের ইতিকথার ন্যারেটিভ স্টাইলে সেই অর্থে পরিবর্তন না হলেও, ঘটনা কমেছে। তবে তা ছবির জন্য জরুরী। নিউ ওয়েভের সময় ফ্রান্সের পরিচালকরা বলতেন সাহিত্যের থেকে সিনেমাকে আলাদা করার কথা। কুমুদ আর মতির পূর্বরাগ বরং উপন্যাসের জন্যই তোলা থাক। তাদের বিবাহিত জীবনের বোহেমিয়ানিজম আমরা শুধু কুমুদের মধ্যে দিয়েই ছবিতে দেখতে পাই। এবং শশীর জীবনে তা আলোর মতোই। একমাত্র কুমুদের সঙ্গে ইন্ট্রো সিনে শশী কুমুদের আলোর কাছে এসে বসে, বাকি সবসময় শশীই যেন বাকিদের কাছে আলো নিয়ে আসে। যেভাবে সেনদিদির বদ্ধ ঘরে ঢুকে শশী জানলা খোলে।যেখানে জীবন বিমুখতা শশীর একমাত্র সঙ্গী, সেখানে শশী জীবনকে শ্রদ্ধা করার কথা বলে। তবুও সেও যেন ধীরে ধীরে মৃত্যু-বিষাদ হারিয়ে ফেলে। সেনদিদির কাঁচের চোখ দিয়ে মন ভোলানোর কথা আমাদের ভাবায় শশীর জীবনের সাথে জীবন-মৃত্যুর শারিরীক যোগ। মন তো কাঁচের চুড়িতে ভোলে। যাদব পন্ডিত এবং তার স্ত্রী এর দেহত্যাগের দিন সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, শশী একমাত্র চলমান। তাকে থামিয়ে রাখে যাদব পন্ডিতের অপমান, হেরো ঠাহরানো। সে চেয়েও আফিমের প্রতিশেধক দিতে পারেনা। পারা- না পারার দ্বৈত চিত্রায়ণ সাররিয়ালিজমের জন্ম দেয়। কুসুম যেখানে সবচেয়ে আধুনিক এবং প্রতিবাদী সত্ত্বা নিয়ে দাঁড়াতো। সেই কুসুমেরও গায়ে আবরণ জড়ায় শেষ অব্দি। শশির কাছে থেকে যায় ধুতি শার্ট আর কুমুদের মতো শহুরে হাওয়া লাগানো কোট। এবং সাইকেল। ভাঙা এরোপ্লেন, সাইকেল, মোটর গাড়ির সময়ের প্রবাহমানতাকে তুলে ধরলেও শশী আটকা পড়ে যায় এই গ্রামেই। বাড়ীর চাবি নিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। গরাদের মতোন। কীসের অপরাধবোধ?কুসুমকে অবহেলা! সেনদিদিকে বাঁচাতে না পারা! নাকি ভুতো? যার ঠিক চিকিৎসা হয়েছিলো কিনা তা নিয়েও সন্দেহ জন্মে শশীর মনে।
দ্বন্দ নিয়েই এগিয়ে যায় শশী। এ গ্রামে না থাকলে তার হয়তো চলবে না। আটকা পড়ে যায় পচা পুকুরে। যেভাবে পড়ে আছি আমরাও। একটা সময়ের পর আমরাও কি হাল ছেড়ে দিই না! মনে হয় না? আর আন্দোলন করে কী হবে! আর প্রতিবাদ করে কী হবে যা হওয়ার তা তো হচ্ছেই। কুসুম যেন এই ভাবনারই উল্টোপিঠ হয়ে দাঁড়ায়। সে শেখায় জীবনে অতো যদি চলে না। কুমুদ যেন শশীর অল্টারইগো। আমাদের দ্বিধা দ্বন্দ, না পেরে ওঠাদের বুঝে ওঠবার পিছনে কুমুদ এবং কুসুমদের প্রয়োজন বড্ডো। এই ছবির আবহের মতোই। আবহ এখানে অনুষঙ্গ নয়, বরং আরেক উপজীব্যই। ছবির চলনকে নিজস্ব মাত্রা দেয় এই ছবির আবহ। যাত্রায় বিবেকের চরিত্র এসে যেমন নীতির কথা বলে, তেমনই শশী-কুসুম-কুমুদ-সেনদিদি সর্বোপরি ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ও জীবননীতি ও তার প্রবাহমানতাকে স্বীকার করার ও শ্রদ্ধা করার কথা বলে চলে। নদীর মতো।
(কৃতজ্ঞতাঃ- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দোল পালিত)
ছবির নামঃ- পুতুলনাচের ইতিকথা
পরিচালকঃ- সুমন মুখোপাধ্যায়