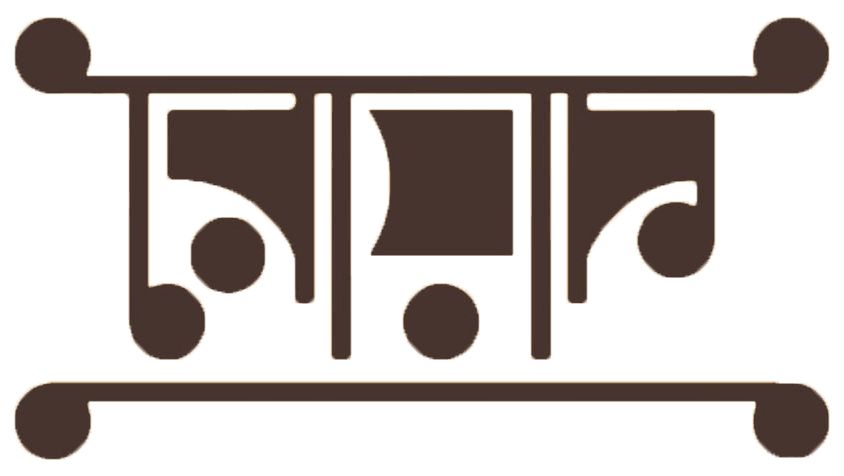চতুর্থ বর্ষ – দ্বিতীয় সংখ্যা – বৈঠক
বহুরূপী বাদল
অংশুমান ভৌমিক
বাদল সরকার আসলে একজন নয়, অনেকজন মানুষ। যাকে বলে ‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার’, তাই। ওঁর যে রূপটা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনায় বসেছি সেটা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাদল সরকারের। বাদলের বর্ণাঢ্য নাট্যজীবনের এই প্রসেনিয়াম পর্বের সবচাইতে মহিমান্বিত অধ্যায়ের আরেকটা নাম দেওয়া যেতে পারে – বহুরূপী অধ্যায়।
বস্তুত এই মুহূর্তে বাদল সরকারের উত্তরাধিকারের যে সামান্য অংশ জনসমক্ষে টিঁকে আছে– থিয়েটারে বা সিনেমায় – তা ওই বহুরূপী অধ্যায়েরই হরেকরকমবা পুনরুৎপাদন। এই সুবাদে যে বাদল সরকারকে আমরা আজও চিনি সেই নাটককার সত্তাটি আদতে বহুরূপীরই অবদান। অন্যান্য বাদলের একটা ঐতিহাসিক ও নান্দনিক গুরুত্ব একদা ছিল। এখন তার ছিটেফোঁটা মাত্র রয়ে গেছে। কথাটা কারুর কারুর পছন্দ নাই হতে পারে, তাও বলে রাখা ভালো যে মূলত রাজনৈতিক বাতাবরণের ভোলবদলের দরুন বাদল-প্রণীত থার্ড থিয়েটার এখন পেল্লায় এক গাড্ডায় আটকে গেছে, এবং আপাতত সেখান থেকে বেরুনোর পথ দেখা যাচ্ছে না।তাই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে বাদলের মাখামাখির পর্বটিকে নিয়ে স্মৃতিকণ্ডূয়ন করা ছাড়া আমাদের হাতে বাদল সরকারের শতবর্ষ উদ্যাপনের আর কোনওফলদায়ক পন্থা নেই।
তথ্যের খাতিরে শুরুতেই বলা থাক যে নয়-নয় করে বাদলের ছটা নাটকের প্রযোজনা করেছেন বহুরূপী। বাদলের নিজের দল শতাব্দী ছাড়া আর কোনও সংস্থা ওঁর এত নাটকের মঞ্চায়ন ঘটাননি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে তারিখে নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে শম্ভু মিত্রর নির্দেশনায় বাদলের ‘বাকি ইতিহাস’ প্রযোজনা করেছিলেন বহুরূপী। সেই শুরু। এর পাঁচ মাসের মাথায়, ৩ অক্টোবরে, ওই নিউ এম্পায়ারেই বাদলের নিজের লেখা নাটক ‘প্রলাপ’ বাদলেরই নির্দেশনায় প্রযোজনা করেছিলেন বহুরূপী। দু দশকের পরম্পরাকে সরিয়ে রেখে সেই প্রথম দলীয় সদস্য নন এমন কাউকে বহুরূপীর প্রযোজনার দায়িত্ব সঁপে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭০-র দশক জুড়ে বাদলের একের পর এক নাটকের প্রযোজনা করে গেছেন বহুরূপী। ১৯৬৯-এ ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ (নির্দেশক হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়), ১৯৭১-তে ‘পাগলা ঘোড়া’ (নির্দেশক শম্ভু মিত্র), ১৯৭৫-এ ‘বাঘ’ (নির্দেশনা তৃপ্তি মিত্র) ও ১৯৭৬-এ ‘যদি আর একবার’ (নির্দেশক তৃপ্তি মিত্র) – বহুরূপী-বাদলের যুগলবন্দিকে এই বিরল উচ্চতায় তুলে দিয়েছিল।
আলোচনার এই পর্যায়ে এ-কথা না বলে নিলে সত্যের অপলাপ হবে যে ১৯৬৫ নাগাদ, ৪০ বছর বয়সে,বহুরূপীর হাত ধরার আগেই নাটককার হিসেবে হাত পেকেছিল বাদলের। সেসব নাটকের কোনওটা – যেমন ‘রাম শ্যাম যদু’ – কলকাতার তৎকালীন নাটকপাড়া হাতিবাগানে মঞ্চস্থও হয়েছিল। কোনওটা – যেমন ‘বড়ো পিসীমা’, ‘সলিউশন এক্স’ – হাতিবাগানে কলকে না পেলেও কলকাতায় ইতিউতি এবং কলকাতার বাইরেও পেয়েছিল। এসব ১৯৬০-৬৩ খ্রিস্টাব্দ কালপর্বের ব্যাপার। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গড়ে তোলা বাদলদের শখের নাটকের দল ‘চক্র’ ছিল এসবের হোতা।
পরে বহুরূপীর সঙ্গে বাদলের বেশ দহরম মহরম তৈরি হয়। ভবানীপুরের একটি ঘরোয়া আসরে বাদলের স্বকৃত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ পাঠ শুনে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই উত্তেজিত হন এবং ঘটনাটি শম্ভু মিত্রর গোচরে আনেন। শমীকেরই তোড়জোড়ে ‘বহুরূপী নাট্যপত্র’-র দ্বাবিংশ সংখ্যা নাটকটা ছেপে বের করে। সেটা ১৯৬৫-র জুলাই মাসের কথা। বাদল তখন কর্মসূত্রে নাইজিরিয়ায় থাকতেন। এরপরপরইবেকবাগান এলাকায় বহুরূপীর ঠিকানাতে বাদলের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। কলকাতায় এলেই প্রবাসে প্রণীত টাটকা সব নাটক পড়ে শোনানোর আখড়া হয়ে ওঠে বহুরূপীর মহড়া ঘর।
‘বাদল সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার গল্পে’ ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন সেদিনের অষ্টাদশী শাঁওলী মিত্র। পিতা শম্ভু মিত্রর জীবনী লিখতে বসে বাদল প্রসঙ্গে শাঁওলীর মনে এসেছে – ‘প্রবাস থেকে ফিরে তখন অনেকগুলি নাটক তিনি ১১এ নাসিরুদ্দিন রোডে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তখনও এ-লেখক শয্যাশায়ী। সে ১৯৬৬-’৬৭-র কথা। বহুরূপী-শুদ্ধ সবাই তাদের বসবার ঘরে। তাকে শুইয়ে দেওয়া হত সেই ঘরের ডিভানটিতে। তার মনে পড়ে ঐভাবে শুয়ে শুয়ে সে শুনেছে, বাকি ইতিহাস, বাঘ, প্রলাপ, সারারাত্তির এমন বেশ কিছু নাটক। তাঁর পড়ার একটা নিজস্ব ধরণ ছিল, যা শম্ভু মিত্র-র ঘরানা বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তো তার থেকে একেবারে পৃথক। কিন্তু ভীষণ আকর্ষণীয়। তাঁর নাটকের রসিকতাগুলো তিনি পাঠে এমনভাবে প্রকাশ করতেন, যে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ত। শম্ভু মিত্র তো খুবই পছন্দ করতেন বাদলবাবুর পড়া।’
মনে রাখতে হবে যে বহুরূপী সে সময়ে খ্যাতির তুঙ্গবিন্দুতে অবস্থান করছেন। ১৯৬৪-তে একের পর এক ‘রাজা অয়দিপাউস’ ও ‘রাজা’ প্রযোজনা করে যে নান্দনিক পরাকাষ্ঠা তাঁরা অর্জন করেছেন তার তুল্য ঘটনা আমাদের উত্তর-ঔপনিবেশিক নাট্যচর্চার আসেনি বললেই চলে। রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায় নিরীক্ষাধর্মিতার শিখর ছুঁয়ে ফেলেছেন তাঁরা। ধ্রুপদি নাট্যনির্মাণের গ্রিক ঘরানাকে আত্তীকরণের একটি সফল উদ্যোগ নিয়েছেন। শম্ভু তখন নয়া ভারতের নয়া নাটককারের খোঁজে আকুল। খানিক অধীর। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগসাজশে বাদলকে পাওয়া কতক মেঘ-না-চাইতে-জলের মতোই দাঁড়িয়েছিল বহুরূপীর অন্দর মহলে। বাদলকে নিমেষে আপন করে নিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র ও তাঁর নির্দেশিত পথে আগুয়ান নাট্যসংস্থা। বহুরূপী হয়ে উঠেছিল বাদলের নাট্যনিরীক্ষার আঁতুড়ঘর। তাঁকে নতুন নাটক লেখার প্রণোদনাও দিয়েছিল। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ার কথা শেষ জীবন অবধি বাদলের মনে ছিল। এ নিয়ে নিজের অগোছালো ও চাঁছাছোলা আত্মজীবনীতে বাদল লিখেছেন –
‘বহুরূপীর’-র রিহার্স্যাল রুমে প্রায়ই আমাকে নাটক পাঠ করতে যেতে হোতো। দামী সব খাদ্যসামগ্রী আসতো, অবাক হয়ে ভেবেছি – এই সবই কি এদের প্রাত্যহিক জলযোগ? পরে অবশ্য বুঝেছি, এ শুধু আমার খাতিরে। ‘বাকি ইতিহাস’, ‘সারারাত্তির’, ‘বাঘ’, ‘রাম শ্যাম যদু’ লেখাপড়া করে অনুমতি নিয়ে নিলো ওরা।
পরে আমার বাড়িতে এসে ওদের একজন এসে প্রস্তাব দিলেন – ওরা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-ও নেবে, যদি আমি শৌভনিকের অভিনয় বন্ধ করে দিই। আমি বললাম – ওরা যতো খারাপই করুক, যতো বিকৃতই করুক নাটকটাকে, গালাগালি দেবো, কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। (‘পুরোনো কাসুন্দি দ্বিতীয় খণ্ড’, ২০০৭ খ্রি, পৃ ৯৯-১০০)
উল্লেখিত চারটে নাটক ছাড়াও বাদলের আরও দুটি নাটকের অনুমতি নিয়েছিলেন বহুরূপী – ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ ও ‘পাগলা ঘোড়া’। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিভা অগ্রবাল ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল জানিয়েছিলেন যে শম্ভু মিত্র ‘বিচিত্রানুষ্ঠান’ শুনেও প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন – ‘এখনও চিঠি আছে ওগুলোর, বহুরূপীকে দেওয়া হল পারমিশন, যদিও শেষ পর্যন্ত করা হয়নি।’
বিদেশি সূত্র থেকে লেখা ‘প্রলাপ’ নাটকটি বহুরূপী থেকে প্রযোজনাও করা হয়েছিল, খোদ নাটককারের নির্দেশনায়। বিশদে পরে আসছি। এক্ষণে এটুকু বলা থাক যে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-ও আদতে বহুরূপীরই করার কথা ছিল। লেখাপড়াও করা ছিল, ডাক মারফত। বহুরূপীর ইতিহাসকার স্বপন মজুমদার লিখে গেছেন ‘এই নাটকটিকে অবলম্বন ক’রেই প্রাচী-প্রতীচী নাট্য সম্মেলনে সমগ্র ভারতবর্ষে বাদল সরকারকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র।’ অস্যার্থ, মোহন রাকেশ, গিরিশ কারনাড প্রমুখের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র নাট্যস্বর হিসেবে বাদলের নামডাকের পেছনে শম্ভু ওরফে বহুরূপীর ভূমিকা ছিল অনুঘটকের। জহুরি চিনেছিলেন জহরত।
কিন্তু১৯৬৬-তে কলকাতায় শম্ভু মিত্রর সাময়িক অনুপস্থিতিতে প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিছু গয়ংগচ্ছ ভাব চলেছিল কিছুকাল।শৌভনিক মাঝখানে ঢুকে পড়ে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ প্রযোজনা করার অনুমতি চাইলে বহুরূপীকে জানিয়ে সায় দিয়ে দেন বাদল। এ নিয়ে বাদল পরে লিখেছিলেন – ‘পরে শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানি না, শম্ভুবাবু ফিরে এসে না কি ওটা বন্ধ করে দিয়েছেন, সুতরাং আটকে রেখে আর কী হবে?’ অবিশ্যি মুক্ত অঙ্গনে শৌভনিকের করা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ একেবারেই বরদাস্ত হয়নি বাদলের। ‘এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা’ – লিখেছিলেন তিনি। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! যে নাটকের ইংরিজি ও মরাঠি তরজমার সূত্রে বাদলের দেশজোড়া নাম হল, ডাক হল, সেই নাটকের প্রথম প্রযোজনা একেবারেই মনঃপূত হল না তাঁর। অথচ গিরিশ কারনাড প্রমুখ নাট্য ভগীরথ এ প্রযোজনা দেখে মাত হয়ে গেলেন। আমরা ফিরি বহুরূপীর প্রযোজনায় বাদলের প্রথম নাটক ‘বাকি ইতিহাস’-এর কথায়।
নিজে অভিনয় না করলেও শম্ভু মিত্র নির্দেশনা দিয়েছিলেন ‘বাকি ইতিহাস’-এর। অভিনয়ে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার রায় সহ বহুরূপীর সকল প্রধান কুশীলব। সংস্থার পক্ষ থেকে ‘বাকি ইতিহাস’-এর প্রযোজনা পুস্তিকায় ভাবিয়ে তোলা এক বিবৃতি বেরিয়েছিল। ১৯৬৭-এ অস্তিবাদী দর্শনের সংকট কীভাবে পেড়ে ফেলেছিল সমকালীন বিশ্বকে, নাড়িয়ে দিয়েছিল বহুরূপীর মতো সমাজসচেতন শিল্পী সম্প্রদায়কে, তারও যেন ইস্তেহার এই বিবৃতি। সাফাই নয়, অজুহাত তো নয়ই, এক নান্দনিক ইস্তেহার। কোন নান্দনিক অবস্থান থেকে ‘বাকি ইতিহাস’ প্রযোজনায় নেমে পড়েছিলেন বহুরূপী তার ব্যাখ্যা মিলছে এতে। এর খানিকটা আমরা পড়ে নিতে পারি।
হঠাৎ একদিন খবর পাই অমুক আত্মহত্যা করেছে। – কেন করেছে? বুঝতে পারিনা। – কিন্তু অস্বস্তি লাগে। – কল্পনা করি। আমাদেরই চরিত্র-অনুযায়ী – হয় আবেগপ্রবণ – নয় লোমহর্ষক – কারণ কল্পনা করি। তবু নিশ্চিত বিশ্বাসের শান্তি পাই না। – কারণ এতো সত্য নয়। তাই, – একদিন রাতের অন্ধকারে হঠাৎ মুখোমুখি হ’তে হয় সেই প্রেতকণ্ঠ প্রশ্নের – কেন বেঁচে আছি!
বিহারে ও বাংলার সীমান্তে দুর্ভিক্ষ – পুরুষ, নারী, শিশু, বিনা অপরাধে শুধু – খেতে পায়নি ব’লে মরছে। – এখনো হিরোশিমার ক্ষত শুকোয়নি তবু ভিয়েৎনামে অজস্র নরনারী ও শিশু ম’রে চলেছে। – দিকে দিকে আণবিক বোমা প্রস্তুত হচ্ছে – কে কতবার পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে তারই অহঙ্কার-দৃপ্ত ঘোষণা – । তবু আমরা নিজের নিজের কোটরের মধ্যে – আমাদের নিজের নিজের না দেখতে চাওয়া, না শুনতে চাওয়া বেঁচে থাকার পরিহাসকে বাঁচা ব’লে প্রতিপন্ন করতে চাই। – কেউ যদি প্রশ্ন করে, – কেন বেঁচে আছো ভাই – তাহলে ক্রুদ্ধ হই। কারণ, তাহলে যে সমস্ত মিথ্যেটা হঠাৎ ধ্ব’সে পড়ে। মুখোমুখি হ’তে হয় সেই উলঙ্গ সত্যের।
তাই আমরা এড়িয়ে থাকি সেই বাকি ইতিহাসটাকে। – মানুষের সেই বাকি ইতিহাসটাকে। – তবু কি পারি – ? এড়িয়ে থাকতে?
একেবারে নয়া আন্দাজের নাটক। থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ডের সঙ্গে কলকাতার ভাবসাব তার আগেই হয়েছে। তবু যেন আলাদা গত এক। সবাই একই রকমভাবে অভ্যর্থনা করেননি। অনেকে চমৎকৃত হন। যেমন ‘যুগান্তর’ খবরের কাগজের সমালোচনায় লেখা হয়েছিল – ‘মঞ্চ কাহিনীর প্রয়োগ এবং আঙ্গিক বিন্যাসে নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বহুরূপীর ভূমিকা সৃজনমুখী বিপ্লবের ভূমিকা। ‘বাকি ইতিহাসে’র মঞ্চরূপ এই বিপ্লবেরই এক অভিনব প্রতিফলন বললে অত্যুক্তি হবে না।’ আবার ‘দেশ’ পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন – ‘বক্তব্যের দিক থেকে একটি অন্তঃসারশূন্য ও অকিঞ্চিৎকর নাটককে বহুরূপী তাঁদের নিজস্ব কৌলীন্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছেন। বলতে হবে, তাঁদের হাতে স্পর্শমণি আছে।’
নাটককারের কেমন লেগেছিল ‘বাকি ইতিহাস’? এক কথায় বলা মুশকিল, উদ্বোধনী মঞ্চায়নের কয়েক মাস বাদে নিউ এম্পায়ারে এক মর্নিং শো-তে ‘বাকি ইতিহাস’ দেখে সবটুকু ওঁর মনঃপূত হয়নি। বিশেষত, ‘একই অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে সীতানাথ-কণা, আর শরদিন্দু-বাসন্তী করার পক্ষপাতী নই’। যাঁরা এ নাটক পড়েছেন বা দেখেছেন, তাঁদের মনে পড়বে যে এই দুটি মাঝবয়সী দম্পতির টানাপোড়েনের বুনোটেই এ নাটকের বিন্যাস। শম্ভু নাট্যবস্তু নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া না করলেও দুটি দম্পতির অভিনয় করিয়েছিলেন কুমার রায় ও তৃপ্তি মিত্রকে দিয়েই। এতেই আপত্তি ছিল নাটককারের। স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন বাদল –
ওটা যদি করা হয়, তাহলে থার্ড অ্যাক্ট-এ নতুন একজন অভিনেতাকে সীতানাথ সাজিয়ে আনতে হয়। যেটা ইমিডিয়েট্লি থিয়েট্রিকালি দর্শকদের ইমপ্রেশন দেবে যে এইটেই তাহলে চিন্তার কারণ। তা তো নয়, আসলে তো শরদিন্দু, তার চিন্তাটাই রিয়াল কারণ। কাজেই ওই একই সীতানাথের আসবার কথা, সেইটেই ওর মনের মধ্যে ঘুরছে। কিন্তু ওখানে একটা নতুন এজেন্সি এসে গেল, সত্যি সত্যিই যেন সীতানাথের প্রেতাত্মা এসে আসল কথাটা বলে দিয়ে যাচ্ছে। এটা হয়ে গেলে বাকি ইতিহাস-এর আসল পয়েন্ট-টাই নষ্ট হয়ে যায়। একটা প্রোডাক্শনল চমক হয়তো হয়, কিন্তু আসল পয়েন্ট-টা বাদ চলে যায়। এইটেই আমার ধারণা। … আমি ওটা বলা সত্ত্বেও শম্ভুবাবু ওটা নিয়ে আমায় কিছু বললেন না। পরে একসময় আমায় ডেকে বললেন, থার্ড অ্যাক্ট-এ লোকের কিছু ডিফিকাল্টিজ হচ্ছে; হচ্ছে, সেটা উনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি আমায় বললেন, আরেক ভাবে নাটকটা বদলে দিয়ে অন্য একটা সলিউশন দিতে। সেটায় আমি রাজি হলাম না। আমি বলেছিলাম, আপনি যা ইচ্ছে করুন, যেটা ইচ্ছে বদলে দিন। উনি বললেন, যতদিন আমি তা না করি, উনি শো বন্ধ করে দেবেন।
শো অবিশ্যি বন্ধ হয়নি। জেদাজেদি একটু হয়েছিল। বাদলের মনে হয়েছিল ‘উনি আমার উপরে রেগে গিয়েছিলেন।’ তা সত্ত্বেও বাদল যখন সঙ্গীত নাটক অকাডেমির পুরস্কার পেলেন, নয়া দিল্লির মবলঙ্কর অডিটোরিয়ামের সেই অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে বহুরূপীর ‘বাকি ইতিহাস’-ই মঞ্চস্থ হয়েছিল। দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৬৯-এর ৩ ও ৪ মার্চ। ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এর সমালোচক লিখেছিলেন –‘To transform this play from inaction into an absorbing production of excitement and emotion is a challenging task. Sambhu Mitra’s directorial imagination was fully evident in the way he was able to vary the mode and pitch of the three acts where different couples play out their roles and yet bind them together in a unity of identity.’
দিল্লি দরবারে এটাই ছিল বাদল সরকারের আবির্ভাবের মুহূর্ত। দ্য ভিনি ভিডি ভিসি মোমেন্ট।
বহুরূপীর জিম্মায় থাকা বাদলের অনেক নাটকের মধ্যে থেকে এরপর বাছা হল ‘ত্রিংশ শতাব্দী’। এ নাটকে পরমাণু অস্ত্রের ভয়াবহতা নিয়ে ডকুমেন্টারি থিয়েটারের রসদ জোগান দিয়েছিলেন বাদল। হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় তখন বহুরূপীর তরুণ প্রজন্মের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মুখ। তাঁর নির্দেশনায় আরও একটি নিরীক্ষাধর্মী কাজ করার আয়াস নিয়েছিলেন বহুরূপী। ১৯৬৯-এর ২২ জুন এটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়। শাঁওলী মিত্র সেই প্রথম নাটকে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ‘এক ডিভোর্সী মাঝ-বয়সী মহিলার ভূমিকায়’। নাটকটি অবিশ্যি তেমন চলেনি। যদিও নির্দেশকের মুনশিয়ানা প্রশংসিত হয়েছিল। প্রযোজনা পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল –
‘ত্রিংশ শতাব্দী’ অন্য ধরনের নাটক। এ নাটক তথ্যভিত্তিক। এ নাটকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার, মানবজাতির এক চরম সঙ্কটের রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাক্তিমানুষকে দেখান হয়েছে। তাই এ নাটকের গঠনপ্রণালী আলাদা – এর আবেদন বলিষ্ঠভাবে পৃথক।
‘বাকি ইতিহাস’-এর পর থেকে মাঝের ক বছর বহুরূপীর প্রযোজনার নির্দেশনা দেননি শম্ভু মিত্র। চেয়েছিলেন অন্যান্যদের হাতে ভার ন্যস্ত করতে। তাতে আংশিক সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই। ১৯৭১-তে আবার নির্দেশনায় ফিরলেন শম্ভু, বাদলের নাটক ‘পাগলা ঘোড়া’ নিয়ে। নাটকটি এতদিনে বাদলের একটি সিগনেচার প্লে হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। শ্মশানে দাহ হতে আসা এক নারীর শবদেহকে সামনে রেখে শশী হিমাদ্রি সাতু ও কার্তিক এই চার যুবকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে মাঝখানে রেখে ঘনিয়ে ওঠা নাটক। বহুরূপীর প্রযোজনাপত্রীতে ওই চার যুবকের বয়ানে ছাপা হয়েছিল –
আমরা চারজন।
চারজন টুকরো মানুষ। শ্মশানের অন্ধকারে বসে তাস খেলি।
আমরা ফাটা-মুখোসপরা মানুষ।
যদিচ স্বীকার করিনা সহজে।
কিন্তু কোনো এক ঘন অন্ধকার রাত্রে
যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের প্রেম,
আমাদের ভালোবাসাকে জ্বালিয়ে দিই শ্মশানের চিতাগ্নির মত ক’রে
যেখানে, পুড়ে যায় পূত অস্থি, পবিত্র ঈশ্বর, নষ্ট শরীরের ঘ্রাণে
যেখানে জ্বালা ধরে চোখে, বুক জ্বালা করে ঝাঁঝালো স্মৃতির উষ্ণবিষে –
তখন হয়তো বা ধরা পড়ে আমরা প্রবঞ্চক।
প্রতারণা করেছি আমাদের বিশ্বাসকে, প্রেমকে, ভালোবাসার ঈশ্বরকে –
সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও। তাই আমরা টুকরো মানুষ –
আমরা কৃৎকর্মের সাফাই গাই
কখনো মূঢ় অহঙ্কারে, নিষ্ঠার বড়াই করে কখনো বা
সুবিধাবাদের আড়ালে।
এই সাফাই-এর অন্তরালে যে জীবন আমাদের,
সে জীবনে কোনও এক গভীর অন্ধকারে
শ্মশানের নিস্তব্ধতায় আমরা নগ্ন হই।
তখন দেখতে পাই আমরা বিগত যৌবন!
অথচ একদিন –
যৌবনের প্রখর রোদ্রে – পূর্ণতার পথে
যে নিয়ে যেতে পারত সে এসেছিল ঝড়ের মত,
ঝাঁকড়া-কেশর পাগলা ঘোড়ার মত।
জীবনে সে একবারই আসে।
তাকে ধরার মত কব্জির জোর পরখ করা হয়নি সেদিন,
ভয় পেয়ে হয় পালিয়ে গেছি দূরে – নয় তো ঔচিত্যের বেড়াজাল বেঁধে নিজেকে আটকেছি।
সত্যের সামনে, জীবনের সামনে, নিজের সামনে মুখোমুখি হবার
আহ্বানকে হেলায় হারিয়েছি। ঝুঁটি ধরে সেই
পাগলা ঘোড়ার পিঠে চাপতে পারিনি কোনওদিন।
ভ্রষ্টলগ্নে তাই শ্মশানে আমরা চারজন –
আর পাঁচজনের মতই – আমরা চারজন –
‘পাগলা ঘোড়া’-র উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়েছিল একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে, ১৯৭১-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি। দিনটি রবিবার। এবং বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে ইতিহাসে লাল আখরে লেখা, কারণ ওই দিন থেকেই লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষণায় কলকাতার প্রধান শিল্পক্ষেত্র হয়ে ওঠা একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত নাট্যাভিনয় শুরু হয়। বহুরূপীই এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই অগ্রপথিক দলটি প্রায় তিন দশক ধরে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় এই একাডেমিতে নিজেদের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। সূচনাপর্বের সঙ্গে ক্রমশ প্রসেনিয়াম-ছুট হয়ে ওঠা বাদলেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই একাডেমির অন্যত্র ততদিনে নিজস্ব নাট্যনন্দনের নিরীক্ষায় মেতে গেছেন বাদল। বহুরূপীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমে আলংকারিক হয়ে পড়েছে।
নাটক ‘পাগলা ঘোড়া’-কে মঞ্চে আনতে বাদলের মূল পাঠ নানানভাবে সম্পাদনা করেছিলেন শম্ভু। স্মরণীয় মঞ্চনির্মাণ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। স্বপনের ভাষায় ‘বাদল সরকারের আঙ্গিক থেকে অবশ্যই স’রে এসেছিলেন শম্ভু মিত্র, তাঁর পরিচালনায়। কিন্তু ঐ অকারণ কৌশল-জটিলতা বর্জনের ফলে নাটকটি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত করেছিল অভিনয়গৌরব – বিশেষ ক’রে শাঁওলী মিত্রের এবং দেবতোষ ঘোষের।’ বাণিজ্যিক সফলতার পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল সাকসেস পেয়েছিল ‘পাগলা ঘোড়া’। যেমন, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ লিখেছিল – ‘প্রযোজনার শৃঙ্খলা আর পারিপাট্যের হাত-ধরাধরি করে চলেছে অভিনয়। এমন সুন্দর দলগত অভিনয় নৈপুণ্য ইতিপূর্বে বহুরূপীর নাটকেও খুব বেশী দেখা যায়নি।’
অনেকদিন ধরে অনেক মঞ্চায়ন হয়েছিল ‘পাগলা ঘোড়া’-র। দেশের নানান কেন্দ্রে তো বটেই, বাংলাদেশেও গেছিল, ১৯৭৪-তে।
বহুরূপী-কৃত এর পরের বাদল-নাটক ‘বাঘ’-এর উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয়েছিল কলা মন্দির বেসমেন্টের ছোট প্রেক্ষাগৃহে, ১৯৭৫-এর ১১ নভেম্বর। শেষ মঞ্চায়ন এর দেড় বছরের মাথায়, একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে, ১৯৭৭-এর ২০ মার্চ। নির্দেশনায় ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। মঞ্চবিন্যাসের দায়িত্বে দীপেন সেন ও উৎপল নায়েক। আলোক পরিকল্পনায় দিলীপ ঘোষ। নাটকে দুটি চরিত্র – একটি বাঘ আর একটি মেয়ে। চরিত্রদুটিতে অভিনয় করতেন যথাক্রমে অরিজিৎ গুহ ও রমলা রায়। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই নাটকের প্রযোজনাপত্রীতে বেশি কথা ছিল না। খানিক ধরতাই দিয়ে সংলাপ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল কিয়দংশ।
একজন বাঘ আর এক মেয়ের গল্প। শুরু হয় বাঘের ডেরায়। হ্যাঁ, বাঘের ডেরা – যেখানে সেল্ফ ভর্তি বই আর বই। বাঘ তার শিকার ধ’রে নিয়ে এসেছে – কাহিনীর খেই ধরতে হবে এখান থেকেই। কাহিনী মানে কতকগুলো কথার পিঠে কথা, যেমন :
কিন্তু এ নাটকটি তেমন দর্শক আনুকূল্য পায়নি। এটি নিয়ে বহুরূপীর তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল না। স্বপনের ভাষায় – ‘সংখ্যাপূরণ আর ‘ডাকঘরে’র মতো স্বল্প সময়ের নাটকে সময়পূরণের জন্যই যেন প্রযোজিত হয়েছিল একাঙ্কটি।’
তুলনায় অনেক গুরুত্ব পেয়েছিল ‘যদি আর একবার’, যার প্রথম মঞ্চায়ন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ খ্রি, একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। নির্দেশনায় ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। মঞ্চ পরিকল্পনায় কুমার রায়, আলোয় কালীপ্রসাদ ঘোষ। নাচেগানে ভরপুর এ প্রযোজনার সংগীত পরিচালনার জন্য বাইরে থেকে আনা হয়েছিল দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকে, নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন অরিজিৎ গুহ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শান্তি দাস, কুমার রায়, নমিতা মজুমদার, গীতা চক্রবর্তী, রমলা রায় প্রমুখ। বুড্ঢা জিনের চিত্তাকর্ষক ভূমিকায় রমাপ্রসাদ বণিক। জমজমাট এই প্রযোজনার মেজাজ বহুরূপীর অন্যান্য মননধর্মী নিরীক্ষামূলক নাটকের চেয়ে আলাদাই ছিল। ফ্যান্টাসি যেমন হয় আরকি! তাই নির্মাণকুশলতা ও অভিনয়ের তারিফ করার পর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ সওয়াল করেছিল – ‘বহুরূপী তার সাতাশ বছরের জীবনে সম্ভবতঃ এই প্রথম বাণিজ্যের দিকে তাকালেন। একে কি আপোষ বলা যেতে পারে?’ উত্তর মেলেনি। তবে কিনা লক্ষ্মীর পরীক্ষায় এবারে ডিস্টিংশন পেয়েছিল বাদল-প্রণীত শেষ বহুরূপী প্রযোজনা।
‘যদি আর একবার’-এর শেষ মঞ্চায়ন ২৭ নভেম্বর ১৯৭৯ খ্রি, রবীন্দ্র সদনে। এই কালপর্বে বহুরূপীর দলে একের পর এক ভাঙন না এলে আরও অনেক দিন ধরে চলতে পারত এই প্রযোজনা।
এই লেখা শেষ করব ‘প্রলাপ’ বকে। আগেই আমরা দেখেছি যে ১৯৬৭-র শেষাশেষি বহুরূপী এই নাটকের প্রযোজনা করেছিলেন, বাদলেরই নির্দেশনায়। সবে নাইজিরিয়া থেকে কলকাতায় ফিরে থিতু হতে চাইছিলেন বাদল। মনোযোগী হতে চাইছিলেন নাট্যচর্চায়। ওঁর জবানে পাচ্ছি, ‘নাইজিরিয়া থেকে ফিরে আসি ষাটষট্টি সালে। কিন্তু নাইজিরিয়াতে এই নাটকগুলো লিখতে লিখতে যে পুরো প্ল্যান আমার মাথায় তৈরি হচ্ছিল, তাতে আমি তখন যথেষ্ট ইন্ভল্ভ্ড্ হয়ে পড়েছি, বুঝতে পারছি যে চক্র দিয়ে আর হবে না, এবার একটা থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবার হেজিটেট-ও করছি। আমি ওই ডিসিপ্লিন-এ খুব একটা আকৃষ্ট হতাম না। তার চেয়ে যদি একটা দল পেয়ে যাই, যাদের হয়তো অভিনয়ের বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে, অথচ ভালো নাটকের অভাব আছে, সেরকম কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেটাকে স্ট্রং করা বরং বেটার। বহুরূপী-তে ঢোকার কথাও আমি চিন্তা করেছিলাম।’ এই সময় কিছুদিনের জন্য বহুরূপীর পুরোধা শম্ভু মিত্র দেশের বাইরে– ফিলিপিনস জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা পশ্চিম জার্মানি সফর করছেন। নির্দেশকের অভাবে যেন থমকে আছে বহুরূপীর অশ্বমেধের ঘোড়া।শাঁওলীর বয়ানে পাচ্ছি – ‘এইসময়ে শম্ভু মিত্র চাইছিলেন, নতুন কোনও নির্দেশক উঠে আসুক, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুক। এরই জন্যে হয়তো ১৯৬৭-তে বাদলবাবুকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁর নিজেরই নাটকের নির্দেশনা দিতে।’ এমন অনুরোধ আরও কাউকে কাউকে করেছিলেন শম্ভু। যথাবিজন ভট্টাচার্যকে, স্বরচিত ‘আজ বসন্ত’ বহুরূপী থেকে করার জন্য। বাউন্ডুলে বিজন পেরে ওঠেননি, বাদল পেরেছিলেন। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা উশুল করেছিলেন। আপাতভাবে যাকে পাল্টি ঘর ভাবছিলেন, তার সঙ্গে পরিণয়টি ফলপ্রসূ হবে কিনা যাচাই করে নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই প্রণয় যদিওবা উদ্দীপক ছিল, পরিণয়টি তত মধুর হল না। বহুরূপীর অন্দরে কান পাতলে এমনই টের পাওয়া যায়। বাকিটা ১৯৮৪-তে প্রতিভা-শমীককে দেওয়া ওঁর সাক্ষাৎকার পড়ে আমরা বুঝে নিতে পারি।
বহুরূপী-তে ঢোকবার আগে একটু ভালো করে ভেবে-চিন্তে ওঁরা যখন অফার দিলেন, শম্ভুদা তখন ছিলেন না, প্রলাপ ডাইরেক্ট করতে, আমি খুব খুশি হয়েই অ্যাকসেপ্ট করলাম, কারণ তখন আমি ভাবছি, আমি এর মধ্য দিয়ে একটা দেখবার সুযোগ পাব, বহুরূপী-তে ঢোকাটা সুবিধের হবে কি না। প্রলাপ আমি ডাইরেক্ট করলাম, কিন্তু মনে হল যে, সুবিধে হবে না, কাজ হবে না। কতকগুলো জিনিস থেকে আমার মনে হল যে, আমার আলাদা কাজ করা ছাড়া উপায় নেই।
এ কথা শুনে প্রতিভা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কেন, বাদলদা?’ সদুত্তর পাননি। বাদল বলেছিলেন, ‘সে-গল্পগুলো বলতে চাই না। মোট কথা, আমার টেম্পেরামেন্ট-এর সঙ্গে ওখানকার টেম্পেরামেন্ট মিলল না। মনে হল, ওখানে আমি টিকতে পারব না।’
অর্থাৎ কিছুদিনের লিভ-ইনের পর দুই তরফই বুঝতে পেরেছিলেন কমপ্যাটেবিলিটির ঘাটতি আছে। টো-টো কোম্পানি আর ঘর-করা এক জিনিস নয়। ‘প্রলাপ’-এর একটিই মঞ্চায়ন হয়েছিল, নাম কা ওয়াস্তে, নিউ এম্পায়ারে, ১৯৬৭-র ৩ অক্টোবর। অভিনয়ে ছিলেন কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ ও রমলা রায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনও আলোকচিত্রী তার কোনও মুহূর্ত সংরক্ষণ করেননি। ফলে ভিস্যুয়াল রেফারেন্স বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই। তবে বহুরূপীর মহাফেজখানায় আজও বাদলের হাতের লেখা থেকে সাইক্লোস্টাইল-করা বেশ কয়েকটি পারফরমেন্স স্ক্রিপ্ট সংরক্ষিত আছে। তাতে মলিনতার দাগ পড়েনি। দুয়েকটি সমালোচনা বেরিয়েছিল। তাতে বাদলের জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ার দরুন শম্ভুকে অভিনন্দিতও করা হয়েছিল। কিন্তু তেলে-জলে মিশ খায়নি। স্বপন মজুমদারের একটি দ্যোতক মন্তব্য আছে এ নিয়ে – ‘তবে ভবিষ্যৎ অবশ্য প্রমাণ করেনি, বহুরূপীর পরিচালকের আলখাল্লা তাঁর মাপে হয়েছিল।’
এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নিজের নাটকের দল গড়েছিলেন বাদল। নাম দিয়েছিলেন শতাব্দী। অচিরেই প্রসেনিয়ামের আওতার বাইরে গিয়ে নতুন নাট্যভাষের অনুসন্ধান করেছিলেন। উল্লেখ্য, এর দরুন বহুরূপীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্কে কোনও চিড় ধরেনি। কোনও অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়নি। কেউ কারুর সম্পর্কে কোনও অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। ‘ত্রিংশ শতাব্দী’ কিংবা ‘বাঘ’ বহুরূপী যেমন করেছেন, শতাব্দীও করেছেন। নিজস্ব নাট্যনন্দনে ঢালাই করে নিয়ে।
বিচ্ছেদ সব সময়ই বিদ্বেষের হয় না। বহুরূপীর ইতিহাসে বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল আজও সুঘ্রাণ বয়ে আনে।
তথ্যসূত্র:
পুরোনো কাসুন্দি দ্বিতীয় খণ্ড, বাদল সরকার, কলকাতা, ২০০৭ খ্রি
পূর্ব (‘বহুরূপী ৭০: ঐতিহ্য ও বিস্তার’, সং প্রভাত কুমার দাস), পাঁশকুড়া, ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি
বহুরূপী ৫০: প্রযোজনা বিষয়ক তথ্যপঞ্জী, বহুরূপী, কলকাতা, মে ১৯৯৮ খ্রি
বহুরূপী ১৯৪৮-১৯৮৮, স্বপন মজুমদার, বহুরূপী, কলকাতা,মে ১৯৮৮ খ্রি
বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার (সং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), থীমা, কলকাতা, ২০২২ খ্রি
শম্ভু মিত্র: বিচিত্র জীবন পরিক্রমা, শাঁওলী মিত্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়া দিল্লি, ২০১০ খ্রি
লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে পুনর্মুদ্রিত
||হল্লার পরেও: বাদল সরকার ও সফদর হাশমির এক কল্পিত কথোপকথন|| ——দেবার্ঘ্য দাস
ভূমিকা: স্বাধীনোত্তর ভারতের নাট্যভূমিতে দুটি প্রবণতা একসঙ্গে বিকশিত হয়। প্রথমত, বাদল সরকারের তৃতীয় নাট্য, যা প্রোসেনিয়ামের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে খোলা আকাশের নিচে, ন্যূনতম উপকরণে, দর্শক–অভিনেতার দূরত্ব কমিয়ে আনতে চেয়েছে (Katyal, 1990)। দ্বিতীয়ত, সফদর হাশমির পথনাটক, যা বিশেষত শ্রমিক আন্দোলন ও জনসমাবেশের ভিতর রাজনৈতিক বার্তাকে সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণ রূপে হাজির করেছে (Machine(মেশিন), 1978; Aurat,(অওরৎ) 1979)।
এই দুটি ধারার সঙ্গে যদি যুক্ত করা যায় মণ্টোর ট্রমা-সাহিত্য—যেখানে পার্টিশনের ক্ষত সংক্ষিপ্ত অথচ শকপ্রদ দৃশ্যে উন্মোচিত—এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক ও উপন্যাস, যেখানে নন্দনশিল্পের মধ্যেই নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন নিহিত, তবে ভারতীয় নাটকের একটি চার-ধারার মডেল পাওয়া যায়: ১.পাল্টা-আর্কাইভ (বাদল সরকার), ২.এজিট-প্রপ সংক্ষিপ্ততা (সফদর হাশমি),
৩.ফরেনসিক বাস্তববাদ (সাদাত হাসান মন্টো),
৪.নান্দনিক-নৈতিকতা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।… লিখতে লিখতে চোখ গেল জানলার বাইরে। বৃষ্টিটা ভালোই পড়ছে; মেঘলা আকাশ , গুমোট ভাবটা কাটবে কি কাটবেনা চিন্তা করতে করতে টেবিল থেকে উঠে ঘরের বাইরে লাল বারান্দায় এসে বিড়িটা ধরালাম। ঠিক কোন সময় আমার সামনের সবুজ বাগান নাটকের স্টেজে পরিবর্তিত হয়েছে মনে নেই— (একটি খোলা আঙিনা। তিন দিক গাছ, এক দিকে অর্ধনির্মিত ফ্লাইওভার। মাঝখানে চক দিয়ে আঁকা বৃত্ত। একটু আগেই বৃষ্টিটা থেমেছে। ভেজা মাটি। দু’টি ভাঙা বেঞ্চ—একটায় বাদল সরকার, অন্যটায় সফদর হাশমি। দূরে ট্রামলাইনের মতন লম্বা একটা ছায়া। চারদিকে ছড়িয়ে আছে কাগজের পোস্টার, বাঁশি, ডাফ, আর কয়েকটা লাঠি—প্রপ না অস্ত্র তা বোঝা কঠিন।)
বাদল: (বৃত্তের দিকে তাকিয়ে) এই বৃত্ত—নিরাপত্তা নয়, দায়। দর্শকের সঙ্গে একটা চুক্তি। আমি যখন আঙিনামঞ্চ বলেছিলাম, আসলে চেয়েছিলাম মঞ্চ আর দর্শকের দূরত্বটাকে বিয়োগ করতে। দেহ, কণ্ঠ, শ্বাস—তারাই প্রপ। পাঁচশো ওয়াটের আলো নয়, বরং চোখের ভেতরকার আলোই হচ্ছে মঞ্চের আলোকসজ্জা।
সফদর: (হাতে ডাফ টোকা দেন) আর আমি চেয়েছিলাম রাস্তার শব্দটাই হোক স্কোর। বাসের হর্ন, ভিক্টোরিয়ার ঘোড়া, ইউনিয়নের স্লোগান—সব মিলেই তো স্ট্রিট থিয়েটার-এর সাউন্ড-ডিজাইন। আমরা JANAM/ জনম-এ শিখেছিলাম, নাটককে দ্রুত জড়ো হতে হয়, দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে হয়, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—দ্রুত মনে গেঁথে দিতে হয়। পাঁচ মিনিটের ‘মেশিন’ও কখনও কখনও এক ঘন্টার বক্তৃতার চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়।
বাদল: ‘মেশিন’—শুধু বিষয় নয়, ভঙ্গিও। শ্রম আর অভিনয়ের সম্পর্কটা সেখানে নগ্ন। আমি ‘ভোমা’, ‘মিছিলে’ খুঁজেছি এই নগ্নতাই—যেখানে ভাষা দণ্ডায়মান, আর শরীর তার ব্যাকরণ। প্রোসেনিয়াম আমার কাছে ছিল এক ধরনের বাধ্যতামূলক শালীনতা; তৃতীয় থিয়েটার সেই শালীনতার গায়ে কাদা ছুঁড়ে দিয়েছে।
সফদর: শালীনতা ভাঙতে গিয়ে আমরা কখনও অশালীন হইনি—বরং কর্তৃপক্ষের শালীন মিথ্যাকে অশালীন বলেছি। আমাদের ‘হল্লা বোল’ রক্তে লিখিত এক উচ্চারণ—সেখানে থেমে যাওয়ার মানে হত পরাজয়; তাই আমরা থামিনি। নাটকের দেহে যে আঘাত এসেছিল, মানুষের দেহে যে আঘাত এসেছিল, তাকে আমরা প্রতিদিন রিহার্সালে সেলাই করেছি। এটাই আমার নন্দন—প্রতিবাদের কর্মশালা।
বাদল: নন্দনের কথায় মনে পড়ল—আমি নন্দনের বাইরে যে পার্কে, মাঠে, ছাদে নাটক করেছি, সেখানে দর্শক ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কেউ এসে বসছে, কেউ উঠে যাচ্ছে, কেউ প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে—“শেষে কী হবে?” তৃতীয় থিয়েটারের ‘শেষ’ নেই; আছে ‘সম্পর্ক’। তুমি সেই সম্পর্ককে পথে নামিয়ে দিলে।
সফদর: সম্পর্ক মানে সংগঠনও। ইউনিয়নের গেটে সকাল আটটায় ‘অওরৎ’ খেলতে গিয়ে বুঝেছি, নাটকের ভাষা বদলাতে হবে। কোরাস ব্যবহার করেছি স্লোগানের মত, ব্যঙ্গ ব্যবহার করেছি আয়নার মত, তথ্য ব্যবহার করেছি হাতুড়ির মত। কিন্তু হাতুড়ি দিয়ে কাচ ভাঙার আগে কাচের কারিগরিকে বুঝতে হয়—তাই লেখার আগে আমরা কারখানায় যেতাম, বাসডিপোর চালকদের সঙ্গে বসতাম, নারীদের মিটিংয়ে আলোচনা শুনতাম। লেখার ঘরে তত্ত্ব খুঁজে, রাস্তায় প্রমাণ করে দেখিয়েছি।
বাদল: আমি অফিস থেকে নাটকে এসেছিলাম—নকশা আঁকা হাতটা একদিন লোকজ আঙ্গিকে ডুবে গেল। শতাব্দীতে আমরা টেক্সটকে দেহে নামালাম: রিপিটেশন, ইম্প্রোভাইজেশন, কালেক্টিভ ডিভাইসেস—সবকটা ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। শিল্পের ‘খরচ’ কমালে দর্শকের ‘খরচ’ও কমে; মুক্তি তখন টিকিটের দামে নয়, দেহের সদিচ্ছায়। আমি বলেছি: “অভিনেতা বেতন নেবে, কিন্তু দর্শক বেতন দেবে না—দেবার কথা নয়।” এই অর্থনৈতিক ব্যাকরণটাই ছিল তৃতীয় থিয়েটারের রাজনীতি।
সফদর: (হেসে) আমরা টিকিট নিতাম না; কিন্তু কেউ যেন বলুক যে, টিকিট বিনামূল্যে ছিল! অভিনয়কারীর সাহস, কোরাসের শ্বাস, প্রপসের তৎপরতা—সবই দামি। ‘বিনা টিকিট’ মানে ‘বিনা দায়’ নয়। তাই রুটিন করেছি—সকাল মিটিং, দুপুরে রিহার্সাল, সন্ধ্যায় শো, রাতে আলোচনা। যারা ভাবে আগিটপ্রপ মানেই হালকা, তারা কখনও দেখেনি আমরা ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে কেমন শান দিতাম। আগিটপ্রপ—এজিটেশন প্লাস প্রোপাগান্ডা—আমার কাছে ছিল যুক্তিযুদ্ধ; স্লোগানও যুক্তি, ব্যঙ্গও যুক্তি, গানও যুক্তি।
বাদল: যুক্তিরও আবার দেহ আছে। এবং ইন্দ্রজিৎ—সেখানে ‘আমি’ আসলে কোরাস; ব্যক্তির নাম—অমল, বিমল, কমল—পুনরাবৃত্তিতে ভঙ্গুর। পুঁজিবাজার যখন আপনাকে এক-একটা ব্র্যান্ড বানায়, নাটক তখন আপনাকে ফিরিয়ে দেয়—মানুষ হিসেবে। তৃতীয় থিয়েটার এই কারণে পেশাদারিত্বকে প্রশ্ন করেছে; পেশাদারিত্ব ভাল, যদি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে; খারাপ, যদি শুধুই বাজারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে।
সফদর: বাজার এখন ডিজিটাল—আলগোরিদম দর্শকের কাঁধে কর্তৃপক্ষের হাত রেখে বলে: “এটাই দেখো।” রাস্তার জায়গা কমে গেছে, মলের জায়গা বেড়েছে। পারমিশন পেতে ফাইল ঘোরে; তবু আমি বলব—রাস্তা এখনো আছে; যতক্ষণ ফুটপাথে একজন নাটক দেখতে গিয়ে থামে, নাটক বেঁচে থাকে। ক্যমেরার রিলস ‘ভিউ’ দেয়, রাস্তার মিটিং ‘ভয়স’ দেয়। ‘ভিউ’ ও ‘ভয়স’-এর টানাপোড়েনে আমাদের কাজ আজ আরও জরুরি।
বাদল: তুমি মৃত্যুর মুখে নাটক থামাওনি; আমি বৃদ্ধ বয়সেও পার্কের ধুলোয় গড়িয়েছি। আজ যারা থিয়েটার করে, তাদের বলব—রিস্ক নাও, কিন্তু রিস্কের তত্ত্ব বানাও। শুধু স্লোগান নয়, স্কোর বানাও; শুধু চরিত্র নয়, ডকুমেন্ট বানাও। আমি ‘বিয়ন্ড দ্য প্রোসেনিয়াম’-এ লিখেছিলাম—দর্শককে ‘সাক্ষী’ বানাও। সাক্ষী সে-ই, যে নিজের দায় বুঝতে পারে।
সফদর: সেইসব সাক্ষীকে ‘সাথী’ করাই আমার লক্ষ্য ছিল। তাই লেখায় ‘কালেকটিভ অথরশিপ’—রিহার্সালে যে লাইন জন্মেছে, সেটা লেখকের নাম পায় না; পায় দলের নাম। ‘অওরৎ’-এ নারীর শ্রমের হিসেব, ‘ডিটিসি কি ধন্ধলি’-তে শহরের পাবলিক সার্ভিসের লুট—এসব আমরা কথা বলেছি সরাসরি ভাষায়, কিন্তু সরলতা মানেই সহজ সম-সরলীকরণ নয়। ব্যঙ্গের ভিতরে ছিল তথ্যের ধার।
বাদল: তথ্যের ধার অভিনয়ের হাড়ে ঢুকতে হবে। থিয়েটার স্কুলে শেখানো ‘প্রজেকশন’-এর আজ অর্থ বদলেছে—সোশ্যাল মিডিয়া প্রজেক্ট করে, অভিনেতা নয়। কিন্তু কণ্ঠ যখন বাতাসে খোদাই হয়, তখন সে খোদাই হয় সোয়াসের পাথরে। আমার প্র্যাকটিসে কোরিওগ্রাফড রিপিটেশন—একই গতির প্রত্যাবর্তন—দেখিয়েছে কিভাবে অভ্যাসে রাজনীতি লুকিয়ে থাকে। মার্চিং কেবল সৈন্যদলের নয়; শহরের অফিস-বাসও এক ধরনের মার্চ। নাটককে সেই মার্চে ফেলে দিতে হবে একটা বাধা হিসেবে—একটা ‘ভুল তাল’হিসেবে।
সফদর: ভুল তালই নতুন তাল। আমরা দৃশ্যমান শত্রুর বিরুদ্ধেই শুধু কথা বলিনি; অদৃশ্য ক্ষমতার বিরুদ্ধেও কথা বলেছি—বাণিজ্যের ছদ্মশালীনতা, সংবাদমাধ্যমের শৈল্পিকতার মুখোশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজারিকরণ। আজ যখন কন্টেন্টই পণ্য, থিয়েটারকে হতে হবে কন্ট্রা-কন্টেন্ট—একটা ঘটমান প্রতিরোধ, যা প্ল্যাটফর্মে আপলোড হয় না, মানুষের স্নায়ুতে আপলোড হয়।
বাদল: (হালকা হাসি) আপলোড—ভাল শব্দ। তৃতীয় থিয়েটার চাইত ডাউনলোড—লোকজ, পালা, কবিয়ালের বডি-নলেজ। নৃত্যশরীর, বাউলের দেহ-বাক—এসব আমরা ‘মডার্ন’ বানাইনি; বরং নিজেদের ‘মডার্ন’ ভাঙতে ব্যবহার করেছি। আধুনিকতা যদি কেবল কংক্রিট ও কাঁচের দালান হয়, তা হলে পার্কের ঘাস-ও আধুনিকতার বিপ্লব।
সফদর: আমাদের পরের প্রজন্মের জন্য তিনটে কথা বলি—এক, রিগর। রাস্তায় যাবার আগে তথ্য যাচাই, স্ক্রিপ্টে ফাঁক না রাখা, সময়-জ্ঞানের জরুরী শিক্ষা; দুই, রিস্ক। কেবল পুলিশের ঝুঁকি নয়; নিজের আরামের বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিতে শেখা। তিন, রিলেশন। নাটক শেষ মানে ‘সমাপ্তি’ নয়—আলোচনা, বিতর্ক, সংগঠন। দর্শক যেন টিমে ঢুকে পড়ে; পরদিন ফ্যাক্টরির গেটে যেন সেই দর্শকই কোরাসে অংশগ্রহণ করে – সেইদিকে লক্ষ্য রাখা।
বাদল: আর আমি বলি—রূপ। প্রতিবাদের রূপও শিল্পের আর্কিটেকচার চায়। ওপেন ফর্ম মানে অবিশৃঙ্খল নয়—বরং সংগত, সংগঠিত স্বেচ্ছাচার। একটি চক-বৃত্ত এঁকে তাতে ঢুকে পড়া মানে নিয়ম বানিয়ে তাকে ভাঙা। ল্যাঙ্গুয়েজ—কেবল শব্দ নয়; ব্লকিং, ব্রেথিং, ব্রেক। ‘পাগলা ঘোড়া’ যখন কালো হাসি ছুঁড়ে দেয়, তখন তার অন্তর্গত মিটার জানে কখন থামতে হয়।
সফদর: আজকের প্রেক্ষাপট—সংকুচিত প্রতিবাদের জায়গা, নজরদারির প্রযুক্তি, ঘৃণার দ্রুতবেগ, মতের বাজার—এদিকে অনলাইন সক্রিয়তা প্রায়ই অফলাইন নিষ্ক্রিয়তার আড়াল। তবু আশার জায়গা আছে—ছোট শহরের নতুন দল, ভাষাভিত্তিক উপভাষার নাট্য-উদ্যম, নারীকেন্দ্রিক স্ক্রিপ্ট, দলিত ও আদিবাসী তরুণ দলের জনমুখী রচনা। পাবলিক স্পেস গায়েব হলে কমন স্পেস বানাও—বাড়ির ছাদ, স্কুলের মাঠ, কমিউনিটি কিচেন, বইমেলার গলি, ট্রামডিপোর শেড।
বাদল: (ট্রামলাইনের দিকে) ট্র্যাক মানে দিকও বটে। থিয়েটারকে বারবার উৎসে ফিরে যেতে হবে—‘কেন’ করি, ‘কার’ জন্য করি, ‘কিভাবে’ করি। আমি যখন বলেছিলাম—থিয়েটার অভ্যাস—তার মানে ছিল প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করা। শিল্পীর অহংকারকে প্রতিদিন ডিফ্লেট করতে হবে; না হলে প্রতিবাদের ভাষা দাঁতে লাগে না।
সফদর: শিল্পীর ইগো-হাইজিন—চমৎকার শব্দ। আমরা দল চালাতে গিয়ে শিখেছি, ভিন্নমতকে দমন করলে শিল্প শুকিয়ে যায়। ক্যালিব্রেশন যেমন প্রয়োজন, তেমনি কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট—মিটিংয়ের টেবিলে যে বিবাদ মেটাতে পারি, রাস্তার মোড়ে তার দাম পড়ে না। তাই স্ক্রিপ্টে বিরোধ রাখো—চরিত্ররা যেন মতভেদে বাঁচে, মোনোলিথ না হয়ে যায়।
বাদল: ফর্মাল এক্সপেরিমেন্ট করো—কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট যেন মানুষের জীবনের খরচে না হয়। দুঃখকে ফেটিশ কোরো না; দারিদ্র্যকে দৃশ্যাবলী বানিও না। তোমার ক্যামেরা না থাকলেও দৃষ্টি আছে—সে দৃষ্টির নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করো। আর, নিজের ভাষাকে ভালবাসো—বহুভাষার দেশ, বহুস্বরের নাটক। অনুবাদ করো, কিন্তু ট্রান্সক্রিয়েশন হবে—শুধু শব্দ নয়, শরীরের রেজিস্টার বদলে দাও।
সফদর: (ডাফে ধীরে তাল) শেষ কথা—ভয়। ভয় থাকবে—আক্রমণ, মামলা, নিষেধাজ্ঞা, অনুদান বন্ধ, হল না পাওয়া, রিভিউ না মেলা। তবে ভয়কে রিহার্সাল করাও—সাইট-রিডিং এর মতো। যে ভয়কে চেনা হয়, সে ভয় নাটকে জায়গা পায়; যে ভয় অচেনা, সে ভয় নাটককে থামায়। আমরা ভয়কে চরিত্র করেছি; কখনও ক্লাউন, কখনও প্রেত, কখনও আমলা।
বাদল: (চকের বৃত্ত মুছে দিতে দিতে) বৃত্ত মুছে গেলেও সম্পর্ক মুছে যায় না। থিয়েটার শেষ হয়ে গেলে থিয়েটার-পরবর্তী আলোচনাই আসল পর্ব। আমরা দু’জন চলে গেছি—কিন্তু প্রশ্ন বেঁচে আছে: ১) বাজারে কীভাবে থাকা যায় বাজারের দাস না হয়ে? ২) বিনোদনের জালে না পড়ে প্রতিবাদকে কীভাবে নন্দনে উত্তীর্ণ করা যায়?
৩) শিখে নেওয়া ভাষাকে কীভাবে ভুলতে শেখা যায়?
সফদর: আর চতুর্থ—কীভাবে আমরা একসঙ্গে থাকি? অভিনেতা, শ্রমিক, গৃহশ্রমে ক্লান্ত নারী, নিরুদ্যোগী ছাত্র, প্রান্তিক ভাষার কবি—সবাই মিলে। দল মানে কেবল থিয়েটার-টিম নয়; দল মানে শহরের নতুন কমন্স। সেখানে নাটক কেবল অভিনয় না, অভ্যাস—জনজীবনের একধরনের দৈনিকতার পাঠ।
(হঠাৎ দূরে ভ্যানে করে কিছু তরুণ-তরুণী আসে। ব্যানার: “আজ সন্ধেবেলায়—আঙিনা নাটক।” তারা চুপচাপ মঞ্চ বানায়: প্লাস্টিকের ক্রেট, দড়ি, পোস্টার। বাদল ও সফদর উঠে দাঁড়ান।)
বাদল: (তরুণদের দিকে তাকিয়ে) আলো না, আহ্বান লাগবে। সফদর: (হেসে) পারমিশন না, পার্টিসিপেশন লাগবে।
(তরুণরা কোরাসে গলা মেলায়; সুর মিলেমিশে যায় শহরের দূরবর্তী ট্রাফিকের সঙ্গে। বাদল ও সফদর পেছনের ছায়ায় সরে যান।)
(একটি খোলা মঞ্চ। টেবিল নেই, কেবল মেঝেতে বই রাখা—ট্যাগোরের নাটক, মণ্টোর গল্প, বাদল সরকারের তৃতীয় নাট্যচিন্তা, সফদরের স্ট্রিট থিয়েটার পেপার। আলো মাঝেমধ্যে ঝাপসা হয়, যেন এক সেমিনার-আলোচনা আর নাট্য-অভিনয় একসঙ্গে হচ্ছে।)
সফদর:
“রবীন্দ্রনাথের নাটক, বিশেষত রক্তকরবী, আজকের সমাজেও Labour Studies–এর পাঠ্য হতে পারে। রাজশক্তি শ্রমিককে মাটির নিচে নামিয়ে দেয়, আর নন্দিনী দাঁড়ায় ‘Agency’ হিসেবে। এটাকে যদি মাইনিং কর্পোরেশন, SEZ, বা আধুনিক কর্পোরেট শোষণের প্রেক্ষিতে রাখি, নাটকটা হয়ে ওঠে সমসাময়িক প্রতিবাদের নন্দন।”
বাদল:“হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলব—রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রতিরোধ নয়, Ritual of Liberation বানান। ডাকঘর–এ মৃত্যু মানে মুক্তি, কিন্তু সেটা শিশু অমলকে কেন্দ্র করে। আসলে একটি Existential Metaphor, যেখানে রাজনৈতিক প্রতীকও লুকিয়ে আছে। উপনিবেশিক সেন্সরশিপের সময়ে ডাকঘর আয়ারল্যান্ডে মঞ্চস্থ হয়েছিল—অসুস্থ দেহ = উপনিবেশিত দেশ। আজকের দিনে এটাকে পড়লে বোঝা যায়—রাষ্ট্র যার শ্বাসরুদ্ধ করে, শিল্প তার জানালা খুলে দেয়।”
“মণ্টোকে আমি পড়ি যেন তিনি এক ধরনের সোশ্যাল হাইপোথিসিস। Partition–এর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখালেন যে রাষ্ট্রের আঁকা রেখা মানুষকে ভেঙে দেয়, কিন্তু শরীরের ক্ষত সেই লাইন মানে না। টোবা টেক সিং–এ ভৌগোলিক বিভাজন এক অসামঞ্জস্যের নাটক—যেখানে মূল চরিত্র এক উন্মাদ। এটা প্রোসেনিয়ামে রাখলে কেবল গল্প হয়, কিন্তু আঙিনা থিয়েটারে করলে দর্শক হয়ে ওঠে সেই সাক্ষী—যারা আজও সীমান্ত নীতির শিকার।”
সফদর:“ঠিকই বলেছ। আমার কাছে মণ্টো ডকুমেন্টারি থিয়েটার–এর পূর্বসূরি। Brecht যেভাবে Verfremdungseffekt–এ শক ব্যবহার করেন, মণ্টোও শক ব্যবহার করেন, তবে ভাষার ভেতরে। তাঁর গল্প ছোট, কিন্তু চমক দেয়। এই চমক আসলে Distancing–এরই ভারতীয় রূপ। আজও যদি ‘খোল দো’ মঞ্চে আনি, সেটা কেবল যৌন সহিংসতার কথা নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার দেহলিপি-এর কথা বলবে।”
বাদল:“মণ্টো আমাদের Wound–এ দাঁড় করান, রবীন্দ্রনাথ আমাদের Healing–এ নিয়ে যান। নাট্যচর্চায় এ দুইই দরকার—Disruption আর Consolation। Brecht বলেছিলেন থিয়েটারকে ‘শিক্ষা’ দিতে হবে; মণ্টো ‘শক’ দিয়ে শেখান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নাটক হলো মানুষের অন্তরের-অভ্যাস; তিনি সৌন্দর্য দিয়ে দায় শেখান।”
সফদর:“হ্যাঁ, একদিকে মণ্টো Subaltern Body–কে সামনে আনে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ Universal Consciousness–এর কথা বলেন। কিন্তু একসঙ্গে রাখলে দেখা যায়—উভয়েই ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। মণ্টো ক্ষত খুলে দেন, রবীন্দ্রনাথ শ্বাস নিতে শেখান। দুটোই সমাজতান্ত্রিক নাট্যচর্চার প্রয়োজনীয় উপাদান।”
কোরাস:
“ঘাসের ডগায় আজও থিয়েটার,
চকের বৃত্তে আজও শহর।
যারা জিজ্ঞেস করে—‘শেষে কী?’
তাদের বলি—‘এখন শুরু।’”
(আলো ধীরে নিভে আসে। বৃষ্টির গন্ধ। দর্শক চারদিকে; মঞ্চ মাঝখানে—আজও।)ভারতীয় নাটকের এই চার ধারা (বাদল সরকার, , সফদর হাশমি, সাদাত হাসান মন্টো, এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ) আসলে সমাজের অদৃশ্য ইতিহাস ও নৈতিক দ্বন্দ্বকে দৃশ্যমান করার অভ্যাস। আজও এনারা প্রাসঙ্গিক কারণ এঁদের টেক্সট স্মৃতি, শ্রম, নারীর দেহ, রাষ্ট্রের সহিংসতা—সবকিছু মঞ্চে টেনে আনে।
বাদল সরকারের তৃতীয় নাট্য ও সফদর হাশমির পথনাটক শুধু ভারতীয় থিয়েটারের বিশেষ অধ্যায় নয়, বরং পাল্টা-আর্কাইভ তৈরির প্রক্রিয়া। যখন এগুলি মণ্টোর ক্ষত-উন্মোচন ও রবীন্দ্রনাথের শ্বাস–সৌন্দর্য–এর সঙ্গে মিলিত হয়, তখন থিয়েটার —
..ইতিহাসের মুছে দেওয়া দাগের পুনর্লিখনের অস্ত্র,
..সমাজের পিতৃতান্ত্রিক/শ্রমপীড়িত কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা,
..এবং দর্শককে কেবল ভোক্তা নয়, নাগরিক ও সাক্ষী বানানোর অভ্যাস — হয়ে ওঠে।
আজও বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, মেশিন, আওরাত এবং রক্তকরবী — প্রাসঙ্গিক—কারণ তারা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শিল্প কেবল সৌন্দর্যের চর্চা নয়; বরং নৈতিকতা ও রাজনৈতিক অনুশীলন।
(বি.দ্র.- প্রসঙ্গত বলে রাখা জরুরী পুরো লেখাটাই কাল্পনিক জায়গা থেকে লেখা। বিশেষ করে আমাদের প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মের বেশিরভাগ মানুষেরা বাদল সরকার, সফদর হাসমি, মান্টো-কে জানেন না ! এ দুঃখজনক হলেও সত্যি! তাই কিছু জায়গায় ইচ্ছে করেই কথোপকথনের মধ্যে ‘বাংরেজি’ ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে)
থার্ড থিয়েটার: অ-বিচ্ছিন্নতার থিয়েটার-দর্শন
সৃজিতা স্যান্যাল
আজকের পৃথিবীতে প্রায় সবদেশের থিয়েটারের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে- সেটা আজকের সময়ের তালটাকে ধরবার। সে তাল যদি না ধরতেই পারা যায় তবে প্রচলিত প্রথাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা তো চলবেই।
(কুমার রায়)
প্রচলিত প্রথা ভাঙার পথে একদিন আসতে হয়েছিল মোটের ওপর তথাকথিত প্রোসেনিয়াম মঞ্চের জন্য নাট্যরচনা ও পরিচালনায় অভ্যস্ত নাট্যকারকেও। আর সেই চেষ্টাই বাংলা তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জন্ম দিল এক নতুন আঙ্গিকের। উন্মোচিত হল এক নতুন দিগন্ত। তার নাম ‘থার্ড থিয়েটার’। নাট্যকার বাদল সরকার।
পবিত্র সরকার বাদল সরকারের লেখা নাটকগুলিকে মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন। ১৯৫৬-৬২ পর্যন্ত সময়কালকে তিনি বলেছেন ‘মূলত হাস্যরসাত্মক নাটক ও বঙ্গীকরণের পর্যায়।’ কখনও বিদেশি নাটক বা চলচ্চিত্রের বঙ্গীয় রূপ, কখনও বা হাস্যরসাত্মক মৌলিক নাটক লেখার দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। গতানুগতিক প্রথা থেকে বেরোনোর চেষ্টা এই নাটকগুলিতে চোখে পড়ে না তেমন। কিন্তু ১৯৬৫-তে বহুরূপী নাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ প্রথাগত বাংলা নাটকের চেনা ধাঁচ ও ছাঁচ থেকে অনেকখানিই বেরিয়ে এল। আঙ্গিক ও বিষয়– দু-দিক থেকেই এল অভিনবত্ব। এই নাটকের পরে-পাত্রী বলতে মাসিমা, মানসী, অমল-কমল-বিমল এবং ইন্দ্রজিৎ। সেই সঙ্গে লেখকও আছেন চরিত্র হিসেবে। অমল, কমল, বিমল ও ইন্দ্রজিৎ নাসের চারটি চরিত্র মঞ্চে ঢোকে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ জানায় সে নিজের ছদ্মনাম নিয়েছে নির্মল। কারণ প্রথানুগত্য ভাঙার ইচ্ছে তার নেই। এখানকার প্রত্যেকটি চরিত্র বয়স বদল করে, নিজেদের পরিচয় বদল করে এবং ভূমিকা বদল করে বারবার মঞ্চে আসে। প্রচলিত কাঠামোর কোনও গল্পও এই নাটকে নেই। শেষ পর্যন্ত প্রথাভাঙা এই নাট্যআঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক-আত্মিক ধ্বংস ও ক্ষয়ের বার্তাই প্রকাশিত হয়। এ নাটক প্রকাশমাত্র তুমুল আলোড়ন তৈরি হয়েছিল নাট্যজগতে। পরে ইংরেজিতে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ অনুবাদ করেছিলেন গিরিশ কারনাড।
‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর নতুন চলন গোটা ভারতবর্ষের নাট্যক্ষেত্রেই সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু এই নতুন নাট্যরূপকে[1] মঞ্চায়িত করার জন্য চিরাচরিত প্রোসেনিয়ামের ধাঁচ থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছিলেন নাট্যকার। তাঁর মতে প্রোসেনিয়ামের প্রধান ত্রুটি হল, অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব[2]। প্রোসেনিয়ামে স্টেজ থাকে দর্শক আসনের চেয়ে উঁচু জমিতে। যেন খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে। “যেন দুটো আলাপহীন ও অপরিচিত সম্প্রদায়”[3]। অভিনেতা ও দর্শকদের সহজ মেলামেশার জায়গাও সেখানে নেই। স্টেজের ফ্রেম ও পর্দা দর্শকদের আরও আলাদা করে দেয়। আর অভিনেতাদের কাছেও দর্শকরা পরিচয়হীন ভেদাভেদহীন একাকার সত্তায় পরিণত হয়। তাদের স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব অভিনেতাদের কাছে ধরা দেয় না। এই স্তরগত এবং স্থানগত বিচ্ছেদের সাথে থাকে আলো দিয়ে তৈরি করা দূরত্ব। আলো তৈরি করে মঞ্চমায়া। অভিনেতারা থাকেন মঞ্চের আলোকবৃত্তে এবং দর্শকরা অন্ধকারে। যেন দর্শকদের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়াটাই অভিনেতাদের কর্তব্য। এমনকি এক দর্শক থেকে অন্য সব দর্শকদেরও বিচ্ছিন্ন করে দেয় মঞ্চসৃষ্ট অন্ধকার। সঙ্গে অভিনেতাদের সাজসজ্জা ও মেক-আপও দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে পার্থক্যের পর্দা তুলে দেয়।
অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যবর্তী দূরত্বের এই বেড়া ভাঙাই ছিল থার্ড থিয়েটারের মূল লক্ষ্য। সেই আলোচনায় প্রবেশের আগে বুঝে নেওয়া দরকার থার্ড থিয়েটার কী?
থার্ড থিয়েটার: পরিচয়
‘Third Theatre’ নামে মার্কিনি নাট্য সমালোচক রবার্ট ব্রুস্টাইনের একটি বই বেরিয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের থিয়েটারে সেইসময়ে দুটি চরম ধারা চলছিল, “excessive lightness” (বক্তব্যহীন বিনোদনমূলক কমেডি) এবং “excessive heaviness” (বুদ্ধিজীবী নাট্যগোষ্ঠীর গম্ভীরমুখী বক্তব্যপ্রধান নাটক)। তাঁর মত ছিল, একদিকে Reality-পন্থী এবং অন্যদিকে joy-পন্থী এই দুই নাট্যধারার মধ্যে সমন্বয় হওয়া সম্ভব থার্ড থিয়েটারের মাধ্যমে—
Fortunately, America has a third theatre, supported primarily by the young, which combines the youthful properties of intensity, exuberance and engagement.[4]
ডেনমার্কের নাট্যপরিচালক ইউজেনিয়ো বারবা-ও ‘থার্ড থিয়েটার’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। ১৯৭৭ সালে International Theatre Institute Bulletin-এর শীত সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর ‘The Third Theatre’ প্রবন্ধে তিনি বলেন, প্রথম থিয়েটার হল ‘the commercial and subsidized theatre’, দ্বিতীয় থিয়েটার হল ‘the established avagarde’। এই দুই থিয়েটারেরই কিছু কিছু খামতির দিক চিহ্নিত করে তিনি বলেন থার্ড থিয়েটার মানুষের অন্তর্জীবনের সত্য নিয়ে দর্শকদের এক গভীরতার উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। বারবা-র মতে, গ্রোটোউস্কি, পিটার ব্রুক প্রমুখের কাজে থার্ড থিয়েটারের আভাস পাওয়া যায়। বাদল সরকার ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দ্বিজেন্দ্রলাল স্মারক বক্তৃতা’য় এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করেন।
তবে বাদল সরকারের নিজের থার্ড থিয়েটারের ধারা অবশ্য এগুলির থেকে পৃথক। ‘থার্ড’ কথাটি ব্যবহার করা হলে প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটারের প্রসঙ্গও এসে যায়। সেগুলি কী কী? তাঁর দৃষ্টিতে প্রথম থিয়েটার হল গ্রামীণ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকনাট্য। ইংরেজদের প্রোসেনিয়াম থিয়েটারের অনুসরণে তৈরি ও ইউরোপের নাট্যরচনার রীতিকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠা থিয়েটার হল দ্বিতীয় থিয়েটার। বাদল সরকারের মত ছিল, এ দুইয়ের নিজস্ব শক্তি যেমন আছে, দুর্বলতাও আছে। প্রোসেনিয়াম-পন্থী শহরের থিয়েটারে “প্রগতিশীল ভাবধারার যতই প্রকাশ হোক” তা “মধ্যবিত্ত দর্শকের মনে বড়োজোর একটা মানসিক উত্তেজনা’ তৈরি করে। সমাজ পরিবর্তনে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। আর গ্রামীণ থিয়েটার যেন সচলতা বর্জিত এক অনড় প্রতিষ্ঠান, তার মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা আধুনিকতা-বর্জিত, সংস্কারাচ্ছন্ন। গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি সেখানে ধরা পড়ে না[5]।
সুতরাং বাদল সরকারের অভীষ্ট ছিল এই দুইয়ের বাইরে গিয়ে তৃতীয় একটি থিয়েটার প্রবর্তন। অবশ্য এ দুই ধারাকে পুরোপুরি বর্জন করে একেবারে একেবারে অভিনব বা নতুন রীতি তিনি সৃষ্টি করতে চাননি। বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল ‘to create a link between the two’. তাই থার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গে তিনি ‘থিয়েটার অফ সিন্থেসিস’ কথাটি একাধিকবার ব্যবহার করেন।
থার্ড থিয়েটার: প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস
১৯৬৭ সালে গঠিত হয় ‘শতাব্দী’ নাট্যদল। তার প্রায় পাঁচ বছর পর ১৯৭১ এর শেষপ্রান্তে এসে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর সময়েই বাদল সরকার মঞ্চের গণ্ডী ভাঙার কথা ভাবছিলেন।
থার্ড থিয়েটার তার যাত্রা শুরু করেছিল, ১৯৭২ সালের ২৪ অক্টোবর। মধ্য কলকাতার গণেশ এভিনিউয়ে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সমিতির প্রেক্ষাগৃহে গৌরকিশোর ঘোষের ‘সাগিনা মাহাতো’ গল্পের নাট্যরূপের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল থার্ড থিয়েটারের পথ চলা। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং বাদল সরকার। এতে অঙ্ক আর দৃশ্যের ভাগ মুছে গেল। সময়ক্রম গেল ভেঙে। জোর দেওয়া হল দলগত অভিনয়, মূকাভিনয়, ছন্দোবদ্ধ গতিভঙ্গি, গান আর নাচের ওপর। উচ্চারিত সংলাপ বরং গুরুত্ব পেল কম, foregrounded হল দৃশ্যগত উপস্থাপনা, অভিনেতাদের দেহগত বিন্যাস-ছন্দ ও Composition.
সেট সম্বন্ধেও থার্ড থিয়েটারে যথাসম্ভব minimalistic approach নেওয়া হয়েছিল। দু-তিন জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল কিছু নিচু বাক্সজাতীয় প্ল্যাটফর্ম। চেয়ারগুলিকে তাঁরা হলের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিছু রেখেছিলেন স্টেজের ওপরে। মাঝে অভিনয়ের জন্য ফাঁকা জায়গা রেখে চারপাশে দর্শকদের বসার জায়গা হল। দর্শকাসনের ফাঁকে ফাঁকেও প্রচুর জায়গা রাখা হয়েছিল। ফলে অভিনেতারা যে শুধু মধ্যস্থলের ফাঁকা জায়গায় অভিনয় করেছিলেন তা নয়, দর্শকদের আসনের পাশ দিয়েও বিস্তৃত করে নিয়েছিলেন তাঁদের অভিনয়ক্ষেত্রকে। যাতে, দর্শকদের মনে হয় তাঁরা অভিনয়েরই অন্তর্গত। এইভাবেই শুরু হয়েছিল, থার্ড থিয়েটার তথা ‘অঙ্গনমঞ্চ’-এর অভিনয়।
‘সাগিনা মাহাতো’ আগে প্রোসেনিয়াম মঞ্চেও অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু ABTA হলে অভিনয়ের পর থেকেই প্রোসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে বাদল সরকার থার্ড থিয়েটারকেই সমাজ পরিবর্তনের বিকল্প হাতিয়ার করে নিতে চাইলেন। বাদল সরকারের কথায় অঙ্গনমঞ্চের সংজ্ঞা হল –
অঙ্গনমঞ্চের রূপটি হল একটি ঘনিষ্ঠ থিয়েটারের, যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক দর্শক অভিনেতাদের খুব কাছে আছে, একই তলে আছে, একই আলোয় আছে; যেখানে দর্শকদের সামনে ছাড়াও পাশে, পিছনে যাওয়া যাচ্ছে, দর্শকদের চোখে চোখ রেখে একান্তে কথা বলা যাচ্ছে, দর্শকদের ধরাছোঁয়ার আওতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে[6]।
‘সাগিনা মাহাতো’র অভিনয়ের পরের বছর জুনে অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের তিনতলায় ‘শতাব্দী’ একটি মেঝে পায় অভিনয়ের জন্য। অ্যাকাদেমিতে অঙ্গন মঞ্চের অভিনয় শুরু হয় ১৯৭২-এর ১২ নভেম্বর থেকে বাদল সরকারেরই লেখা ‘স্পার্টাকুস’ নাটক দিয়ে। প্রতি রবিরার এই অভিনয় হত।
অ্যাকাদেমিতে অঙ্গনমঞ্চের বৈশিষ্ট্য
বাদল সরকার তাঁর ‘Third Theatre’ বইতে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনটি ভাগে ভেঙে আলোচনা করেছেন।
১) আলো:
ওপর থেকে বিশেষ ধরনের ‘শেড’ দেওয়া ষোলোটি বাল্ব জ্বলত– ১০০, ৬০ এবং ৪০ ওয়াটের। ‘ডিমার’, ‘স্পট’ ইত্যাদির ব্যবহার না করে সাধারণ ঢালা আলোর ব্যবহার দর্শক-অভিনেতা ব্যবধান কমানোর একরকম নিরীক্ষা হিসেবেই নেওয়া হয়েছিল।
ইতিপূর্বে ‘সাগিনা মাহাতো’-র অভিনয় চলাকালীন একটি বিশেষ আকর্ষণীয় মুহূর্তে এবিটিএ হলে আলোর ফিউজ পুড়ে যাওয়ায় নাটকের স্পটলাইট নিভে গেছিল। ফলে আধ মিনিট সম্পূর্ণ অন্ধকারে এবং মিনিট পাঁচেক হলের সাধারণ টিউবলাইটের আলো ইত্যাদিতেই অভিনয় চলেছিল। বাদল সরকার পরে দর্শকদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছিলেন তাঁরা এই আলোর পরিবর্তন নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, অভিনয় যেমন দেখার দেখে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল এই সাধারণ আলোর ব্যবহারই হয়তো অঙ্গনমঞ্চের নাটক দেখায় দর্শকদের সক্রিয়তাকে বাড়িয়ে তুলবে।
২) আসন:
অভিনয়ে কোনো চেয়ারের ব্যবহার হত না। ব্যবহার হত ‘লেভেল’ বা ‘স্তর’-এর। তিনটি পৃথক উচ্চতার বেঞ্চ ধরনের আসবাব ব্যবহার করা হয়েছিল।
৩) ধ্বনি:
অ্যাকাদেমির হলটিতে প্রতিধ্বনি হত বলে খালি দেয়ালের ওপর তাঁরা ভাঁজ করা চটের পর্দা আটকে দিয়েছিলেন।
দর্শকদের আসন তাঁরা প্রতি নাটকে আলাদা আলাদাভাবে বিন্যাস করতেন। বাদল সরকারের ‘থার্ড থিয়েটার’ বইটিতে ‘সাগিনা মাহাতো’, ‘স্পার্টাকুস’ এবং অঙ্গনমঞ্চে করা ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের দর্শকাসন বিন্যাস ও মঞ্চ পরিকল্পনার নকশা দিয়েছেন। ‘প্রস্তাব’ নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা ছিল এইরকম—
Platforms were laid in the shape of a ‘T’ on the floor. The spectators were let in one by one, and they found me spread-eagled on the platform, blindfolded, with my wrists and ankles tied with strong ropes. The ropes were stretched to the four corners of the room, with the other ends secured to the walls. There was one strong light on the top of the platform.[7]
এইভাবে মঞ্চ-পরিকল্পনার ফলে দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হত, তা থার্ড থিয়েটারের এক জোরালো দিক বলেই মনে করেছিলেন বাদল সরকার।
থার্ড থিয়েটার: প্রকারভেদ
কেবল অঙ্গনমঞ্চের কথা বললে ‘থার্ড থিয়েটার’ আঙ্গিকটির পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। অঙ্গনমঞ্চের পাশাপাশি থার্ড থিয়েটারের আরেকটি রূপ হল মুক্তমঞ্চ। নাম থেকেই স্পষ্ট, ‘মুক্তমঞ্চ’ হল চার দেওয়ালের বাইরে খোলা জায়গায় থার্ড থিয়েটারের অভিনয়ক্ষেত্র। ১৯৭১ সাল নাগাদ কার্জন পার্ক বা সুরেন্দ্রনাথ পার্কে সিলুয়েট নাট্যগোষ্ঠী প্রতি শনিবার খোলা মাঠে অভিনয় করতে আরম্ভ করে। ‘শতাব্দী’ ‘সিলুয়েট’কে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। অন্যদিকে ‘সিলুয়েট’ও ‘শতাব্দী’কে সুরেন্দ্রনাথ পার্কে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তাতে সাড়া দিয়ে ১৯৭৩-এর মার্চ মাসে ‘শতাব্দী’ সেখানে ‘স্পার্টাকুস’ অভিনয় করে। প্রায় পাঁচশোরও বেশি লোক নিস্তব্ধ হয়ে সে নাটক দেখেছিল। বাদল সরকার নিজে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান থাকলেও ‘স্পার্টাকুস’ নাটকে মাঠের ঘাস ও ধুলোর আস্তরণ এবং পাথরের ছোটখাটো আঁচড়ের দাগ দাসচরিত্রের অভিনেতাদের আরও জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। এই মুক্তমঞ্চকে থার্ড থিয়েটারেরই একটি ‘সম্প্রসারিত রূপ’ হিসেবে দেখেছেন অনেকে।
সাফল্য–ব্যর্থতার খতিয়ান
প্রোসেনিয়ামকে বাদল সরকারের মনে হয়েছিল ‘একটি মধ্যবিত্ত বিপ্লবী প্রয়াস’। তবে অঙ্গনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চও শেষপর্যন্ত ‘একটি মধ্যবিত্ত বিপ্লবী প্রয়াস’-এই সীমাবদ্ধ থাকল কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ‘শতাব্দী’র প্রতি রবিবারের অভিনয় বা ১৯৮৬-এর মার্চ মাসে মাত্র তিনদিনের গ্রাম সফর কি সমস্ত নিপীড়িত বঞ্চিত জনসাধারণের সমস্যা আদৌ মেটাতে পারল বা তাদেরকে কি আদৌ সচেতন করতে পারল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে?
অবশ্য কেবল থার্ড থিয়েটার নয়, যে কোনও শিল্পকলাই শেষপর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে কিনা সে নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পরিসর তৈরি করা যায়। সেই তর্কে না গিয়েও বলা যায় থার্ড থিয়েটার এক ব্যতিক্রমী থিয়েটার-প্রয়াস। দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে স্থানিক-মানসিক ও শিল্পকৌশলগত দূরত্বকে কমিয়ে আনার যে দর্শনে বাদল সরকার বিশ্বাসী ছিলেন তা আগামী দিনের থিয়েটার চর্চাকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে, নানামাত্রায়। দর্শককে কীভাবে থিয়েটারের অন্তর্গত এক অস্তিত্ব করে তোলা যায়, কীভাবে মুছে দেওয়া যায় দর্শক-অভিনেতা বিচ্ছিন্নতা— এই চিন্তন যখনই যেভাবে উঠে এসেছে বাংলা থিয়েটারে, তার সঙ্গে লগ্ন থেকেছে বাদল সরকারের অনন্য থিয়েটার-দর্শন।
[1] এবং ইন্দ্রজিৎ-কে অ্যাবসার্ড গোত্রের নাটক বলা যায় কিনা এ নিয়ে যদিও বিতর্কের অবকাশ আছে।
[2] পবিত্র সরকার, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ (কলকাতা: দে’জ, ২০০৮), ৩২৫।
[3] সরকার, ৩২৫।
[4] নিউ ইয়র্কের Alfred A Knopf প্রকাশিত, ৭-৮।
[5] Badal Sircar, The Third Theatre (Calcutta: Published by the author, 1978), 16.
[6] বাদল সরকার, থিয়েটারের ভাষা (কলকাতা: অপেরা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), ৫৮।
[7] Sircar, 73.
থার্ড ক্লাস
অর্ক সান্যাল
বাদল বেলা
১ ৯ ২ ৫ সাল। ঠনঠনিয়া কালী বাড়ির কাছে এক বাদলার দিনে জলমগ্ন কলকাতায় জন্ম নিলেন বাদল সরকার । স্কুল ,কলেজ ,কর্মস্থল, পেশার গন্ডি পেরোতে পেরোতে তিনি পেরিয়ে গেলেন শিল্প মাধ্যমের সমস্ত গন্ডীও। হাতে তুলে নিলেন গান্ডীব , অস্ত্র থিয়েটার। চুরমার করে দিলেন প্রসেনিয়ামের সমস্ত দেওয়াল। নাটক এল রাজপথে , গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তিনি নাকি উচ্চ শিক্ষা জীবনে সব পরীক্ষাতেই তৃতীয় হয়েছেন । আবার সেই তিনিই তৈরী করেছেন থার্ড থিয়েটার।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে ভারতে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স’ অ্যাসোসিয়েশন (PWA) এবং ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (IPTA)-এর মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলন পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক সংগঠন এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে মঞ্চে স্থান দিত। নাট্যকাররা ধীরে ধীরে মঞ্চকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন আধুনিক মানুষের মানসিক ও সামাজিক সংকটকে অনুসন্ধান করার জন্য।
বাদল সরকার কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রসেনিয়াম মঞ্চকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে তিনি সলিউশন এক্স (১৯৫৬), টম, ডিক, হ্যারি (রাম, শ্যাম, জাদু, ১৯৫৭), বড় পিসিমা (১৯৫৯) এবং শনিবার (১৯৫৯)-এর মতো নাটক রচনা করেন।
তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল তাঁর পরীক্ষামূলক অন্বেষণ। এই সময়ে তিনি সমকালীন ভারতীয় সমাজের গুরুতর সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এই পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল এবং ইন্দ্রজিৎ (১৯৬২), বাকি ইতিহাস (১৯৬৫), ত্রিংশ শতাব্দী (১৯৬৬) এবং পাগলা ঘোড়া (১৯৬৭)।
যদিও ১৯৬৭ সালে তিনি নিজের নাট্যদল ‘শতাব্দী’ গঠন করেন এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা, নির্দেশনা ও প্রযোজনা শুরু করেন,তবুও তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকেন যে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চের সীমাবদ্ধতা।
প্রসেনিয়াম প্রযোজনা অর্থনৈতিকভাবে যেমন অচল হয়ে পড়ছিল, শৈল্পিক ভাবেও তেমনি সীমাবদ্ধ ছিল। নাট্যদলগুলোর পক্ষে নিয়মিত অডিটোরিয়াম ভাড়া করে নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সময়ের প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ না করে বাদল সরকার প্রসেনিয়াম মঞ্চের ধারণাকেই প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তিনি খুঁজতে থাকেন এই থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা কোথায়? কীভাবে অভিনেতারা সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন? সিনেমার যুগে থিয়েটার কীভাবে টিকে থেকে তার সামাজিক ও শিল্পগত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে? কীভাবে প্রোসেনিয়াম প্রযোজনার আর্থিক সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব?
বাদল সরকারের ‘তৃতীয় থিয়েটার’ ধারণা ছিল এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার এক প্রচেষ্টা।
প্রোসেনিয়াম মঞ্চের ব্যয়বহুল কাঠামো বা গ্রামীণ লোকনাট্যের ঐতিহ্যিক রূপের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তৃতীয় থিয়েটার। এটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক নাট্য-দর্শন, যেখানে অভিনয়শিল্পীর শরীর, দর্শকের অংশগ্রহণ এবং খোলা আকাশই হয়ে উঠেছিল নাটকের প্রধান অবলম্বন।
তৃতীয় থিয়েটারের মূল লক্ষ্য ছিল থিয়েটারকে বাজার থেকে বের করে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। নাটক প্রোসেনিয়ামে নয়; মাঠে, পার্কে, স্কুলের আঙিনায় বা রাস্তার মোড়ে। আলো, সাউন্ড, সেট, বিশাল কস্টিউম—কিছুই প্রয়োজন নেই। দর্শক আর অভিনেতার মধ্যে কোনো দেওয়াল নেই। সবাই একই সমতলে, একই আলোয়। দর্শক অবাধে ঢুকতে বা বের হতে পারে; কখনো কখনো নাটকের অংশও হয়ে ওঠে। এই নাটক বিনোদনের জন্য নয়; সচেতনতা ও প্রতিবাদের জন্য।
থার্ড থিয়েটার – অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
অর্থনীতিতে উৎপাদনের চারটি উপাদান —ভূমি (land), শ্রমিক (labour), পুঁজি (capital), ও উদ্যোক্তা (organiser)। এই কাঠামোয় তৃতীয় থিয়েটারকে বিশ্লেষণ করলে একটি অভিনব চিত্র ফুটে ওঠে।
ভূমি: প্রোসেনিয়াম নাটকে অডিটোরিয়াম ভাড়া বিরাট খরচ। কিন্তু বদল সরকার বললেন, খোলা রাস্তা বা পার্কই যথেষ্ট। অর্থাৎ ‘ভূমি’ এখানে মালিকানাহীন, সাময়িক এবং সবার।
পুঁজি: প্রচলিত নাটকে আলো, সেট, কস্টিউমে প্রচুর টাকা লাগে। তৃতীয় থিয়েটারে এই পুঁজির প্রয়োজন নেই। একটি ছাতা, একটি হাতপাখা, অথবা খালি শরীর দিয়েই দৃশ্য তৈরি হয়। নাটক তৈরি হয় মানুষের শরীর ও কণ্ঠের শক্তিতে, টাকার জোরে নয়।
শ্রমিক : তৃতীয় থিয়েটারের মূল ভিত্তি হল শ্রম—অভিনেতার দেহ। অভিনেতার শরীরই একমাত্র উপাদান, যেখান থেকে মঞ্চ, শব্দ, ছবি, ছন্দ সবকিছু তৈরি হয়। যেমন—অভিনেতারা একসাথে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের মতো চলাফেরা করলে মনে হয় বিশাল মেশিন চলছে।
উদ্যোক্তা: সম্পূর্ণ শূন্য নয়। বদল সরকার ও তাঁর দল “শতাব্দী” সংগঠক হিসেবে কাজ করেছে—রিহার্সাল, নাটক সাজানো, ভ্রমণ, দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি সামলেছে। কিন্তু এটি কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোক্তার কাজ নয়; বরং একধরনের সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব।
অতএব, উৎপাদনের চার উপাদানের মধ্যে বদল সরকারের নাটকে প্রায় একমাত্র সক্রিয় উপাদান হল শ্রমিক —শরীর। ভূমি ও পুঁজি প্রায় বিলুপ্ত; উদ্যোক্তা আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা নয়, বরং সাংস্কৃতিক সংগঠক।
প্রোসেনিয়াম থিয়েটারে দর্শক অন্ধকারে বসে থাকে, অভিনেতা আলোয় থাকে—এক দূরত্ব তৈরি হয়। বদল সরকার এই বিভাজন ভেঙে দেন। সবাই একই আলোয়, একই জায়গায়, সমানভাবে উপস্থিত।
লোকনাট্যে গ্রামীণ জীবনের ঐতিহ্য ও গানের আধিপত্য থাকে। তৃতীয় থিয়েটার গ্রামীণ নয়, আধুনিক রাজনৈতিক প্রশ্নে আবদ্ধ, শহর ও গ্রামের সেতুবন্ধন ঘটায়।
অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রোসেনিয়াম বা লোকনাট্য উভয়ই কিছু না কিছু খরচসাপেক্ষ। কিন্তু তৃতীয় থিয়েটার প্রমাণ করে, নাটক করতে টাকা লাগে না—শুধু অভিনেতার শরীর ও দর্শকের উপস্থিতি যথেষ্ট।
তৃতীয় থিয়েটারের অন্যতম বড় শক্তি ছিল দর্শক–অভিনেতার সম্পর্ক। দর্শক নাটকের বাইরে নয়, ভেতরে।নাটক চলাকালীন যে কেউ মাঝপথে ঢুকতে বা বের হতে পারে। অনেক সময় দর্শক নাটকের সংলাপে প্রতিক্রিয়া জানায়, এমনকি অংশগ্রহণও করে। এতে নাটক একপাক্ষিক ‘দেখানো’ নয়, বরং দ্বিমুখী ‘আলাপ’। নাটক শেষ হলে বদল সরকার ও তাঁর দল একটি কাপড় বিছিয়ে দিতেন। দর্শক স্বেচ্ছায় অনুদান দিত। ধনী শহরে যেমন, তেমনি দরিদ্র গ্রামে একইভাবে অর্থসংগ্রহ করা হত। ফলে অর্থের ভিত্তিতে কোনো বিভেদ তৈরি হতো না—সবার অবদান সমান মর্যাদা পেত। এটি ছিল নাটকীয় অর্থনীতির এক অভিনব গণতান্ত্রিক রূপ।
অনেকে বলেন, বদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার জেরজি গ্রোটোস্কির Poor Theatre থেকে প্রভাবিত। সত্যিই কিছু মিল আছে—ন্যূনতম প্রপস, দেহনির্ভর অভিনয় ইত্যাদি। কিন্তু পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ।গ্রোটোস্কির নাটকে অভিনেতাদের কড়া শারীরিক প্রশিক্ষণ (ব্যালেট, ড্রামা স্কুল ইত্যাদি) দরকার। বদল সরকারের মতে তাঁর থিয়েটার গ্রোটোস্কির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের । দৈনন্দিন শরীরের স্বাভাবিক ভঙ্গি, কণ্ঠ ও অভিব্যক্তি দিয়েই অভিনয় সম্ভব।
তাই তাঁর থিয়েটার ছিল আরও গণতান্ত্রিক—যে কেউ অভিনেতা হতে পারে, কোনো শারীরিক এলিটিজম নেই।
কৈফিয়ৎ
থার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গে বাদল বাবু বলছেন ,
“ইংরাজিতে বলে ‘হিয়ার-নাউ’। দর্শক এবং অভিনেতা একই জায়গায় একই দিনে একই সময়ে উপস্থিত হচ্ছে। এই যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যাপারটা ঘটছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ত। সিনেমা কোনোদিন নকল করতে পারবে না।
প্রথমেই মাথায় আসে তিনটি বেড়ার কথা। এক, দূরত্বের বেড়া। সবাই একদিকে বসেছে বলে শেষ সারিটা অনেকটা পিছনে। তারা তিনদিকে বা চারদিকে বসলে অঙ্কের নিয়মেই অনেকটা কাছে চলে আসতো। দুই,স্তরের বেড়া বা বাধা। স্টেজটা একটা স্তরে, অডিটরিয়াম আর একটা স্তরে এবং ব্যালকনি ততীয় আরও একটা স্তরে। তিন, আলো ও অন্ধকারের বাধা। থিয়েটার হচ্ছে আলোতে এবং দর্শক আছে অন্ধকারে লুকিয়ে। সেটা অদ্ভুত একটা সোনার পাথরবাটি গোছের ব্যাপার। দর্শকদের জন্যেই সব কিছু করা কিন্তু দর্শকরা যেন উপস্থিত নেই এই ভান করে অভিনেতারা। অভিনয় করে যান। এটা যে কী করে সম্ভব হয় আমি জানি না। তাহলে দর্শকদের আমরা যে ভূমিকা দেখি তা হল, স্টেজে প্রাইভেট কিছু জিনিস হচ্ছে তা তোমার দেখার কথা নয়, কিন্তু লুকিয়ে দেখছ। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবহার করব অথচ এরকম একটা কন্ডিশন রাখব, তাতো হয় না। তখন যে চিন্তা আসে মাথায়, এই বাধাগুলো দূর করতে গেলে নেমে আসতে হবে। নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে অভিনয় ক্ষেত্রটা ভাগ করে নিতে হবে। একই ঘরের মধ্যে দর্শকও আলোতে আছে, আমরাও আছি। একই স্তরে আমরাও মেঝেতে দর্শকও মেঝেতে বসে কিংবা মেঝেতে চেয়ার পেতে বসে। এভাবেই বাধাগুলো দূর করতে হয়। একটা ইন্টিমেট থিয়েটার হয়তো তাতে হয়ে যায়, কম দর্শক দেখছে। তবে মাঠে গিয়ে মুক্তমঞ্চে করলে সেই ইন্টিমেট থিয়েটারটা আর থাকে না। এই দিক থেকে থিয়েটারকে অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ ও শক্তিশালী করবার জন্য নেমে এসেছিলাম। নেমে এসেই উপলব্ধি করলাম যে থিয়েটারে দামি এবং ভারি জিনিসগুলো আর দরকার হচ্ছে না। সেট খাটাবার আর দরকার নেই, তাতে দর্শকের দৃষ্টি আরো ব্যাহত করবে। প্রসেনিয়ামে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করা হয়-এটা মঞ্চ নয়, এটা চায়ের দোকান কিংবা শোবার ঘর-এইসব ভাগ অঙ্গনমঞ্চে আর দরকার নেই। তার মানে দর্শকের কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করা আরম্ভ হল। এক ধরনের অডিয়েন্স পার্টিসিপেশন শুরু হল তার কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করতে। তাতে ওই সেট, স্পট লাইটের যাদুর আর প্রয়োজন হল না, বরং প্রয়োজন হল অভিনেতার দেহ ও মনকে ব্যবহার করা। তাতে আমাদের সম্পূর্ণ থিয়েটারটাই বদলে গেল। কেমন করে হল? আমি তিনটে কথা ব্যবহার করি-পোর্টেবল, ফ্লেক্সেবল এবং ইনএক্সপেনসেবল।
যেখানে মানুষ আছে সেখানেই ‘ফ্রি’ কথাটি ভারি মজার। দুটো মানে আছে ফ্রি কথাটির। একটা মানে হচ্ছে- মাগনা। দেখতে গেলে পয়সা লাগে না। এটাই প্রচলিত অর্থ। সবচেয়ে প্রথম এটাই মাথায় আসে সবার। আর একটা মানে আছে যেটায় অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। ফ্রি মানে সেখানে বাঁধন নেই, মুক্ত। আমি দুটো অর্থেই দেখছি ফ্রি-থিয়েটার কথাটি প্রযোজ্য। মাগনা মানে সবচেয়ে গরীব লোকও আসতে পারে, আর বন্ধন নেই মানে হচ্ছে কোনো শর্ত নেই। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা স্থাপিত হতে পারে। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটা ব্যবহারিক হতে পারে কিন্তু মানবিক সম্পর্ক বলা চলে না। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষমতা আছে মানবিক-ক্রিয়া হয়ে ওঠার। সেটা আমাদের থিয়েটারে হতে পারছে। দর্শক আসছে ফ্রি, আমরা তাদের ডাকছি ফ্রি। এখানে কোনো বন্ধন নেই।
কনটেন্ট ইজ দ্য স্টারটিং পয়েন্ট। আগে আমরা ভাবি কনটেন্টটাকে সবচেয়ে তীব্রভাবে পৌঁছে দিতে পারে এইরকম ফর্ম, তখন সেটা গ্রহণ করি। কাজেই, প্রত্যেকটাই নাটকে আমাদের নতুন করে ফর্ম খুঁজতে হয়। তাই এ প্রসঙ্গে যদি আমায় কেউ বলে এটা কি এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার? আমি বলি, না’ এক্সপেরিমেন্ট জীবনে করিনি। এক্সপ্লোর করেছি, খুঁজেছি, অনুসন্ধান করেছি, তাই প্রত্যেকটা নাটক আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। কোনো বিশেষ ফর্মের কাছে আমরা দায়বদ্ধ নই। একটা নতুন ফর্ম বা নাট্যশৈলী সৃষ্টি করব, এটা আমাদের একটুও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ওই কথাটাকে সবচেয়ে তীব্রভাবে বলা, তার জন্যে এক্সপ্লোরেশন শব্দটাই যথেষ্ট।”
কার্টেন কল
তৃতীয় থিয়েটার আসলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এটি প্রমাণ করে যে নাটক কেবল প্রোসেনিয়ামের সম্পত্তি নয়; নাটক এমন এক অভিজ্ঞতা, যা খোলা আকাশে, মানুষের ভিড়ের মাঝখানেই সম্ভব। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বললে—তৃতীয় থিয়েটার ভূমি, পুঁজি ও উদ্যোক্তার আধিপত্য কমিয়ে দিয়ে শ্রম বা মানবদেহকে কেন্দ্রীয় উপাদান বানিয়েছে।
বাদল সরকারের থিয়েটার আমাদের মনে করিয়ে দেয়: শিল্পের আসল শক্তি টাকা বা প্রযুক্তিতে নয়, বরং মানুষের শরীর, কণ্ঠ ও সম্মিলিত চেতনার ভেতরেই নিহিত। এ কারণেই তাঁর নাটক আজও সমান প্রাসঙ্গিক—যতদিন মানুষ বঞ্চিত, শোষিত, কিংবা সত্য খুঁজে ফিরবে, ততদিন তৃতীয় থিয়েটার থাকবে তাদের কণ্ঠস্বর। আর দুঃসাহস দেখিয়ে প্রায় কিছু না জেনে বুঝে লিখতে চেষ্টা করা , বলা ভালো খুঁজতে চেষ্টা করা এই থার্ড ক্লাস লেখার লেখক বাদলের মেঘ সরিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করবো ভোমা কে।
“- কে ভোমা ?
- একটা মানুষ। ভোমা ভাঙে না। ভোমা সৃষ্টি করে। ভোমা কে ভাঙি আমরা।
- কি বলছো বুঝতে পারছি না। কে ভোমা ?
- ভোমা জঙ্গল। ভোমা আবাদ। ভোমা গ্রাম । ভারতবর্ষের বারোআনা মানুষ গ্রামে বাস করে। কোটি কোটি ভোমা। ভোমাদের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। শহরে।
- রক্ত খেয়ে ?
- হ্যাঁ। ভোমারা যদি ভাত খেত ,আমরা খেতে পেতাম না। বোমার লাল রক্ত সাদা জুঁই ফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের ভাতের থালায়। রোজ ,দুবেলা ।” তথ্য সূত্র
- তথ্যচিত্র – ” বাদল সরকার , প্রসার ভারতী আর্কাইভস “
- মিছিলে বাদল সরকার – অদ্রীশ বিশ্বাস
- Badal Sircar : people’s playwright – Śailajā Vāḍīkara
- Exploring the Aesthetics of the ‘Third Theatre’: A Study of Badal Sircar’s Indian History Made Easy – Victor Mukherjee
- Sircar, Badal. On Theatre. Kolkata: Seagull Books, 2009. Print.
- Wikipedia
বাদল সরকারের পথনাটক ও পাগলা ঘোড়া: আমার চোখে এক বিশ্লেষণ
দীপ্তেশ মুখার্জী
বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাসে বাদল সরকার এমন এক নাম, যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। যিনি নাটককে শুধু মঞ্চসজ্জা, আলো, দর্শকের সামনে অভিজাত প্রেক্ষাগৃহের অভ্যস্ত উপস্থাপনায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং রাস্তায়, মাঠে, পাড়ায়, মেলায় সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহসী ও নবতর ধারা “তৃতীয় থিয়েটার” আজও অনন্য। তাঁর পাগলা ঘোড়া নাটক ও পরবর্তী পথনাট্য রচনাগুলি আমার চোখে কেবল নাটক নয়, সমাজ-রাজনীতির গভীর ভাষ্য বাংলা নাটক দীর্ঘদিন ধরে proscenium মঞ্চনির্ভর ছিল। যেখানে দর্শকরা বসবেন এক পাশে, আর অভিনয় চলবে আলোর প্রভা ও সাজসজ্জার আবহে অন্য পাশে। এই ব্যবধানই ছিল নাটকের মূল ভরকেন্দ্র। কিন্তু বাদল সরকার সেই প্রথা ভেঙে ফেললেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নাটক শুধু শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত বা প্রেক্ষাগৃহে আসতে সক্ষম মানুষের সম্পত্তি নয়। নাটক হলো সবার রাস্তার শ্রমিক, মজুর, বেকার যুবক, গ্রামের কৃষক সবাইয়ের। আর তাই তিনি নাটককে টেনে আনলেন খোলা আকাশের নিচে, পথের ধুলোয়, মানুষের ভিড়ে।
আমার চোখে এই সিদ্ধান্ত কেবল শিল্পের নয়, এক রাজনৈতিক অবস্থান। কারণ এর ভেতরে আছে শ্রেণি-বিভাজন ভাঙার তাগিদ। নাটককে গণতান্ত্রিক করে তোলার এক সাহসী পদক্ষেপ।
পাগলা ঘোড়া: স্বপ্ন, মৃত্যু ও বেঁচে থাকার ভাষা
বাদল সরকারের সবচেয়ে আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে পাগলা ঘোড়া নিঃসন্দেহে অন্যতম। প্রথম দর্শনে এটি চার মৃত মানুষের কাহিনি। তারা কবর থেকে উঠে এসে কথা বলতে শুরু করেমৃত্যুর পরও যেন তাদের আত্মা মুক্তি পায়নি। প্রতিটি চরিত্রই এক একটি সামাজিক প্রতীক: যুদ্ধ, দারিদ্র্য, জাতপাত, শোষণ সব মিলেমিশে আছে তাদের অভিজ্ঞতায়।
আমার চোখে পাগলা ঘোড়া এক ভয়ঙ্কর প্রতীকী নাটক, যেখানে মৃত্যু আসলে জীবনের অসহায়তাকে প্রকাশ করে। সমাজ মানুষকে যেভাবে পিষে ফেলে, মানুষকে তুচ্ছ করে দেয়, সেই অভিজ্ঞতাই মৃত্যুর পরেও চরিত্রগুলির মধ্যে বেঁচে থাকে। তারা মুক্তি চায়, কিন্তু মুক্তি পায় না।বাদল সরকার এখানে নাট্যরীতিকে ভেঙেছেন। সংলাপগুলো কবিতার মতো, ভাঙা-গড়া ছন্দে। দর্শককে গল্পের ধারাবাহিকতা নয়, বরং অনুভব ও প্রতীকের জগতে টেনে নিয়ে যায়। চারটি চরিত্রের কথোপকথন ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে যায় এই প্রশ্নে: জীবনে কীভাবে আমরা স্বাধীনতা হারাই, আর মৃত্যুতেও কীভাবে মুক্তি মেলে না?
আমার কাছে পাগলা ঘোড়া আসলে এক দার্শনিক নাটক। এটি আমাদের শেখায়, মৃত্যু চূড়ান্ত সমাপ্তি নয়, বরং জীবনের অমানবিক শৃঙ্খলাকে ভাঙতে না পারার আর্তনাদ।
বাদল সরকারের ভাবনা ছিল, যদি নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়, তবে সেটিকে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে সরাসরি। আর তাই জন্ম নেয় তাঁর পথনাটক। ভোমা, ভূমির ছেলে, মিছিল প্রভৃতি নাটক রাস্তায় অভিনীত হয়।
এখানে নেই জাঁকজমক, নেই বড় বাজেট। শুধু অভিনেতাদের দেহ, কণ্ঠ, আবেগ আর দর্শকের অংশগ্রহণই মূল শক্তি। দর্শকরা মাটিতে বসে থাকেন, অভিনেতারা তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেন। ফলে দর্শক আর অভিনেতার দূরত্ব মুছে যায়।আমার চোখে এই ধারা কেবল নাটক নয়, আন্দোলন। এটা সাধারণ মানুষের সমস্যাকে মঞ্চে আনার সাহস। যখন রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ সাধারণ মানুষের দুঃখ-অভিযোগ শোনে না, তখন নাটকই হয়ে ওঠে তাদের কণ্ঠস্বর।
মিছিল: প্রতিবাদের নতুন রূপ
বাদল সরকারের পথনাটকগুলির মধ্যে মিছিল একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি এক সমবেত চলার প্রতীক। নাটকটিতে ব্যক্তির নয়, জনতার শক্তি মুখ্য। মানুষ একত্রে হাঁটছে, প্রতিবাদ করছে, প্রশ্ন তুলছে।
আমার চোখে মিছিল হলো সেই কণ্ঠস্বর, যা দমন করা যায় না। রাষ্ট্র কতই না চেষ্টা করুক, প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে মানুষের ভেতরে ভেতরে। নাটকটির সংলাপ ও ভঙ্গিমা স্পষ্ট করে দেয় বাদল সরকার চেয়েছিলেন এক জাগ্রত সমাজ, যে সমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিছিল গড়ে তুলবে।প্রতীকী ঘোড়া ও মিছিলের শক্তি
এখানে একটি মিল খুঁজে পাই পাগলা ঘোড়া ও মিছিল নাটকের মধ্যে। প্রথমটিতে ‘ঘোড়া’ প্রতীক, উন্মাদনা ও অসহায়তার প্রকাশ। দ্বিতীয়টিতে ‘মিছিল’ প্রতীক, মানুষের ঐক্য ও শক্তির প্রকাশ। অর্থাৎ, একদিকে মৃত্যু ও বেদনায় ভরা কণ্ঠস্বর, অন্যদিকে বেঁচে থাকার, লড়াই করার অঙ্গীকার।
আমার দৃষ্টিতে বাদল সরকারের নাট্যযাত্রা এই দুই প্রতীকের ভেতরে নিহিত হতাশা থেকে আশা, মৃত্যুর অন্ধকার থেকে লড়াইয়ের আলো।
সমাজ-রাজনীতি ও বাদল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি-
বাদল সরকার যে সময়ে লিখছিলেন, তখন ভারতবর্ষে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, দমননীতি। সমাজে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভয় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর নাটকগুলো হয়ে ওঠে প্রতিরোধের ভাষা।আমার চোখে তিনি ছিলেন এক রাজনৈতিক শিল্পী। সরাসরি দলীয় রাজনীতির অংশ না হয়েও তাঁর নাটকগুলো রাজনৈতিক অর্থ বহন করে। তিনি দেখিয়েছেন থিয়েটার মানে শুধু বিনোদন নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।
বাদল সরকারের নাটকের প্রভাব
আজও যখন আমরা কোনো পাড়ার মোড়ে, কলেজ ক্যাম্পাসে, গ্রামে-গঞ্জে পথনাটক দেখি, তখন তার শিকড় খুঁজে পাই বাদল সরকারের সৃষ্টিতে। তাঁর নাটক আমাদের শিখিয়েছে, কম খরচেও বড় নাটক সম্ভব। শুধু প্রয়োজন শিল্পীর নিবেদন আর মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা।আমার মনে হয়, বাদল সরকার আমাদের শিখিয়েছেন শিল্পীর দায়িত্ব কী। শুধু সৃজন নয়, সমাজকে প্রশ্ন করা, প্রতিবাদ তোলা, মানুষকে ভাবানো এই দায়িত্বও শিল্পীর।বাদল সরকারের পাগলা ঘোড়া ও পথনাটক, বিশেষত মিছিল, আমার চোখে দুটি ভিন্ন মাইলফলক। পাগলা ঘোড়া আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মৃত্যু আর জীবনের সীমারেখা ভেঙে মানুষ কেবল এক আর্তনাদের প্রতীক। আর মিছিল আমাদের দেখায়, মানুষ যখন একত্রে দাঁড়ায়, তখন কোনো শক্তিই তাকে রুখতে পারে না।তাঁর এই নাট্যধারা আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ সমাজে এখনো দমন আছে, অন্যায় আছে, শোষণ আছে। আর যতদিন এই বাস্তবতা থাকবে, ততদিন বাদল সরকারের নাটক আমাদের অনুপ্রাণিত করবে রাস্তার ধুলোয় দাঁড়িয়ে, আকাশের নিচে বসে, সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে।আমার চোখে বাদল সরকারের নাটক হলো জীবনের প্রতি এক অঙ্গীকার“আমরা চুপ করব না, আমরা মিছিল গড়ব, আমরা প্রতিবাদ করব।”
এখনও বাদল
অসিতা সেন
আমরা যারা দুহাজার সাল পরবর্তী সময়ে থিয়েটার করতে এসেছিলাম, তারা বাংলা থিয়েটারের প্রনম্য নাট্যকারদের প্রায় কাউকেই দেখিনি। আমরা শ্রী উৎপল দত্ত, আচার্য শম্ভুমিত্র , বুদ্ধদেব বসু, এঁদের লেখাই শুধু পড়েছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে এঁদের কারো কারো লিখিত নাটকে অভিনয়ের সুযোগ ঘটেছে, অথবা নিজে অভিনয় না করলেও থিয়েটারের দলে সেইসব নাটক অভিনীত হয়েছে। সেই সুত্রে একটু বেশী করে জানা বোঝার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, আজ অবধি বাদল সরকারের নাটক গুলো শুধু পড়েই গেছি। একটি নাটকেও অভিনয় করার সুযোগ পাইনি বা বলা ভালো একটি নাটককেও কাছ থেকে গড়ে উঠতে দেখিনি। আমার বরাবরই কীরকম মনে হয়, আমাদের বাংলায় পঞ্চাশ একশ বছর আগে বাংলায় যেধরনের নাটক লেখা হতো সেগুলো সাহিত্য হিসেবেও খুব উচ্চমানের হতো। তাই গল্প উপন্যাসের মতো নাটকগুলোও বেশ সাহিত্য পড়ার মতো করে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। বাদল সরকারের কয়েকটা নাটক পড়ার পর এক সময় মনে হল, কোন নাটকের সাথে কোন নাটকের মিলনেই। যেমন বিচিত্রানুষ্ঠান একরকম আবার বাঘসম্পূর্ণ অন্যরকম। আবার কদিন বাদে পড়লাম প্রলাপবাত্রিংশ শতাব্দি। আমার কাছে এই বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। একজন মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী নাটক লেখেন কি করে?
সেই আগ্রহ থেকেই ওনার আত্মজীবনী পুরনো কাসুন্দি পড়তে শুরু করি। ওনার জীবনটা যদি বাল্যকাল থেকে দেখা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে ওনার জীবন তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনগুলোর থেকে শুরু থেকেই আলাদা। মা দিদিমা অত্যন্ত শিক্ষিত। মুক্তমনা খ্রিষ্টান পরিবার। ফলত শুরু থেকেই আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালির থেকে খানিকটা ভিন্ন চিন্তা নিয়ে বড় হয়েছেন তিনি। মা দিদিমার থেকে বই পড়ার নেশা পেয়েছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অদ্ভুতভাবে নাটক পড়তে ওনার সবথেকে বেশী ভালো লাগত। কখনও কখনও কোন একটা বাংলা নাটকের চরিত্রগুলোর ভূমিকায় খেলার ছলে একা একাই অভিনয় করতেন। এভাবেই ছোট থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরীশ ঘোষের নাটকের সাথে পরিচয় ঘটে গেল। এছাড়া ছিল রেডিও নাটক। ছোটবেলায় হলে গিয়ে থিয়েটার না দেখলেও শুধু রেডিও নাটক শুনে শুনেই তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেতাদের গলা চিনে গিয়েছিলেন। মনে মনে থিয়েটার করার বাসনা বেশ জেঁকে বসেছিল। স্কুল জীবনে ছোটখাটো অনুষ্ঠানে পাড়ার নাটক দেখেছেন, বা ছোটখাটো নাটক রচনা করেছেন। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়েস পরিবারে যখন তমলুকে থাকতে যান সেই সময়, সেখানে থিয়েটারে একবারই ফিমেল পার্ট করেছিলেন। তাছাড়া সেই প্রথম সারারাত জেগে তিন হাজার দর্শকভর্তি মাঠে নাটকের অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা। তার আগে থিয়েটার হলে নাটক দেখতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তেমন হয়নি। তারপরেও স্কুল কলেজ জীবনে যে খুব থিয়েটার দেখেছেন এমন নয়। এরপর স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ঢুকে গেলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। সেখানে বছর চারেক কলেজের থিয়েটার দেখেছেন। কিন্তু নিজে কখনই এগিয়ে যাননি। কলেজ জীবনের শেষ দিক থেকেই যোগাযোগ ঘটে গেল বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে। যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। কয়েক বছর বেশ মন দিয়ে সক্রিয় ভাবে পার্টির কাজ করেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি করতে গিয়ে বস্তির মানুষ, কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। পরবর্তী কালে রচিত অনেক নাটকে তাঁর সেইসব দিনের জমানো স্মৃতি কাজে লেগেছে। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও বেশকিছু বিষয়ে পার্টির সঙ্গে তাঁর মতান্তরও তৈরি হয়েছিলো। তবে বামপন্থার সূত্র ধরে বাদল সরকার কিন্তু থিয়েটারের আঙিনায় গিয়ে দাঁড়াননি। সাধারণত আমরা দেখেছি, আমাদের প্রখ্যাত বিশিষ্ট নাটককার, পরিচালকরা সকলেই কম বয়েস থেকেই স্বাধীনতা উত্তর পর্ব সময়ে গ্রুপ থিয়েটারের ভাবনার সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ করে থিয়েটারের দিশা দেখতে চেয়েছিলেন প্রায় সকলেই। তাই নবনাট্য বা গণ নাট্য আন্দোলনের সময়ে তাঁদের লেখা নাটক গুলিতে সরাসরি সমাজ বদলে দেওয়ার চিন্তা আছড়ে পড়ছিল। কমবয়েসের লেখাগুলোর তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই পরিণত বয়সে গিয়ে তাঁদের লেখাগুলো অনেক বেশী পরিণত, অনেক বেশী ক্ষুরধার হয়েছিলো। তিরিশ চল্লিশ বছরের সময়ের ব্যবধানে কোন কোন সময় তাঁদের ভাবনা চিন্তাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিলো। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের রাজনৈতিক দর্শনের মূল সুরটি অপরিবর্তিতই ছিল। কিন্তু বাদল সরকার এক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বামপন্থী হয়েও বামপন্থী আদর্শের অনুসারী গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে গিয়ে ঢোকেননি। তাই গণনাট্যের যে ঘরানা ছিল তা তাঁর নাটকে বরাবরই অনুপস্থিত থেকে গেছে। একই ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন, হয়তো সেকারণেই অনেক দিক থেকেই তাঁর নাটক ভবিষ্যতে এক ধরনের স্বকীয়তা লাভ করে।
ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি করাকালীন এনাকা বলে যেদলটি তৈরি করেন সেখানেও মূলত বিনোদন ধর্মী নাটকেরই চর্চা চলতো। পড়ে চাকরি সুত্রে মাইথন গিয়ে স্রেফ সময় কাটানোর জন্য অফিসের কয়েকজন সারাদিনের পর সন্ধ্যেবেলা কিছু নাটকের রিহার্সাল দিয়ে সময় কাটানো শুরু করলেন। মানে সে নাটক কোনদিনও মঞ্চস্থ হবে না, কোনদিনও অভিনীত হবে না। তবু তাঁরা একেকজন জন একেকটা পার্ট মুখস্থ করে রিহার্সাল করে যেতেন। শেষে এক সময় দেখা গেল পার্টগুলো তাঁদের এতোটাই ভালভাবে মুখস্ত হয়ে গেছে, মহড়া দিতে দিতে গোটা নাটক এতোটাই ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে মঞ্চস্থ না করার কোন কারন নেই। অফিসের প্রোগ্রামে ম্যারাপ বেঁধে মঞ্চ বানিয়ে নাটক হতে লাগলো। ধীরে ধীরে বেশ জমে উঠলো সেইসব নাটক। যথেষ্ট প্রশংসিতও হল। কিন্তু দর্শকরা মূলত হাসির নাটক দেখতে চাইছিলেন। কিন্তু ঠিক যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি নাটক পাওয়া যায় না। অগত্যা তাঁকে নিজেকেই কলম ধরতে হল। এই পর্যায়েই লিখে ফেললেন বড়পিসিমা, বিচিত্রানুষ্ঠানের মতো আদ্যন্ত হাসির নাটক গুলি। এরপর চাকরি ছেড়ে নতুন করে আবার পড়াশোনা করতে পাড়ি দেন লন্ডন।
এই লন্ডন থেকেই তাঁর বিশ্ব দর্শনের শুরু। চেনা শহর চেনা গলি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পড়লেন যেন এক বিরাট সমুদ্রে। এই পর্যায়ে তাঁর বিভিন্ন দেশের মানুষ, বিভিন্ন সংস্কৃতি উন্মোচিত হয়েছিলো তাঁর কাছে। লন্ডন থেকেই তাঁর নিয়মিত থিয়েটার দেখার অভ্যাস তৈরি হয়েছিলো। খুলে যাচ্ছিলো বিশ্ব সংস্কৃতির দ্বার। একে একে ফ্রান্স, জার্মানি, নাইজিরিয়া সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছেন। তারপর দীর্ঘদিন চাকরি সুত্রে নাইজিরিয়ায় বসবাস। থিয়েটার দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কালজয়ি নাটকপড়াও শুরু করেন। বিদেশে থাকাকালীনই কখনও টুকটাক ‘বড়পিসিমা’, কখনও‘এবংইন্দ্রজিত’, কখনও আবার ‘সারারাত্তির লিখে ফেলছেন। মধ্যে মধ্যে দেশে ফিরলে সেগুলো অভিনয় হচ্ছে। এই সময় থেকে দেখা যায় ধীরে ধীরে নিখাদ হাসির নাটক লেখার পাশাপাশি শুরু করছেন আপাত সিরিয়াস নাটক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘোরার কারণে বিশ্বরাজনীতি তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিলো।
সত্যি বলতে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন উনি লন্ডনে হাজির হয়েছিলেন এবং তার পরের কয়েকটা বছর তিনি ইয়োরোপেই কাটান। ফলত খুব কাছ থেকে তিনি যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিলেন। দেশে যে যুদ্ধ সংক্রান্ত উৎকণ্ঠাদেখেননি তা নয়, কিন্তু পশ্চিমিদেশগুলোতে তার অভিঘাত অনেক সরাসরি অনুভূত হয়েছিলো। সেই আতঙ্কের বোধ, আশঙ্কা তাঁর অনেক নাটকে সুস্পষ্ট ভাবে ফিরে ফিরে আসে।
এরপর কলকাতায় ফিরে তিনি নিজেকে শুধু নাটক লেখায় সীমাবদ্ধ রাখলেন না। নিজের লেখা নাটক গুলিকে মঞ্চস্থ করার কাজ শুরু করলেন। নিজের দল তৈরি করলেন। শতাব্দী। এই পর্বে তিনি সরাসরি সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা গুলো বিরোধিতা করে কথাবলা শুরু করলেন। নব নাট্য বা গণনাট্যধারার সাথে শুরু থেকে সম্পৃক্ত নাহলেও তিনি একটি বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনার থিয়েটারের সূচনা করলেন। যা বক্তব্যে আঙ্গিকে পরিবেশনায় সবদিক থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠিত দলগুলির থেকে আলাদা একটা ধারা তৈরি করে। তিনি কখনই কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাবলম্বী শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলেননি। অনেকেই মনে করেন সত্তরের দশকে তিনি নকশালপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং সেই দর্শনকে তাঁর নাটকে প্রতিফলিত করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেই এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর নাটকের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সত্তরের দশকে যখন হল ভাড়া, এবং নাট্য নির্মাণের বিভিন্ন খরচ আকাশছোঁয়া, তখন গ্রুপথিয়েটারের বিভিন্ন দলই অসম্ভব সঙ্কটের মুখে পড়ে। মঞ্চে অভিনয় করাটাই একটা ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাদল সরকার সম্পূর্ণ অন্য পথে হাঁটেন। আক্যাদেমি কেন্দ্রিক থিয়েটারের মুখাপেক্ষী না হয়ে শুরু করেন অন্যধারার বাংলা থিয়েটার। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘরানা থেকে বেরিয়ে বরং ঝুঁকেছিলেন দেশজনাট্য ধারার দিকে। গ্রুপথিয়েটার ও ব্যবসায়িক থিয়েটার এই দুই থিয়েটারের বাইরে তাঁর নিজস্ব থিয়েটার তৈরি করলেন। যার নাম দিলেন থার্ডথিয়েটার। বললেন প্রসেনিয়াম বাধ্যতামূলক নয়। যেখানে যেভাবে জায়গা পাবো, সেখানেই থিয়েটার হবে। রাস্তায় থিয়েটার করেছেন, লোকের বাড়ির উঠোনে থিয়েটার করেছেন, নিজের নাটক নিয়ে ছুটে গেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তাঁর দেখান পথে অনেক দলই তখন প্রসেনিয়াম ছেড়ে পথনাটকে আগ্রহী হয়েছিলেন। আজ যাকে আমরা অন্তরঙ্গ থিয়েটার বা ইন্টিমেট থিয়েটার বলছি তার সূত্রপাত কিন্তু একরকম ভাব বাদল সরকারের হাতেই হয়েছিলো। এখনও বহুদল থার্ডথিয়েটারের দেখান পথে নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে চলেছে। কিন্তু তাঁর নাট্যপদ্ধতি অনুসরণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আজও বাদল সরকারের নাটক সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। বাবলা ভালো বিগত দুই দশকের তুলনায় তাঁর নাটক নিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ আরও বেড়েই চলেছে। ষাট সত্তর বছর আগে লেখা নাটক অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়। কিন্তু বাদল বাবুর বেশিরভাগ নাটকের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার কারন এমন কিছু সমস্যা নিয়ে উনি আলোড়িত হয়েছিলেন যা সেইসময়ের তুলনায় আজ শুধু একইরকম প্রাসঙ্গিক নয়, হয়তো আরও বেশী জরুরী। পরমানু যুদ্ধ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা বারবার উঠে এসেছে বিভিন্ন নাটকে। তিনি বারবার ভেবেছেন পরমাণু অস্ত্র থেকে এই পৃথিবী কি কখনও মুক্তি পাবে? আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি পরমাণু রাজনীতি কি বিধ্বংসী ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রগুলো শুধু তাদের কূটনীতি সামলাতেই ব্যস্ত। চোখের সামনেই স্রায়েল প্যালেস্টাইন গাজার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। রাষ্ট্রগুলো সেই মর্মান্তিক মৃত্যুলীলা দেখে যাচ্ছে নীরবে।
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেকবার সমালোচিতও হয়েছিলেন বাদল সরকার। তাঁর চিন্তা ভাবনা, তাঁর নাট্য পদ্ধতি অনেক কিছু নিয়েই তর্কের অবকাশ ঘটেছে। আবার অনেক সময় তাঁরই রচিত কিছু নাটককে তিনি নিজেই বাতিল বলে অস্বিকার করেছেন। যা হয়তো বাকিরা মেনে নিতে পারেননি। তবে আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে একটাই কথা বলবার আছে। তিনি যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টারমতো আসন্ন পৃথিবীর সঙ্কট দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর বেশ কিছু নাটক যত দিন যাচ্ছে, ততই বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। তাই হয়তো আজকে আমরা আশেপাশে ভোমা, প্রলাপ, সারারাত্তির, যদি আরও একবার, ত্রিংশ শতাব্দী, মিছিল এর মতো প্রচুর নাটকের মঞ্চায়ন দেখতে পাচ্ছি বর্তমান প্রজন্মের হাতে। হয়তো ওঁর নাটকগুলির হাত ধরেই আজকের থিয়েটারের ছেলেমেয়েরা আজকের সময়টাকে বুঝে নিতে চাইছে।
নাট্যব্রহ্ম কিংবদন্তি বাদল সরকার • শক্তি চট্টোপাধ্যায়
বাঙালির নাট্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারায় পরিবর্তনের এক নতুন ইঙ্গিত বহন করেছিলেন বাঙলার যে নাট্যকার-নাট্য নির্দেশক-নাট্য ব্যক্তিত্ব তিনি বাদল সরকার । নাটক নিয়ে তাঁর ভাবনা এবং আন্দোলন আজও এক স্থায়ী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বয়ে নিয়ে চলেছে । বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনকে অজস্র শ্রেষ্ঠ মণিরত্নে শোভিত করেছিলেন তিনি । তাঁর নাটক বারবার দর্শক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । বিভিন্ন বাস্তব কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে, অদম্য সাহসিকতা নিয়ে তাঁর একটির পর একটি নাটক মঞ্চস্থ হয় । মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে-সঙ্গে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এই বাঙলার বুকে । কিছু ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন কিছু নতুন সৃষ্টির জন্য । প্রখ্যাত কিংবদন্তি নট ও নাট্যকার বাদল সরকার তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব । কেবলমাত্র তাঁর প্রযোজনা কলকাতাতেই মঞ্চস্থ হয়েছিল এমনটি নয় । কলকাতা ও কলকাতার বাইরে সমস্ত জেলা তথা সমগ্র দেশে তাঁর লেখা নাটক অভিনীত হয় । বাঙলার অবহেলিত লোকসংস্কৃতিকে নাট্য আন্দোলনে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন তিনি । আদ্যন্ত এই মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার নট ও নাট্যকার সমাজের শোষণ, নিপীড়ন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলমকে বারবার সোচ্চার করেছেন । তাঁর নাটকের ভাষা জোতদার বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, কালোবাজারি বিরোধী, উগ্রজাতীয়তাবাদ বিরোধী । যাঁর সামনে সোনালি ভবিষ্যৎ, যাঁর সামনে বিত্তবান হবার বহু-বহু সুযোগ, যাঁর চাকুরি বেশ আমলা-আমলা, সেই সমস্ত কিছুকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করেছেন আমৃত্যু । তিনি ভাববিলাসিতায় ভাসেন নি । তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে জীবনের যোগ রেখে গিয়েছেন । সাহিত্য সংস্কৃতি, ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, সকলের কাছে নাট্যকার কিংবদন্তি বাদল সরকার আজও প্রাসঙ্গিক । বাদল সরকারের নাটক মানেই বাস্তব জীবনের উপজীব্য বিষয় । নাট্যকার জানতেন যে সমাজে বসে তিনি নাটক লিখছেন, নাটক মঞ্চস্থ করছেন, সেই নাটককে সমাজের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করতে হয় । সময়ের সঙ্গে সমাজ পাল্টায় । পাল্টে যায় ভূগোল,ইতিহাস, অর্থনীতি,, । পাল্টে যায় সমাজের মূল্যবোধ । নাটক একটি অন্যতম সাহিত্যকর্ম । নাটক একটি বিনোদন । নাটকে রসসৃষ্ট হয় । নাটকের গঠনশৈলি ভীষণ রকম বৈজ্ঞানিক । তাই নাট্যকার হতে হলে তাঁর ভাবনা, প্রয়োগ, ভাব, ভাষা, বার্তা মৌলিক হতে হয় । সবই যদি ইংরেজি নাটকের অনুসারী হয় তবে একজন নাট্যকারকে অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে পৃথক করা দুঃসাধ্য হয় । ফলে বহু নাট্যকার হারিয়ে যান । নাট্যকার বাদল সরকার হারিয়ে যান নি । শতবর্ষের পরেও যত দিন যাচ্ছে নাট্যজগতে বাদল সরকারের ততই গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে ।
সামাজিক কুপ্রথাকে কশাঘাত করা নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসাময়িক কালে মৌলিক সাহসী নাটক রচনার জন্য নীলদর্পণ রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র উদ্ভাসিত হয়েছিলেন । ১৮৬০ সালের আগেপরে নাট্যজগতের দুই দিকপাল গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি নাট্যশালাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন । আচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্নেহধন্য । তবুও গিরিশযুগেও মৌলিকতা ও ভাবনায় বহু নাট্যকার অভিনেতা নাট্যধারাকে পুষ্ট করেছিলেন । যেমন অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশ চন্দ্র ঘোষের পুত্র দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ইত্যাদি প্রমুখজন । নাট্যকার বাদল সরকারের সমসাময়িক কত-কত নাট্যকার-অভিনেতা । শম্ভু মিত্রের ধ্রুপদী পাণ্ডিত্য, উৎপল দত্তের পাশ্চাত্য থিয়েটার ভূমি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালি মেজাজে থিয়েটারে প্রবেশ । কিন্তু নাট্যকার বাদল সরকারকে কেউ বালিচাপা দিতে পারেন নি । নাট্যকার বাদল সরকার শুধুমাত্র নাটক লিখেছেন, দল তৈরি করেছেন, অভিনয় করেছেন, সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে নাট্যমঞ্চে তুলে এনেছেন এমন নয় । নাট্যকার বাদল সরকার ছিলেন নাট্যশাস্ত্রের গবেষক-পরীক্ষক-নিরীক্ষক । সমাজে অযৌক্তিক ও উদ্ভট আখ্যা দিয়ে যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হতনা, নাট্যকার বাদল সরকার সেই অযৌক্তিক ও উদ্ভট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন একের পর এক নাটক । তাঁর নাটকে তৎকালীন সময়ে কিছুটা তর্ক উঠলেও নাট্যামোদী দর্শকদের পরিবেশনায় মোহিত করে তাঁর অনন্ত গুণ ও পরিচ্ছন্ন মহিমান্বিত প্রতিভাকে বারংবার উদ্ভাসিত করেছে । মন, বাক্য, দেহ, বচন দ্বারা যে উজ্জ্বল সাহিত্য তিনি মঞ্চে সৃজনশীল নাটকের মাধ্যমে লৌহকঠিন সমাজে লৌহকারের মতো হাতুড়ির আঘাত করেছেন তাতে সমাজের অনিষ্টকারীরা ভয় এবং বেগ দুই-ই পেয়েছেন ।
বাদল সরকার । নামেই যেন বৃষ্টির গন্ধ । জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৫ সালের ১৫ই জুলাই । জুলাই মাস মানেই আষাঢ় মাসের লাগাতার বরিষণ । এমনই এক বরিষণ দিনে কলকাতার ঠনঠনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন নাট্য তপস্বী বাদল সরকার । বাবার নাম মহেন্দ্রলাল সরকার । মায়ের নাম সরলাবালা । জন্মমুহূর্তে এমন বর্ষণ চলছিল যে ঘর-বার করাই মুশকিল হয়ে পড়েছিল । জন্ম মুহূর্তে আনন্দে বৃষ্টির ফোঁটারা যেন কোলাহল শুরু করেছিল । যেন প্রচেতারা খুশিতে তাঁকে প্রণাম করছিলেন । ঘন বর্ষণ দিনে এক দার্শনিকের জন্ম হল । ঘন বর্ষণ দিন এক সংকল্পের জন্ম হল । নবজাতকের নামকরণ করা হল সুধীন্দ্র । একেবারে দেবরাজ ইন্দ্রযোগ । কাকা বিপিনচন্দ্র সরকার অঝোর বাদল দিনে সুধীন্দ্রের জন্ম বলেই ডাকনাম রেখে দিলেন ‘বাদল’ । শৈশব থেকেই লেখাপড়া শুরু হল সুধীন্দ্র সরকার নামেই । কিন্তু সৃষ্টির কাজে ‘বাদল’ নাম ব্যবহার করবার কারণে ‘সুধীন্দ্র’ চাপা পড়ে গেল । সুধীন্দ্র রয়ে গেল পাশ সার্টিফিকেট ও আপিসের কাগজপত্রে । হয়ে উঠলেন বাদল । বাদল সরকার । শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী শিশু ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি স্কুলে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন । ১৯৪১-৪৩ সালে তাঁর বয়স যখন ১৬-১৮ বছর ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়বার জন্য । সময়টা তখন অস্থির । দুর্বার গতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে । কলকাতায় ঘন-ঘন বোমাতঙ্ক চলছে । খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে । কলেরায় বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছেন । ছাত্র বাদল সরকার সে-সব দেখে পাথর হয়ে যাচ্ছেন । বিস্ময়ান্বিত চোখ তুলে বিশ্বকে দেখবার চেষ্টা করছেন । মন যেন মন থেকে ছিন্ন হতে চাইছে । লেখাপড়া বা ক্যারিয়ার তৈরি তাঁর কাছে অকালপক্ক শস্যভোজনের মতো বিসদৃশ লাগছে । তিনি হিমবায়ু, অগ্নিতাপ, বর্ষা, রৌদ্র হয়ে অন্তরের সুধীন্দ্র সরকারকে সংযত হতে পরামর্শ দিলেন । বাদল সরকারকে এগিয়ে আসতে বললেন । ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ১৯৪৩ সালে তৎকালীন বি-ই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হলেন । দেশভর তখন ইংরেজ খেদাও মন্ত্রে আলোড়িত । পরিস্থিতি বারবার বিচলিত করছিল তাঁর হৃদয়কে । ১৯৪৭ সালে বি-ই ডিগ্রি লাভ করেই চাকুরি পেলেন মহারাষ্ট্রের রেলশহর নাগপুর থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে খাপড়খেদা নামক এক জায়গায় । মন তখন গাঁথছে ইঁট মশলায় নাটকের ইমারত । কলকাতা থেকে বহুদূরের পোস্টিং তাঁর পছন্দ হলনা । চাকুরি ত্যাগ করলেন । এদিকে অর্থের দরকার । চাকুরি ত্যাগ মানে বেতন বন্ধ । তিনি কলকাতায় আসার খোঁজখবর শুরু করলেন । কলকাতায় থাকলে চাকুরির পাশাপাশি নাট্যচর্চা জমিয়ে চলবে । কলকাতা তখন থিয়েটারের দিকচিহ্ন । তিনি তখন মননে-হৃদয়ে থিয়েটারের ভবন, থিয়েটারের ভুবন, থিয়েটারের সবুজ বন, থিয়েটারের নীল সাগর । আশামতো কলকাতায় চাকুরি পেয়ে গেলেন । ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহ-অধ্যাপকের পদে যোগদান করলেন । শুরু হল বুর্জোয়া বিলাসকে ধাক্কা দিতে অধ্যাপনার পাশাপাশি বেশি-বেশি নাট্যচর্চা । ১৯৪৮-৪৯ সালে যোগদান করলেন কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়নে । সেখানে সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠলেন । এরপরই ত্যাগ করলেন নিজের ঘর ।
নাটক, যাত্রা প্রভৃতি শুধুমাত্র বিনোদনের বস্তু নয় । প্রতিবাদের ভাষাও । প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আগেই বলেছি নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার নাট্যাভিনয়, নাট্য-নির্দেশনা, নাটক রচনার পাশাপাশি নাট্যজগতের নাট্যচর্চা কে নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন । নাট্য সাহিত্যের উচ্চমানের অধিকারী মানুষটি এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন । চল্লিশ ঊর্দ্ধ বয়সকালে তাঁর চোখের সামনে ছিল আরও এক অস্থিরতার কাল । চীনের সঙ্গে ভারতে যুদ্ধ, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধ । লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এই বঙ্গে আসছেন । খাদ্য নেই । পানীয় সংকট । অন্যদিকে মাও বিপ্লব । নকশাল আন্দোলনে অলিতে-গলিতে । নকশাল আন্দোলন তখনও সশস্ত্র বা হিংসাত্মক হয়নি । জনগণের হতাশা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর ক্ষতে জোতদার-জমিদারদের লোভ, মজুতদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ফ্যাসিস্ট বিরোধী গণ আন্দোলন শুরু করে নকশালরা । সেই সময় নকশালদের উপর পুলিশি নির্যাতন চোখে পড়ে নাট্যকার বাদল সরকারের । বামপন্থা ভাবিত মানুষটি সমাজে অত্যাচারিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রবল সোচ্চারে ফেটে পড়েন নাটকে-নাটকে । নাটক নয়, যেন এক একটি কামানের গোলা বেরিয়ে আসে তাঁর প্রযোজনায় । এরপর তিনি সাংঘাতিক কান্ড ঘটিয়ে ফেললেন । সমাজের তথাকথিত সমস্ত উদ্ভট কাহিনী নিয়ে নাটক তৈরি করে কলাকুশলীদের নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে সোজাসুজি নেমে পড়লেন রাস্তায় । দল বেঁধে নাটক চলতে লাগলো পাড়ার মোড়ে, রাস্তার উপর, রেল স্টেশনে । এতদিন দর্শক যেতেন থিয়েটারহলে থিয়েটার দেখতে । এবার থেকে থিয়েটার চলে গেল দর্শকদের দুয়ারে থিয়েটার দেখাতে । আগে ছিল ফেলো কড়ি মাখো তেল । অর্থাৎ টিকিট কাটুন, হলে প্রবেশ করুন, থিয়েটার দেখুন । এখন থেকে থিয়েটার হয়ে গেল একেবারে নিঃশুল্কে বিনে পয়সায় । সাজগোজ-মেক-আপ অনেক কমে গেল । আলোর খুব একটা প্রয়োজন হলনা । শিল্পীরা নিদারুণ লড়াইয়ের মধ্যে আশা ও প্রত্যয়ের সৃষ্টি করলো । সূচিত হলো নাটকের তৃতীয় আঙ্গিক । নাম হলো থার্ড থিয়েটার । নাটক ও নাট্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতি পাল্টে যে নতুন পথ পরিক্রমা শুরু করেছিলেন বাদল সরকার তাই হয়ে গেল থার্ড থিয়েটার । পথনাটক বা পথনাটিকা থার্ড থিয়েটার । থার্ড থিয়েটারের জনক হয়ে চির স্মরণীয় হয়ে রইলেন নাট্যবিদ-নাট্যপণ্ডিত বাদল সরকার ।
বাদল সরকারের নাটক শুরুতেই ছিল অন্যস্বরে সংলাপ । অন্যস্বরের অর্থ দুটি পৃথক শব্দের সন্ধি করে কথা বলা । যা নাট্যসাহিত্যে যথেষ্ট শক্ত । এরপরই তিনি অন্যস্বর বাদ দিয়ে তাঁর রচিত নাটকের সংলাপে নিয়ে এলেন সিরিয়াস কমেডি এবং অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট কথাবার্তা ও আবহ । নাট্যবিদ বাদল সরকার যখন ফ্রান্সে গিয়েছেন তখন সেখানে বসেই লিখে ফেলেন অ্যাবসার্ড নাটক ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ । এই নাটকে প্রথাসিদ্ধ কাহিনীতে না গিয়ে কয়েকটি বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টি করলেন । এরপর এক-এক করে অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক লিখে ফেললেন । ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে পঞ্চাশটির মতো নাটক লিখেছেন এই কিংবদন্তি নাট্যকার । নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বাকি ইতিহাস’, ‘ত্রিংশ শতাব্দী’, ‘পাগলা ঘোড়া’, ‘যদি আর একবার’, ইত্যাদি ।
জীবনে পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন বহু । ১৯৭১ সালে জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপ, ১৯৭২ সালে পদ্মশ্রী, ২০১০ সালে পদ্মভূষণ । সৃষ্টির প্রবক্তা হলেও অহংকার ছিল না কিংবদন্তি মানুষটির । পা কখনও মাটি থেকে উপরে উঠে যায় নি ।
‘স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ / ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কূলে ভবতি ।/ তরতি শোকং তরতি পাপমানং / গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ।‘ মুণ্ডক উপনিষদে আছে, যে কেউ পরমব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হন । তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন । নাট্যজগতের মহাধ্রুবতারা নাট্যবিদ নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্যব্রহ্ম কিংবদন্তি বাদল সরকার ওরফে সুধীন্দ্র সরকার ২০১১ সালের ১৩ই মে তাঁর কর্মলীলা সাঙ্গ করে নাট্যব্রহ্মে লীন হয়ে যান । লাভ করেন অমরত্ব এবং অমৃতত্ব দুই-ই ।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৪৭৬৪৯৬৫০৫
Address :
Sakti Kumar Chattopadhyay
Vill-Ekteswar
P.O.+P.S.+Dist-Bankura
Pin-722101 WB
Email : chattopadhyaysakti4444@gmail.com
শক্তি চট্টোপাধ্যায় মূলত প্রাবন্ধিক এবং শিশু-কিশোরদের গল্পকার । লিখেছেন উপন্যাস ‘পুরাণ প্রান্তরে’ এবং প্রবন্ধগ্রন্থ ‘শক্তির নামাবলী’ । এছাড়াও লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ, গল্প । কলকাতা থেকে নানান প্রথমশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় । শিশু-কিশোরদের গল্প লিখেন শক্তি কাশ্যপ নামে । জন্ম ১৯৬০ সালের ১৭ই এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর গ্রামে । চাকুরি করেছেন বনবিভাগে । ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে কোভিডকালে প্রধান করণিক পদ থেকে অবসর নিয়েছেন এই প্রাবন্ধিক ।এর সাথেও সংস্কৃত স্তোত্র পাঠে অদ্বিতীয় এই শ্রদ্ধেয় মানুষটি। বহু যায়গায় সেই স্তোত্র পাঠের জন্য নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে তাঁর।
রক্তকরবী
রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী: একটি বিশ্লেষণ
অরূপ কুমার সাউ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী (১৯২৪) বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। এটি তাঁর প্রতীকধর্মী নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত। নাটকটি শুধুমাত্র নাট্যরস সৃষ্টির জন্য নয়, বরং মানুষের স্বাধীনতা, শ্রমজীবী মানুষের জীবন, অর্থলোভী শাসকের নিষ্ঠুরতা এবং প্রেমের মুক্তির বার্তা তুলে ধরে। এর প্রতিটি চরিত্র, দৃশ্য ও প্রতীক পাঠকের কাছে নতুন ব্যাখ্যার দরজা খুলে দেয়। আমার চোখে রক্তকরবী শুধু একটি নাটক নয়, বরং সভ্যতার অন্তর্লীন অসুখের বিরুদ্ধে মানবমুক্তির গান।
রক্তকরবী-এর কাহিনি গড়ে উঠেছে “যক্ষপুরী” নামের এক খনিজ-সমৃদ্ধ রাজ্যের প্রেক্ষাপটে। রাজা সেখানে অদৃশ্য তিনি অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে থাকেন। তাঁর অসংখ্য কর্মচারী, প্রজা, যন্ত্রপাতির মতো নিঃশব্দে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের জীবন খাঁচার পাখির মতো, স্বাধীনতা নেই, আনন্দ নেই।
এই মৃতপ্রায় রাজ্যে আসে নন্দিনী। সে প্রকৃতির প্রতীক, প্রাণের প্রতীক। তার উপস্থিতি শ্রমিকদের মনে প্রশ্ন তোলে, রাজ্যের বন্ধ দরজাগুলো কড়া নাড়ে। নন্দিনী শ্রমিকদের সাহস দেয়, প্রেম শেখায়, মুক্তির স্বপ্ন জাগায়।নাটকের শেষে রাজা তার অন্ধকার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, কিন্তু তার মধ্য দিয়েই মুক্তির সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়।রক্তকরবী মূলত প্রতীকী নাটক। এখানে চরিত্র ও উপকরণগুলো সরাসরি কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা নয়, বরং গভীরতর সামাজিক-দার্শনিক সত্যের প্রতীক।
- যক্ষপুরী -শিল্পসভ্যতার প্রতীক, যেখানে খনিজ সম্পদ আহরণে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা হয়।
- রাজা – অর্থলোভী ও অমানবিক ক্ষমতার প্রতীক। তাঁর গোপন বাস কেবল আধিপত্য ও ভয়ের প্রতীক।
- নন্দিনী – প্রকৃতি, প্রেম, স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক। সে জীবনকে রক্তকরবীর মতো রঙিন করে তোলে।
- রক্তকরবী ফুল -জীবনীশক্তি, রক্ত, প্রেম ও আত্মত্যাগের প্রতীক।
- শ্রমিকেরা – নিপীড়িত সাধারণ মানুষ, যাদের শ্রমের বিনিময়ে সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে।
১. রাজা
রাজা অদৃশ্য, অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ। তিনি আধুনিক শিল্পসভ্যতার প্রতীক যেখানে শাসক জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার ভয়, সন্দেহ ও নিষ্ঠুরতা সভ্যতার এক অমানবিক রূপকে প্রকাশ করে।
২. নন্দিনী
নন্দিনী নাটকের প্রাণকেন্দ্র। সে সুন্দরী, প্রাণবন্ত, নির্ভীক। তার মধ্যে প্রেম, সাহস, জীবনোদ্দীপনা প্রবল। নন্দিনী কেবল এক নারীমাত্র নয়, বরং মানুষের অবিনাশী স্বাধীনচেতা সত্তার প্রতীক।
৩. শ্রমিকেরা
তাদের পরিচয় নেই, কেবল সংখ্যা। তারা যন্ত্রে পরিণত, শাসকের শোষণের শিকার। কিন্তু নন্দিনীর উপস্থিতি তাদের মনে প্রশ্ন তোলে, বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়।
৪. বিষু
সে নন্দিনীর প্রতি গভীর টান অনুভব করে। সাধারণ শ্রমিক হলেও তার প্রেম জীবনের আশার প্রতীক। বিষু নন্দিনীর কাছে এক অর্থে মানুষের সহজ সরল ভালোবাসার প্রতীক হয়ে ওঠে।
১. স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা
নাটকের মূল সুর হলো মানুষের স্বাধীনতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। রাজা মানুষকে বন্ধন দিয়েছে, কিন্তু নন্দিনী সেই বন্ধন ভাঙার বার্তা নিয়ে এসেছে।
২. প্রেম ও মানবিকতা
প্রেম এখানে কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামষ্টিক। নন্দিনীর প্রেম মানুষের অন্তরে সাহস জাগায়, ভয়ের শৃঙ্খল ভাঙে।
৩. শোষণ ও শ্রম
যক্ষপুরীর শ্রমিকেরা আমাদের চোখে শিল্পবিপ্লব-উত্তর সভ্যতার নিপীড়িত মানুষ। তাদের শ্রমের বিনিময়ে সম্পদ গড়ে ওঠে, কিন্তু তারা নিজে বঞ্চিত।
৪. মৃত্যু ও পুনর্জন্ম
রক্ত, আত্মত্যাগ ও মৃত্যু নাটকে সর্বত্র ছায়া ফেলেছে। তবে এই মৃত্যু ধ্বংস নয়, বরং পুনর্জন্মের পথ। রক্তকরবীর লাল রঙই সেই আশার প্রতীক।
রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখানে কাব্যিক, সংগীতধর্মী। নাটকটি পড়তে গদ্য হলেও মনে হয় যেন কাব্য। প্রতিটি সংলাপ দার্শনিক তাৎপর্যে ভরা। সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর বার্তা উঠে আসে। যেমন, নন্দিনীর সংলাপগুলো জীবনীশক্তি জাগায়; আর রাজার সংলাপে ভয় ও অন্ধকারের ছায়া। রক্তকরবী লেখা হয়েছিল ১৯২০-এর দশকে, যখন উপনিবেশিক শোষণ ও আধুনিক শিল্পসভ্যতার সংকট একসাথে অনুভূত হচ্ছিল। ভারত তখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। নাটকটি সরাসরি রাজনীতি নয়, কিন্তু তার অন্তর্লীন বার্তা হলো শোষণ-প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার ডাক।আজকের দিনে রক্তকরবী সমান প্রাসঙ্গিক। আধুনিক সভ্যতা এখনও মানুষের শ্রমকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে, পরিবেশ ধ্বংস করে, প্রেম-মানবিকতাকে অবদমিত করে। নন্দিনীর মতো প্রাণশক্তির প্রয়োজন আজও সমান।
- প্রতীকী নাটক হিসেবে রক্তকরবী বিশ্বসাহিত্যে অনন্য।
- রবীন্দ্রনাথ এখানে ইউরোপীয় নাট্যশৈলী ও ভারতীয় দার্শনিকতা মিলিয়েছেন।
- নাটকের গঠন, চরিত্রায়ন ও প্রতীকের ব্যবহারে আধুনিক বাংলা নাটকের পথপ্রদর্শক।
- কেবল নাট্যরস নয়, গভীর দর্শন ও মানবতাবাদ এর মূল ভিত্তি।
আমার দৃষ্টিতে রক্তকরবী
আমার চোখে রক্তকরবী কেবল একটি নাটক নয়, বরং মানুষের আত্মার মুক্তির সঙ্গীত। রাজা আমাদের ভেতরের ভয়, লোভ, স্বার্থপরতার প্রতীক। নন্দিনী আমাদের ভেতরের স্বাধীনচেতা সত্তা। শ্রমিকেরা আমাদের চারপাশের মানুষ, যারা বঞ্চিত হলেও আশা ছাড়ে না। এই নাটক আমাকে শেখায় মানুষকে দমন করা যায় না, প্রেমকে বন্দি করা যায় না। নন্দিনী বারবার মনে করিয়ে দেয়, “জীবন রক্তকরবীর মতো উজ্জ্বল, তাকে ঢেকে রাখা যায় না।”রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী মানবসভ্যতার অন্ধকারে আলোর প্রদীপ। এটি শোষণবিরোধী কণ্ঠস্বর, প্রেমের জয়গান, স্বাধীনতার ঘোষণা। নাটকটি যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন প্রাসঙ্গিক থাকবে।
রক্তকরবী: কিছু অক্ষম পর্যালোচনা
সুদক্ষিণা গুপ্ত
অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রক্তকরবী একটি ফুলের নাম। লাল রঙের ফুল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নামে একটি নাটক লেখেন। আজ থেকে একশো বছর আগে। নাটকটি ‘প্রবাসী ‘ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় এর ইংরেজি নাট্যরূপ ‘Red Oleanders’. ১৯৫৪ সাল থেকে বহুবার এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে। নাটকটির অনেকগুলো খসড়া থাকলেও নাট্যকারের জীবদ্দশায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাইরে এটি অভিনীত হয় নি। হয়তো তিনি নিজে এটি অভিনয় করানোর মত কাউকে খুঁজে পান নি, হয়তো নিজে সন্তুষ্ট ছিলেন না নাটকটির চূড়ান্ত রূপটি নিয়ে। শোনা যায় তিনি মনস্থ করেও মঞ্চস্থ করে উঠতে পারেন নি নাটকটি।
কিন্তু এই নাটকটির মধ্যে কী এমন আছে, যে লেখার ১০০ বছর পরও নাটকটি নিয়ে চর্চার শেষ নেই? কেন এই নাটকটি ১০০ বছরেও পুরোনো হয় না?
নাটকটি আবর্তিত হয় যক্ষপুরী নামে এক রাজ্যের এক রাজাকে ঘিরে। যক্ষপুরী কেন? কারণ এই রাজ্যের পাতালে আছে এক বিশাল সোনার খনি যেখানে আছে তাল তাল সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই রাজাটির নাম মকররাজ। মকরের মত দাঁতে দাঁতে তিনি চেপে ধরেন সে দেশের মানুষকে -নিস্পেষণ করে বার করে নেন তার সব প্রাণশক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা, ভাবনা চিন্তা করার ক্ষমতা। একে তিনি বলেন তাঁর জাদু, যার দ্বারা তিনি মানুষের জাগরণ ঘুচিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু জাগিয়ে তুলতে পারেন না মানুষকে…এ তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। শুধু সে মানুষ সোনার খনিতে সুড়ঙ্গ খোদাই করে, তুলে আনে সোনার পিণ্ড যন্ত্রের মত। তাদের পরিশ্রমের অন্ত নেই, কীভাবে যেন রাজার জাদুতে তারা সবাই বোবা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। তাদের সর্দার তাদের চালনা করে, সে রাজাকে খুশি করে সর্দার হয়েছে, আবার মোড়ল সর্দারকে খুশি রাখে নানারকম খবরের যোগান দিয়ে, গুপ্তচরবৃত্তি করে। মোড়লরাও একসময় খোদাইকর ছিল, সর্দারদের খুশি করে তারা মোড়লের পদ পেয়েছে। পছন্দের পোষাক পরার স্বাধীনতাও সে দেশের মানুষের নেই। পরতে হয় বিধিবদ্ধ পোষাক, যেমন একদল পরে লালটুপি।সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্য, অন্যমনস্ক করে রাখার জন্য যক্ষপুরীতে গোঁসাইজিকে নিয়ে আসা হয়, যিনি নামগান করে তাদের মুগ্ধ করে রাখবেন। এই গোঁসাইজিও কিন্তু রাজা ও সর্দারের অনুগ্রহপুষ্ট, তাদের হয়ে কাজ করাই তাঁর কাজ। খোদাইকরদের উপদেশও তিনি সেভাবেই দেন।
এই খনির খোদাইকরদের নেই কোনো নাম, কোনো মুখ, কোনো পরিচয়। তাদের সবারই পরিচয় সংখ্যা দিয়ে, যেমন ৪৯ গ বা ৬৭ ফ ইত্যাদি। সম্পূর্ণ যক্ষপুরী যেন একটি কয়েদখানা। মনে পড়ে, “হাজার চুরাশির মা” উপন্যাসটির নাম, যা লেখা হয়েছে রক্তকরবী লেখার অনেক পরে। এমনকি যারা অত্যাচারের, নৃশংসতার প্রতিবাদ করতে চায়, তাদেরও মগজধোলাই হয়ে যায়, তারাই সর্দারের সামনে লুটিয়ে পড়ে ভক্তিতে, মেনে নয় তার সবকথা।
রাজা নিজে থাকেন জালের আড়ালে। না, তাঁরও মুখ দেখা যায় না। কিন্তু অমিত শক্তিধর তিনি। বাহুবলী। পেশীর জোরে তাল তাল সোনাকে চুড়ো করে সাজান তিনি। যত বড় চুড়ো, তত শক্তির পরিচয় । তাঁর শক্তির প্রতীক একটি সুবিশাল ধ্বজাদণ্ড। তার ওপরে ওড়ে নিশান। সেদেশের মানুষ এই ধ্বজারই পুজো করে, আর করে অস্ত্রপূজা, অর্থাৎ রাজার শক্তিকেই। যদিও গোঁসাইজি তাদের নামগান শোনান। এই রাজা থাকেন আড়ালে, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু তিনি দেখতে পান সবাইকে, জানতে পারেন কোথাও কোনো বিদ্রোহ হলো কি’না। তাঁর নিযুক্ত সর্দারের চরেরা খবর আনে চারদিক থেকে। মনে পড়ে যায় জর্জ অরওয়েলের লেখা 1984 উপন্যাসটির কথা, যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, রক্তকরবী প্রকাশিত হবার প্রায় ২৫ বছর পরে এবং যখন রবীন্দ্রনাথ আর পৃথিবীতে নেই। জানি না জর্জ অরওয়েল রক্তকরবী পড়েছিলেন কিনা। তবে জানি যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ একজন কবি, এবং সত্যদ্রষ্টা ও ক্রান্তদর্শী। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ করেন ১৯৩০ সালে, অর্থাৎ রক্তকরবী লেখারও ৫/৬ বছর পরে। রাশিয়ার তৎকালীন সুব্যবস্থা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। কিন্তু কমিউনিস্ট দেশটির ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবের কথা তিনি জানতে পারেন অনেক পরে। তবু রক্তকরবীতে তিনি তুলে এনেছেন একজন স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটরকে যার প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু শোষণের। কোথায় যেন স্টালিনের রাশিয়ার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় না? স্টালিনের “রাজত্বকাল” ছিল ১৯২৪ থেকে ১৯৫২।
এই যক্ষপুরীতে এসে পড়ে একঝলক বসন্তের বাতাস।সে হলো নন্দিনী। সারা গায়ে তার রক্তকরবীর আভরণ। সে সেজে থাকে যৌবনের রাঙ্গা রঙে – এই আভরণ তাকে পরিয়েছে রঞ্জন, যাকে সে ভালবাসে। সম্পূর্ণ সংলাপনির্ভর নাটকটিতে কিন্তু রঞ্জনের কোনো সংলাপ নেই। শুধুমাত্র সংলাপের মধ্যে দিয়েই বুঝে নিতে হয় সমস্ত একশন। রঞ্জন অনুপস্থিত থেকেও প্রবলভাবে উপস্থিত এই নাটকে। তার নামেও লাল রং।
এই নন্দিনী এসে পাগল করে দেয় যক্ষপুরীর কিছু মানুষকে। বাদ যান না পুঁথিজ্ঞানসর্বস্ব অধ্যাপক, খোদাইকর ফাগুলাল ( এর নামেও কেমন লাল রঙের দ্যোতনা, ফাগের অনুষঙ্গ), সদ্য আগত পুরানবাগীশ, এমনকি অত্যাচারী সর্দারও। সর্দার নন্দিনীর কাছ থেকে সাদা কুন্দফুলের মালা পায়, পায় না তার হৃদয়রাঙানো লাল রঙের রক্তকরবী, যা সে কেবল রঞ্জনের জন্যই রাখে, তাই সর্দারও ঈর্ষা করে রঞ্জনকে। যাই হোক, এদের সকলের মনে রং ধরিয়ে দেয় নন্দিনী – না, সে শুধু তার রূপযৌবন নিয়ে নয়, তার মিষ্টি ও হাসিখুশি স্বভাব ও আচরণ, তার সরলতা, তার সবাইকে ভালোবাসা ও সবার ভাল চাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে। যক্ষপুরীর নিয়ম ও অত্যাচার শিথিল হয়ে যেতে চায়, এমনকি চোখে ঘোর লাগে স্বয়ং রাজারও। ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা একজন সাধারণ নারী। নন্দিনীর প্রতি তার স্বামী ও অন্য পুরুষরা আকৃষ্ট হয়, তাই সে সাধারণ নারীপ্রকৃতি অনুযায়ী নন্দিনীকে ঈর্ষা করে। সে ফাগুলালকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায় গ্রামে, নবান্ন উৎসবের, প্রকৃতির মাঝে। কিন্তু সর্দার তাকে বোঝায় যে এখানেই সে ভালো আছে, যেটি আদতে একটি কয়েদখানা। স্বাধীন চিন্তা ভাবনা সব ছেড়ে দিতে হয় তাদের । অথচ ফাগুলালও একজন বিদ্রোহী খোদাইকর।
কিশোর নামের আরেকটি চরিত্র আছে নাটকটিতে, সে যথার্থই কিশোর। সেও প্রতিবাদী হয়ে উঠতে চায়, হয়তো বয়সের ধর্মেই, কিন্তু তারও পরিণতি সুখের হয় না। নন্দিনীর ভক্ত ছিল সেও, যাকে আজকের ভাষায় বলা যায় admirer বা fan। হয়তো সে প্রেমিকও, অনেকটা শ্যামা নৃত্যনাট্যের উত্তীয়র মত। নন্দিনীকে রোজ রক্তকরবীর ফুল তুলে এনে দেবার দায়িত্ব নেয় সে স্বেচ্ছায়, যা ছিল রঞ্জনের দায়িত্ব, এবং অধিকার তো বটেই। রঞ্জনকে খুঁজে পায় না নন্দিনী, কিশোরও খুঁজে পায় না তাকে। নন্দিনী উৎকণ্ঠিত হয় রঞ্জনের জন্য। সবাই তাকে দেখেছে হয়তো, কিন্তু কেউ জানে না সে কোথায় এখন। অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী রঞ্জন – নন্দিনীর প্রাণের দোসর সে – নন্দিনীকে ভালোবাসায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নন্দিনীর অসংখ্য admirer থাকলেও রঞ্জনের জন্যই তার প্রাণ আকুল হয়, কারণ রঞ্জনকে সে ভালবাসে। খোদাইকরেরা জানায় রঞ্জন খোদাইকরদের গাইতে শিখিয়েছে, নাচতে শিখিয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের অভাবে তারা রঞ্জনের নেতৃত্বে কোদাল নিয়ে খোদাইনৃত্য করেছে। এ তো অনাচার – যক্ষপুরীতে প্রাণের হওয়া বওয়াতে আসে রঞ্জন- এ তার অপরাধ সাব্যস্ত হয়।
ওদিকে রাজার মনও রক্তিম হয়ে ওঠে নন্দিনীর সংস্পর্শে। নন্দিনীর খোলা চুলে মুখ ডুবিয়ে প্রাণের আরাম পেতে চান তিনি। রঞ্জনের প্রতি ঈর্ষাও তাই প্রকাশ করে ফেলেন। তিনি নন্দিনীকে ভয়ও পান। পাছে যক্ষপুরীর সব নিয়মকানুন ভেঙে যায় নন্দিনীর অনুপ্রেরণায়- পাছে রাজাও শিথিল হয়ে পড়েন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রচণ্ড বলশালী রাজা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন – পাছে তিনি কোমল হয়ে পড়েন – তাই তিনি নন্দিনীকে বারবার সরিয়ে দিতে চান সম্মুখ থেকে – তাঁর কাজের ব্যাঘাত হবার ভয়ে – সর্বোপরি তাঁর মন দুর্বল হয়ে পড়ার ভয়ে বারবার নন্দিনীকে বলেন – আমার সময় নষ্ট করো না – যাও, যাও।
নন্দিনী রাজাকে বার করে আনতে চায় জালের ঘেরাটোপের আড়াল থেকে, ভিতরে ঢুকতে চায় জোর করে – রাজাকে মুক্ত পৃথিবীতে বার করে আনার চেষ্টা চলতে থাকে অবিরত । এই জাল থেকে মনে পড়ে যায় পরবর্তীকালের লৌহযবনিকা বা iron curtain এর কথা, যার আড়ালে ঢাকা পড়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া সহ অর্ধেক পৃথিবী। অথচ রাজার মনও চায় নন্দিনীর কাছে ছুটে চলে যেতে – প্রাণভরে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে। নিজের তৈরি জালের আড়াল থেকে বার হয়ে আসতে পারেন না তিনি। তাসের দেশের রাজাও ছিলেন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী ক্ষমতার লোভ আর নিষ্ঠুরতা ছিল না তাঁর মধ্যে। কারণ হয়তো এই যে তিনি কোনো খনির মালিক ছিলেন না।
সোনার খনি থেকে উঠে আসা শ্রমিকের দল – যাদের পরিচয় সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ – সার দিয়ে চলে। তাদের প্রাণ নেই, বোধ নেই। মাথা নীচু। নন্দিনী দেখে তার পূর্বপরিচিত অনেক যৌবনদীপ্ত পুরুষ, যাদের মধ্যে ছিল তার গোপন admirerও, পরিণত হয়েছে ভাবলেশহীন ক্রীতদাসে। তাদের না আছে কোন অভিব্যক্তি , না আছে কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধের ক্ষমতা । তার ডাকও শুনতে পায় না তারা। কী জাদুবলে তারা এমন প্রাণহীন পুতুলে পরিণত হয়েছে, তা ভেবে পায় না নন্দিনী। আমাদের মনে পড়ে যায় সিনেমায় দেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার দৃশ্য, যেখানে নাজীদের concentration ক্যাম্প থেকে সার দিয়ে বেরিয়ে আসছেন ইহুদীরা – তাঁদের gas chamber এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে-, তাঁদের শরীরে মনে কোথাও কোনো প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই – মাথা সকলের নীচু। এটি কিন্তু রক্তকরবী লেখার দু দশক পরের ঘটনা, যখন রক্তকরবীর নাট্যকার আর পৃথিবীতে নেই।
যা হোক, পাগলের মত খুঁজে বেড়ায় নন্দিনী রঞ্জনকে, তাকে তার ভীষণ দরকার । শুধু ভালবাসার জন্য নয়, তার প্রাণশক্তি দিয়ে আলোবাতাস বইয়ে দেবার জন্যও। কিশোরও খুঁজতে যায় তাকে, নন্দিনীর রক্তকরবীর একটি আভরণ নিয়ে। কিন্তু সেও হয়ে যায় নিরুদ্দেশ। রাজা পরে নিজেই স্বীকার করেন যে কিশোর লুপ্ত হয়ে গেছে। অবশেষে নন্দিনী খুঁজে পায় রঞ্জনকে – প্রাণহীন মৃত – শরীরে তার রক্তের দাগ, যখন রাজা নিজের জালটি নিজেই ভেঙে দেন । নন্দিনীর challenge এর উত্তরে রাজা জানান, হ্যাঁ তিনি সে যে রঞ্জন তা না জেনেই তাকে সাজা দিয়েছেন কারণ সে যক্ষপুরীতে প্রাণের পরশ দিতে চেয়েছিল, খোদাইকরদের মুক্তির স্বাদ দিতে চেয়েছিল । রাজা স্বীকার করেন যে তিনি যৌবনকে মেরেছেন ।কিশোরের ‘ লুপ্ত’ হয়ে যাবার কথাও নন্দিনী জানে রাজার মুখ থেকেই। আর রঞ্জন ও নন্দিনীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসাও যে রঞ্জনের এই পরিণতির একটি কারণ, তাও তিনি প্রকাশ করে ফেলেন। এইবারে নন্দিনী রাজাকে প্রত্যক্ষ challenge জানায়। এতদিন সে চেষ্টা করেছে রাজার মন পরিবর্তনের, আজ সে ডাক দেয় সম্মুখসমরের। রাজা তাকে মৃত্যুভয় দেখান। নন্দিনী জানায় তার একমাত্র অস্ত্র মৃত্যু, মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। নন্দিনী মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। এবারে রাজার সত্যি মন পরিবর্তন হয়, কারণ নন্দিনীকে তিনি বশে আনতে পারেন নি। নিজেই সেই প্রচণ্ড অন্যায় শক্তির প্রতীক ধ্বজাদণ্ডটিকে দুহাতে ভেঙে ফেলেন। অবাক হয় সর্দারসহ তাঁর তাবেদারেরা। নন্দিনী ছুটে এগিয়ে যায় বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, নিয়মকানুন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে। সম্পূর্ণ যক্ষপুরীটিই তো একটি বন্দীশালা। আবার রাজাও যান তার সঙ্গে। আজ এই ভাঙনের কার্যে তিনি তাঁর দোসর হতে চান। কিন্তু তাঁর নিজের তৈরি যন্ত্র, মেশিন, অর্থাৎ সর্দারের নেতৃত্বে সৈন্যদল তাঁর বিরুদ্ধে যায়। অনেকটা আজকালকার ‘ক্যু’ যেন। তবে এইবার ফাগুলাল যেমন ছুটে যায় বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, তেমন অধ্যাপকও সঙ্গ নেন তাদের। আমাদের মনে পড়ে যায় রক্তকরবী লেখার প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরে তৈরি একটি বাংলা সিনেমার একটি দৃশ্যের কথা। সে সিনেমায় সোনা ছিল না, ছিল হীরের খনি। সে দেশের রাজাও ছিলেন অমিতশক্তিধর স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী এবং হীরের খনির মালিক। সে রাজাও নিজেরই যন্ত্রে মগজধোলাই হবার পর ভেঙে ফেলেন নিজের সুবিশাল মূর্তি প্রজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।
বিশু পাগল এই নাটকটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যক্ষপুরীতে একমাত্র সেই নন্দিনীকে বুঝতে পারে। বোধহয় ভালোওবাসে। নন্দিনীর খোলা আকাশের মত হৃদয় তাকেও খোলা আকাশের নীচে নিয়ে যেতে চায়। সে তো আগেই পাগল আখ্যা পেয়েছে। নন্দিনীর প্রকৃত শুভাকাঙ্খী সে, শুধু যে তার প্রতি আকৃষ্ট, তা নয়। একসময় সে সর্দারদের চর ছিল, তখন ছিল আরামে, কিন্তু সে আরাম সহ্য হয় নি তার নিজের। এখন তার মনে বিদ্রোহ। নন্দিনীর সঙ্গে সেও নিয়ম ভাঙতে চায়। চর থেকে খোদাইকরে পরিনত হবার পর তার স্ত্রী চলে গেছে অন্য কারোর সঙ্গে। এই বিশু পাগলকেও রাজার লোকেরা বেঁধে নিয়ে যায় জন্তুর মত, কারণ সেও বিদ্রোহের গান গায়। ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা তাকেও সতর্ক করে নন্দিনীর সম্পর্কে। এবং এসব কথোপকথন ঘটতে থাকে নন্দিনীর সামনেই।
নন্দিনী যখন রাজাকে উদ্বুদ্ধ করছে শেকল ভাঙবার জন্য, তখন ফাগুলাল মুহূর্তের জন্য নন্দিনীকে সন্দেহ করে বিশ্বাসঘাতিনী ভেবে। নাটকের শেষে যখন রঞ্জনের মৃত্যু হয়, নন্দিনী ছুটে চলে যায় নিয়মের বেড়াজাল ভাঙতে, বন্দীশালার দেওয়াল ভাঙতে, পথে পড়ে থাকে তার রক্তকরবীর কঙ্কন, কারণ এসবের প্রয়োজন তার কাছে ফুরিয়েছে। বিশু পাগল, যাকে নন্দিনী বলতো ভাই, সে সেই কঙ্কন কুড়িয়ে নেয়, এই আভরণ কিশোর নিয়ে গিয়েছিল রঞ্জনকে দেখাতে নন্দিনীর চিহ্ন হিসেবে ।
বিশু পাগল গান গায়…”পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে আয়, আয় আয়..” সম্পূর্ণ নাটকটিকে এই গানটি বেঁধে রেখেছে। এ গান মাটির গান। সাধারণ মানুষকে এই গান ডাক দেয় মাঠে ছুটে যেতে, কারণ প্রকৃতিতেই তো মুক্তি। আর ভয়ংকর যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে কৃষিসভ্যতার জয়গান। সোনার খনির খোদাইকরদের ডেকে কৃষিতে ফিরে যেতে বলে এই গান।, কারণ যুগযুগ ধরে কৃষিই ভারতের মানুষকে লালনপালন করেছে। আর মাটির তলায় পড়ে থাকা সোনাকে নন্দিনী বলে পৃথিবীর কবরে পড়ে থাকা মরা ধন। রাজাও কিন্তু স্বীকার করেন যে তিনি মাটির তলার মরা ধন খুঁড়ে আনতে পারেন, কিন্তু জানেন না মাটির ওপরে গজিয়ে থাকা ঘাসের থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করতে। চাইলেও পারেন না। অর্থাৎ নিজের প্রবল অপশক্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ জানান তাঁর কোনো একটি বাড়ি তৈরির সময়ে এক কোণে লোহালক্করের নীচে চাপা পড়ে যায় একটি ছোট্ট প্রস্ফূটিত রক্তকরবীর চারা। অনেক পরে লোহালক্কর সরিয়ে সেই জায়গাটি পরিষ্কার করার সময়ে দেখা যায় গাছটি যে শুধু দিব্যি বেঁচে আছে, তা নয়, আপন মনে ফুলও ফুটিয়েছে সে। রবীন্দ্রনাথ তার অদম্য প্রাণশক্তি দেখে মোহিত হয়ে ‘ রক্তকরবী ‘ নাটকটি লেখার কথা চিন্তা করেন, যদিও তিনি নিজে বলেন এটি রূপক নাটক নয়, এটি সত্য। নন্দিনী এখানে সেই অদম্য প্রাণশক্তির রূপ পরিগ্রহ করে — নারীরূপ। হ্যাঁ, নারীরূপ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অসংখ্য ব্যতিক্রমী নারীচরিত্রর মত নন্দিনীও কোমলতা ও তেজস্বিতায় ভরা একটি অতুলনীয় সৃষ্টি । সে একটি পুরুষকে ভালবেসেও স্বাবলম্বী ও নেতৃত্বগুণের অধিকারী। একটি অবরুদ্ধ ব্যবস্থাকে সে শুধু নিজের প্রাণশক্তির জোরে মুক্ত করতে পারে। নন্দিনীর অর্থ কন্যা বা নারী। নন্দিনী তাই নারীশক্তির প্রতিভূ। রক্তকরবীতে তাই রবীন্দ্রনাথ নারীশক্তিকেও সম্মান জানান। এই নাটকটিতে চন্দ্রার মত অতিসাধারণ একটি মহিলা যেমন আছে, তেমনই আছে নন্দিনীর মত একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রও।
তবে হ্যাঁ, রঞ্জনের মৃত্যু না হলে রাজার পরিবর্তন হতো কিনা সন্দেহ। এ সেই রাজা, যার মুখ দেখা যায় না। আসলে দুনিয়ার সব স্বেচ্ছাচারীরই মুখ ঢাকা থাকে, আর কারোর সঙ্গে কারোর তফাৎই থাকে না যে!
নাটকটিতে শুধু যন্ত্রসভ্যতা বা খনিমালিকের মুনাফা সর্বস্বতা ও লোভের কথাই তুলে ধরা হয় নি, তুলে ধরা হয়েছে স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারের কথাও। এখানে খনিমালিক ও দেশের রাজা একই। শুধু নিজের লাভের জন্য তাঁর প্রজাদের ওপর, সাধারণ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার করতে, তাদের নিপীড়ন করে মেরে ফেলতে পিছপা হন না তিনি। রক্তকরবী যে সময়ে লেখা, অর্থাৎ ১৯২০র দশকে, জোরদার হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের অর্থনীতিকে আরো দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ আরো আরো নীতি প্রণয়ন করছে। সেইসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখ চিরতরে বন্ধ করার জন্য চালাচ্ছে অমানুষিক অত্যাচার ও দমনপীড়ন। রবীন্দ্রনাথ যেমন মুনাফাসর্বস্ব ইংরাজ ও দেশী খনিমালিক, চা বাগানের মালিক ও অন্যান্য শিল্পমালিকদের অত্যাচার দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন ব্রিটিশের স্বেচ্ছাচারিতা। সব মিলে যাচ্ছে রক্তকরবীতে।
রবীন্দ্রনাথ কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করেন নি, তিনি কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি উপনিবেশের ঔপনিবেশিক দেশের রাজার প্রজা। গণতান্ত্রিকতা বা ডেমোক্রেসির অভাব তিনি বুঝতেন। হয়তো এসবই রক্তকরবীতে ছায়া ফেলেছে। রক্তকরবী শেষ হয় ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি দিয়ে, তবে তাকে ছাপিয়ে যায় নন্দিনীর জীবনের বিশালতা, যখন সে দৌড়ে যায় যক্ষপুরীর নিগঢ় ভাঙতে (তাই রঞ্জনের দেওয়া রক্তকরবী তুচ্ছ হয়ে পড়ে থাকে পথের পাশে),এবং যখন সে সেই অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী রাজাকেও সঙ্গে পায়। রাজাকে সে মৃত্যুর কথা বলেও সে পথে হাঁটে না, কিন্তু রাজার মনকে পরিবর্তিত করতে পারে। তাহলে কি এখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিরাচরিত অহিংসার পথে হাঁটলেন? ১৯২০র দশকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম হাঁটছে সশস্ত্র ও অহিংস দুটি পথ ধরেই। রক্তকরবীতে জীবনের জয় হলো, মানুষের জয় হলো।
এত সব আলোচনার পরে মনে হয় রক্তকরবী সৃষ্টির ১০০ বছর পরেও কেন এত চর্চার কারণ? এই নাটক লেখার পরের ১০০ বছর বিশ্বজুড়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। স্টালিনপন্থী রাশিয়ার উত্থান ও পরিবর্তন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের স্বেচ্ছাচারিতা ও নৃশংসতা, অক্ষশক্তির পরাজয়, প্রচুর উপনিবেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, একাধিক দেশের মানচিত্র বদলে যাওয়া ও নতুন দেশের সৃষ্টি, অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে রাশিয়ার আধিপত্য, বাকি পৃথিবীতে আমেরিকার দাদাগিরি, ঠান্ডা যুদ্ধ, কমিউনিজমের পতন, বিশ্বায়ন ইত্যাদি। এতগুলি ঘটনার পূর্বছাপ পড়েছে রক্তকরবী নাটকে। কতখানি সত্যদ্রষ্টা ও ক্রান্তদর্শী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তা ভাবতে অবাক লাগে। এই নাটকটি নাট্যকারের মতে রূপক নয়, ইতিহাস, কিন্তু কোন দেশের ও কবেকার ইতিহাস, তা তাঁরও জানা নেই। চূড়ান্ত পুঁজিবাদ ও ডানপন্থী এবং চূড়ান্ত বামপন্থা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব.. দুটিই যে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়, তা তাঁর মত করে কে আর বুঝবে? তাঁর সৃষ্টিতে তো বারবার তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে তিনি নিজে ভূস্বামী ছিলেন এবং নিজের জমিদারিতে অনেক মানবিক কাজ করেছেন। আসলে সবকিছু ছাপিয়ে তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী। মহামানবের আবির্ভাবে তাঁর বিশ্বাস ছিল। মহামানব কিন্তু কোনো বিশেষ মানব নন, মহামানব হলো মহান মানবজাতি। নন্দিনী সেই মহান মানবজাতিরই প্রতিভূ।
আরো একটি প্রশ্ন আসে মনে। তিনি রক্তকরবীর প্রাণশক্তির কথা বলেছেন। রক্তকরবীর রং হলো লাল – সে তো শুধু যৌবনের রং নয়, রক্তেরও, বিপ্লবেরও। রক্তকরবী লেখার মাত্র ৭ বছর আগে ঘটে গেছে বলশেভিক বিপ্লব… রক্তকরবীর লাল রঙে তার কোনো ছায়া পড়েছিল কি?
সত্যই ‘সত্য’ সত্য তো?
–শ্রমণা বিশ্বাস, কলকাতা
বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ‘প্রকৃতসত্য’ – কে নিয়ে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এটি এখন বিশ্বের বিরলতম বিষয় হিসবে স্বর্ণ-পদক প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম। এই list এর বাকিরা হলেন বিশ্বাস, ভরসা, পরার্থপরতা ও অনান্য। এটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও কিছু “মানুষ” তা লক্ষ্য করেছেন। এবার আমাদের বুঝতে হবে ‘সত্য’ আর ‘প্রকৃতসত্য’ কী? এদের মধ্যে পার্থক্যটাই বাকী? এই একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে, ‘সত্য’ হলো ‘যা আমি বা আমরা চাই’, আত্ম-স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে বাস্তবটাকে আমরা মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করতে পারি সেটা; আর ‘প্রকৃতসত্য’ হলো ‘যে বাস্তবটা বাস্তবে ঘটেছে’। কেমন গুলিয়ে গেলো তাই না? আর এই গুলিয়ে যাওয়ার জালেই আপামর জনসাধারণ নিমজ্জিত। সেই সুযোগ নিয়েই সমাজের বিত্তশালী মানুষেরা সব লাভের গুড় লুটে-পুটে খাচ্ছে আর কর্মব্রতী “মানুষদের” নিঃশেষে শোষণ করছে। আপনাদের সুবিধার্থে একটু ভেঙ্গেই বলি। আপনার boss আপনাকে কোনো কাজ নিয়ে একটা deadline দিলেন কিন্তু সম্পন্ন কাজটা চাওয়া হলো নির্দিষ্ট সময়ের আগে। আপনি তখন বুঝতে পারলেন কর্তৃপক্ষ আপনাকে বেঠিক তথ্য দিয়েছে। আপনি সঠিক তথ্য জানালেও, boss তা মানতে নারাজ। সেই নিয়ে ঝামেলা হলো। তারপর boss এর superior-এর কাছে complain হলো। সেখানে আপনার boss ভুল তথ্যের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করলেন। তিনি উচ্চপদস্থ তাই স্বভাবতই তার কথাকে ‘সত্য’ বলে গণ্য করা হলো। অনায়াসে বিকৃতসত্য, স্বীকৃত সত্য হয়ে গেলো। আপনি নিম্নপদস্থ বলে আপনার প্রকৃত সত্য কথার সত্যই কোনো দাম দেওয়া হলোনা। অর্থাৎ “authority” আর “power” –এর চাপে প্রকৃত সত্য নিদ্রামগ্ন হল। একটা ছোট্ট setup – এর মধ্যে দেখছেনতো কি হচ্ছে? ভাবুনতো, বৃহত্তরক্ষেত্রে একজন “উচ্চ” ও “নিম্ন”- র মধ্যে সত্যের equation টা ঠিক কেমন হতে পারে? সঙ্গত কারণেই বিশ্বজুড়ে সত্যের বর্তমান চিত্রটা ভয়াবহ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “সত্যেরেল ও সহজে”। সেজন্য মানুষ, world’s most intelligent species, সত্যকেই নিজের মতো modify করে নিয়েছে যাতে তা সহজেই মেনে নেওয়া যায়। তাই উঠে এসেছে “Versions of Truth”; ভাবুনতো, কেমন অদ্ভূত না, সত্যেরও “versions”! আমরা কেউ Shakespeare কে চিনি বা না চিনি“ Fair is foul, and foul is fair” করতে আমরা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছি। অর্থ ও ক্ষমতা যার, সত্যতারই ক্রীতদাস। তারা তাদের ক্ষমতা বলে মিথ্যাকে এমনভাবে তুলে ধরবে আপনি কিছু বুঝতেই পারবেন না। আর যদি দুর্ভাগ্যবশত আপনার বুদ্ধিমত্তা সেটিকে পার্থক্য করতে পারে তাহলে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। এইযে কোর্টের এজলাসে থাকা মানুষদের ধর্মগ্রন্থের উপরে হাত রেখে বলানো হয়, “যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বহি মিথ্যা বলিব না” – আপনার কি মনে হয় না, সর্বপ্রথম এটার একটা amendment দরকার?সবাই যদি সব প্রকৃত সত্য অমন গড়গড় করে বলে দেবে তাহলে কি আর কোর্টের কোনো দরকার হতো? আর যে সত্যকে সিলমোহর দেওয়া হলো সেটাই যে প্রকৃত সত্য তারও কোনো guarantee নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তর সত্যকে আড়াল করার জন্যে কত ‘ধনঞ্জয়’ – দের যে বলির পাঁঠা হতে হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। অপরদিকে ভয়ংকর অপরাধীরা প্রতিপত্তির জোরে এলাহি জীবনযাপন করছে। রবীন্দ্রনাথের “শাস্তি” গল্পে চন্দরা সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করে তার স্বামী ও ভাসুরকে সারাজীবনের জন্য যন্ত্রণার ভাগীদার করে দিয়ে গেছিল। কিন্তু আমরাতো সময়ের সাথে adapt করে নিয়েছি, গায়ের চামড়া আর মনের পর্দা অনেক মোটা হয়ে গেছে। বিবেকের উঁকিকে পাত্তা দেওয়ার মতো সময় বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই। তাই আমাদের এইসব অন্যায়, অবিচার দেখলে আর গায়ে লাগেনা, মনে দাগ কাটেনা। গা সওয়া হয়ে গেছে পুরো ব্যাপারটা আরকি, এক রকমের “new normal” বিষয়টা। “মানুষ” থেকে হয়ে উঠেছি বিবেকবর্জিত মস্তিষ্ক – বিহীন কেবল একটা অস্তিত্ব।
এইবার কথা হলো এইসব হিজিবিজি সত্যকে সবাইকে তো জানাতে হবে, নইলে এতকাঠ – খড় পুড়িয়ে তাকে বদলে কি হলো? সেই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সকালের প্রিয় Social Media পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেকোন কিছু মুহূর্তের মধ্যে সেবিশ্বজুড়ে সম্প্রচারিত করে। আর মানুষ ‘brain’ নামক যন্ত্রটি কে airplane mode – এ পাঠিয়ে সেই সকল content গোগ্রাসে গিলে ফেলে। খবরের channel গুলো সেইসব audio আর video গুলো অবলীলায় সম্প্রচার করে, আর microscopic অক্ষর দিয়ে লিখে দেয়“ video/audio টির সত্যতা আমরা যাচাই করিনি”। এর কোনো মানে দাঁড়ায়? কজনই বা তা দেখে? তার সাথে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নকল প্রমাণ জোগাড়ের Pandora’s Box. এই সুযোগের সৎ ব্যবহার না করে উপায় কি বলুনতো? কোনো ভালো কিছুর (অপ)ব্যবহার না করলে কি চলে? তাইতো “deepfake” – এর আজকাল এ তোর মরমা। AI – কে দিয়ে home – work করিয়ে নিয়ে কতজন যে আমরা নিজের বলে কতবার চালিয়েছি, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো। এভাবেই ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কখন যে মিথ্যার বীজবপন হয়ে যায় আমাদের মধ্যে তা আমরা বুঝতেও পারিনা। আমাদের ছোট্ট ছোট্ট (অ)কাজের মধ্যে দিয়ে সেই চারাগাছ জল, সার, আলো, বাতাস পেয়ে বড় হয়ে ওঠে নিজেদের অজান্তেই। তারপর যখন টের পাই তখন দেখি গাছটি – ই সব হয়ে উঠেছে, তাকে উৎপাটন করলে নিজেদেরই “নিজের” বলে আর কিছু থাকবেনা! মিথ্যার মহীরুহ কে মেনে নেওয়াই তখন safest option বলে মনে হয়।
বেশির ভাগ শিক্ষিত চাকুরী জীবীরা এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে ‘দূরত্ব ভালত্ব বজায় রাখে’ এরকম একটা নীতি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অশিক্ষিতদের সাথে শিক্ষিতরাও যদি এই পরিস্থিতির থেকে বিমুখ হয়ে যান তাহলে সমাজের অবক্ষয় ঠেকায় কার সাধ্য? তাও কি তারা এর থেকে পার পেয়েছেন? সরকারি হোক বা বেসরকারী, তাদের জীবনের শ্রমের ফসল, সবচেয়ে বড় প্রকৃত সত্য, তাদের চাকরি – আজ আছে কাল নেই। শিক্ষার কাণ্ডারিদের প্রকৃত সত্য আজ নিখোঁজ! তবে কীসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে পরবর্তী দিনের পৃথিবী? কেউ জানেনা এ প্রশ্নের উত্তর কী। যে সমাজে শিক্ষারই সত্যে গরমিল, সে সমাজের অবস্থান, পরিস্থিতিও পরিণতি ঠিক কেমন তা বলা শক্ত। তাই “উত্তম” তার থেকে বেঁচে গেলেও, “মধ্যম” ও “অধম” –র মিথ্যার কালগ্রাস থেকে নিষ্কৃতি নেই; তার black hole – এ সে সকলকে টেনে নিয়ে যাবেই।
এবার প্রকৃত সত্যের দোসর বিশ্বাসের কথা একটু জানা যাক কেনোনা সত্যপ্রমাণ সাপেক্ষ হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তি – মানুষের বিশ্বাসের উপরে নির্ভরশীল। বিশ্বাস ও প্রকৃত সত্যের মতো এখন বিলুপ্তি প্রায়। এদের প্রতি পক্ষ অবিশ্বাস ও মিথ্যা এখন এই বিশাল পৃথিবীর যুগ্ম-সম্রাট। তাই আনাচে-কানাচে যেটুকু বিশ্বাস আর সত্য বেঁচে আছে, তা জয় করতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একটা শিশু এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলো। ২-৩ বছরের সেই অজ্ঞ শিশুকে বিজ্ঞ হওয়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করা হলো। তার পাশে বসে থাকা প্রিয় বন্ধু তার কাজটা নষ্ট করেদিলো শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে নিজেকে ‘better’ প্রমাণ করার জন্যে। ব্যাস, পারিপার্শ্বিক কিছু মানুষের উস্কানিতে আর নিজের রাগের ফলে বাচ্চাটা এখন তার পাশে থাকা সহপাঠীকে আর বিশ্বাস করে না। তারপর ধরুন ক্লাসের ফার্স্ট বয় বা গার্লকে তার একজন শিক্ষক কিছু তথ্য জানিয়ে বললেন, “এটা তোমাদের ক্লাস এ একটু জানিয়ে দিও”। নিজের ফার্স্ট থাকার পথ সুমসৃণ রাখার জন্য সে কথাগুলি সুকৌশলে হজম করে নিলো, এককথায় সত্য-গোপন। আর কি, Teacher চাইলেও সেইভাবে সেই Student কে কি আর বিশ্বাস করতে পারে? মনে হয়না। কোনো অন্যায়ের বিচার আশা করবেন? সেখানেও মিথ্যার দৌরাত্বে আপনি সফল ভাবে নিরাশ হবেন। আপনার জীবনসাথী, সন্তান, ভাই-বোন যে আপনার প্রতি একনিষ্ঠ, সেই সত্য নিয়ে আপনি হয়তো সন্দিহান। এরূপ নানান ঘটনার ফলে আপনার জীবনে যারা নিঃস্বার্থ ভাবে পাশে দাঁড়াতে এসেছিলো, মন চাইলেও আপনি তাদের ‘বিশ্বাস’ করে উঠতে পারেননি। আপনার মনে হচ্ছে এরকম কি হয়! স্বার্থ ছাড়া এ পৃথিবীতে কেউ কিছু করে! দেখলেন তো? কিভাবে অবিশ্বাস আপনার জীবনে জেঁকে বসলো? And the cycle continues… তাই বলা চলে ‘বিশ্বাসের’ বেশ শোচনীয় অবস্থা, মারাত্মক existential crisis – এর শিকার।
এবার মুস্কিল হয় কিছু “মানুষ”, মানে যাঁদের “মান” এবং “হুঁশ” দুটোই আছে, তাঁরা বলে ওঠেন “সত্যমেব জয়তে” (সংস্কৃত: सत्यमेवजयते) অর্থাৎ “সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী”। তাই তাঁরা সত্যের অনুসন্ধানে “সত্যান্বেষী” হয়ে ওঠেন। গল্পের ব্যোমকেশ বক্সী বা ফেলুদার মতো এঁনারা সুস্থ জীবন পান না, তাও তাঁরা সত্যকে পাথেয় করে চলেন। যেমন অনুজ ধর ও চন্দ্রচূড় ঘোষ যাঁরা নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্যে নিজেদের সম্পূর্নজীবন উৎসর্গ করে চলেছেন, প্রকৃত সত্যকে সর্বস্তরে গৃহীত হওয়ার জন্য নিষ্ফল আবেদন করে চলেছেন বারে বারে। এবার যারা মিথ্যের ওপর plastic surgery করে সত্যের কাঁচের রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে তাদের হয় মহাবিপদ। যদি বিদ্রোহের এবং প্রকৃতসত্যের আঘাতে সেই শীষ-মহলচূরমার হয়ে সব জারিজুরি ফাঁশ হয়ে যায় কী হবে? এইসকল স্বার্থান্ধ মানুষদের সৌজন্যে “মানুষ”-দের জন্য তোলা থাকে জীবনাবসান অথবা জীবন্ত নরকে বাস। তাও তাঁরা দাঁতে দাঁত চেপে, অদম্য মনের জোর নিয়ে,আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা করে লড়াই করে যান “সত্যের দারুণ মূল্যলাভ করিবারে”। এই সূত্রেই ওইটুক-টাক প্রকৃত সত্যের দর্শন পাই আমরা। এর থেকেই কেউ কেউ এই মিথ্যার দাস্যবৃত্তি ছিন্ন করারর সদ পায়।
এর অন্তিমে পৌঁছানোর আগে আমাদের এইসব গুলিয়ে দেওয়ার যিনি “গুরু” তাকে স্মরণ করা অন্তত্য জরুরী, তিনি হলেন আমাদের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ – রাজনীতি। না না, আর বেশী মুখ খুলবো না, পালাবেন না। এবার আরেকজনের কথা বলি, এই সত্য আর মিথ্যার যোগ্য সন্তান-অর্ধ-সত্য। তার শক্তি যে কত তা আমাদের “মহাভারত”-ই জানিয়ে দিয়েছে। এরপরিবার এতটাই প্রভাবশালী তাদের একটা যুগ আছে – উত্তর-সত্য। বুঝলেন কিছু? উঠুন এবার ঘুম থেকে! চোখ খুলুন! আর কতদিন ignore করে যাবেন? এই ভয়ংকর যুগে আমরা সবাই belong করি। তাই বাঁচতে গেলে আমাদেরই লড়তে হবে। শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে আর কদ্দিন? এর শুরু মানুষ করেছে তাই এর ইতি মানুষকেই টানতে হবে! কেবল মজার ছলে না পড়ে “ভাবুন, ভাবুন, ভাবা প্র্যাক্টিস করুন”!
সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। প্রকৃত সত্যের প্রদীপ আজও নিভে যাইনি। তা ধিক ধিক করে হলেও জ্বলছে। আমাদের আগামী দিন গুলোকে বাঁচাতে এই আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিতে হবে যা সত্যের মোড়কে জড়ানো মিথ্যেকে জ্বলিয়ে – পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেবে। এমন এক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে যা প্রকৃত সত্যকে অস্ফুটে সামনে আসার অভয় দেবে। এই যুদ্ধে জয়লাভে সংবেদনশীল মানুষ গঠিত সৈন্যদের প্রয়োজন যারা সকল বাঁধা উপেক্ষা করে, শুধুমাত্র আগামীকে রক্ষার্থে এগিয়ে চলবে। কি, পাশে থাকবেন তো?