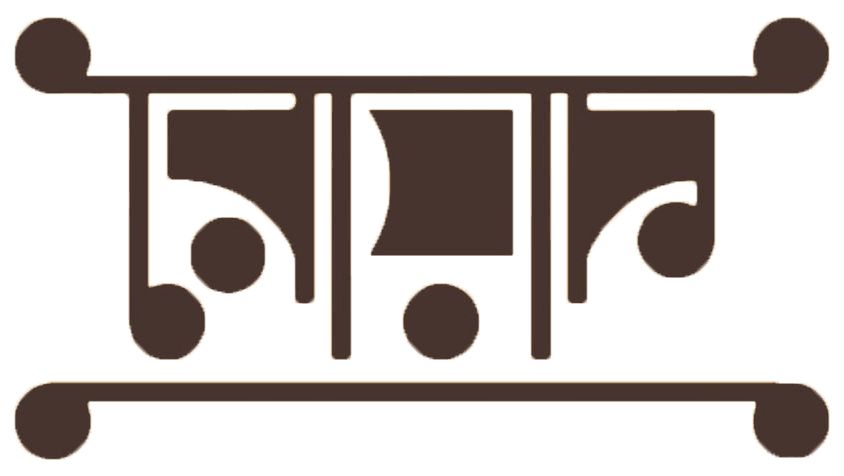দ্বিতীয় বর্ষ ✦ দ্বিতীয় সংখ্যা ✦ সাক্ষাৎকার
লিটিল ম্যাগাজিন এর ভবিষ্যৎ কি? লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি-এর পিছনের আন্দোলন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? বর্তমান সময় যখন দু’মিনিট যাপনে ব্যস্ত সেখানে পড়াশোনা করা, করতে চাওয়া মনন কে কীভাবে তৈরি করা সম্ভব? – এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে মুখোমুখি কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের পুরোধা, প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সন্দীপ দত্ত’র। রোয়াকের তরফ থেকে দেবার্ঘ্য দাস এবং গৌরব রায় সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন। অনুলিখনে টিম রোয়াক।

রোয়াক ♦ এই লাইব্রেরি শুরু করার ভাবনা কোথা থেকে পেলেন?
সন্দীপ দত্তঃ আসলে ব্যাপারখানা যে এইভাবে হবে তা আমি জানতাম না। কারণ কোনো ধারণা থেকে তৈরি হয়নি। এটা একটা ঘটনাক্রমে ঘটলো।যার জন্য আমিও আগে থেকে প্রস্তুত ছিলাম না। সালটা ১৯৭২। স্কটিশ চার্চ কলেজে পার্ট টু পরীক্ষা দেব। ওই অনার্স পড়ার সূত্রে ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতাম। একদিন দেখি বহু লিটিল ম্যাগাজিন দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে বাংলা-বিভাগের সামনে।সংগতই কৌতুহলী হলাম ইতিমধ্যে আমিও একটি পত্রিকা করতে শুরু করেছি নাম ‘পত্রপুট’ আমি আনন্দের সঙ্গে উৎসাহ নিয়েই বাংলা বিভাগের যিনি দায়িত্বে ছিলেন ঐদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম এইগুলো কেন বেঁধে রাখা- তিনি জানালেন এগুলো রাখা হবে না কারণ নিয়মিত বেরোয় না এবং ছোট-বড়-মাঝারি অদ্ভুত সাইজের বাঁধাই করতে অসুবিধে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি.. এই যে বই ম্যাগাজিনগুলো আর রাখা হবেনা তা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলো না, আমার রীতিমতো অপমানিত বোধ হলো, লাইব্রেরী সেই মুহূর্তেই ত্যাগ করলাম। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস ছাত্রজীবন চলছে, পার্ট-টু পরীক্ষা হয়ে গেছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী কে উত্তর দেওয়ার জন্য অনেক দিন ধরেই মনের ভিতরে কি রকম একটা করছিল; ঠিক করলাম এর জবাব দেব প্রদর্শনীর ভাষায়! প্রদর্শনীর জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার অর্থ দরকার। আস্তে আস্তে সেইসবও হলো। প্রদর্শনী বলতে সবাই বুঝতো চিত্র প্রদর্শনী লিটল ম্যাগাজিনের প্রদর্শনী সবাইকে বোঝানো একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল ;কিন্তু দরকারও ছিল। সঙ্গে উপরি হিসেবে ডেকোরেশন লাইট এর খরচা ছিল। যাহোক করে সাড়ে সাতশো ম্যাগাজিন নিয়ে প্রদর্শনীটা শেষমেশ করেই ফেললাম। তখনও পাঠাগার পুরোপুরি ভাবে গড়ে ওঠেনি। বছর ৬ পর লাইব্রেরী গড়ে উঠলো। প্রদর্শনীর জোগাড় পর্বটাও ছিল সাংঘাতিক। এদিক ওদিক খুঁজে কিছু পেলাম। কিছু কিনলাম। এইভাবে চারদিন ধরে চলেছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরির ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কফি হাউজ বাড়ির কাছে হলেও যাতায়াত সেইভাবে ছিল না নিজের ম্যাগাজিন থাকার সূত্রে কিছুর লেখক এর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও কফি হাউসে গিয়ে লেখক মহলের সাথে উঠাবসা পুরো হয়নি প্রদর্শনী দেখতে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যেই অনেকে কফি হাউসে যাবার নিমন্ত্রণ দিলেন সেই থেকেই শুরু হয় কফি হাউসে যাতায়াত, এইভাবে কেটে গেল বছর ৬-৭। আমার স্টাডি টেবিল তিনতলায় ছিল তাকে এই একতলার ঘরে নামিয়ে আনলাম, সবুজ রঙের কাঠের র্যাক যেখানে অনেক বাসনপত্র রাখা থাকে নিয়ে আসা হলো। যতগুলো বই ধরানো যায় রাখা হল বাদবাকি দড়ি দিয়ে টাঙ্গানো থাকতো। ছ’টা চেয়ার তৈরি হলো, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন যাকে বলে সেই ভাবে কিছুই হয়নি তখনো নিজের ডায়েরিতে সবুজ রঙের কালি দিয়ে লিখেছিলাম ‘শুরু করলাম সাময়িকপত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র – টু ডু সামথিং কনস্ট্রাক্টিভ, জুন৬, ১৯৭৮।’ যাত্রা তো শুরু হলো চেয়ার-টেবিলে ও এলো ও রাখা হলো ।তা সত্ত্বেও আসল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছিল পাঠক কোথায়? এইসব চিন্তার মধ্যেও এইভাবেই দেশের প্রথম লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর জন্ম হলো।
রো ♦ যে বিদ্রোহ, থুড়ি কাউন্টার দ্রোহ আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন এর প্রেরণা কী?
সঃ দঃ আমি যখন শুরু করি তখন ব্যাপারটা ছিল শূন্যতার মধ্যে ভাসমান ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই কেটে যাচ্ছিল যে হোয়াট ইস লিটল ম্যাগাজিন মানুষদের মধ্যে বিস্তার করানো কিভাবে সম্ভব তখন চার আনা থেকে ৫ টাকা ৪ টাকা অবধিও ম্যাগাজিন পাওয়া যেত। ১ টাকায় তো আকছাড় পত্রপত্রিকা পাওয়া যেত, খাসির মাংস ৩০ টাকা ছি্ল, ইলিশ মাছ তো সেই যুগে এক টাকায় পাওয়া যেত। লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী করার ক্ষেত্রে আমার প্রেরণা ছিল আমার আত্মবিশ্বাস।লিটিল কথাটির বিপরীতে আছে বিগ- মানে বিশাল, এই বিশালত্ব দেখে মোটেই ভয় পায়নি মনে হয়েছিল এর বিরুদ্ধে দাঁড়াই একবার। ঘটনার প্রতিবাদে যাওয়াটা সাধারন ছিলনা। তখন তো আজকের মত প্রচার সহায়ক বৈদ্যুতিন মিডিয়া ডিজিটাল দুনিয়া ছিলনা, কাছে পৌছানোর প্রধান রাস্তাটাই ছিল মৌখিকভাবে, বিভিন্ন বইমেলা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান স্টলে স্টলে গিয়ে বলে আসতে হতো লাইব্রেরী খুলেছি। কেউ কেউ এলো কেউ কেউ এলোনা। আমার বিশ্বাস ছিল এইযে এতো লিটিল ম্যাগাজিন যার মধ্যে সাংঘাতিক সৃজনশীল মন রয়েছে, সর্বোপরি কিছু একটা করার তাগিদ রয়েছে তা কি চাপা পড়ে যাবে ? কোন মোহনায় যাবে ? এই হদিশ খুঁজতে খুঁজতেই এই লাইব্রেরি। তাহলে এবার একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে – যদি ন্যাশনাল লাইব্রেরির ঘটনা না ঘটতো হলে কি এইভাবে লাইব্রেরীর জন্ম হতো? আসলে সব ঘটনারই একটা ট্রিগার পয়েন্ট থাকে পরম্পরা থাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির ঘটনাটা না ঘটলে আজকের দিনে এই লাইব্রেরির অবস্থানটা এইভাবে আসতো না কিন্তু পৃথিবীর অদৃশ্য ইতিহাস ঘটে গেল আমারই হাত দিয়ে। ইতিহাসটা নিজের প্রয়োজনেই, লাইব্রেরী ম্যাগাজিনের প্রয়োজনে, শুরুর দিকে কোন পাঠক ছিল না, মাইক নেই, মিডিয়া নেই, কোনও কোনও দিন পাঠক আসছে কিন্তু রোজ প্রত্যেকটা দিন নিয়ম করে লাইব্রেরী খুলে রাখা সেই বিশ্বাস থেকেই ধৈর্য থেকেই বসে থাকা। আমি জিনিসটাকে এই ভাবে দেখতাম পত্রিকা পাঠক সংযুক্তি আন্দোলন । আমাদের পারিবারিক জুতোর ব্যবসা ছিল।অনেকেই চাইত আমি জুতোর ব্যবসায় না ঢুকে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যেন আমি যুক্ত হই। আমার স্বপ্ন পূরণ করতে সিগারেট ছেড়ে দিলাম, যাতে আরো পত্রিকা কিনতে পারি। তিন পয়সার পালা নাম দিয়ে একটা পিগি ব্যাংক করলাম।এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা দিয়েও পত্রিকা কিনেছি। শিল্পী তিনিই কোন অবস্থাতেই যার শিল্পী মননের কাজ করার তাগিদ বন্ধ হয়ে যায় না, ঠিক যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “শিল্পী”। তাই প্রথম ১৮ বছর ধরে আমি সময় এর কাছে বিশ্বাস রেখেই আমি আমার কাজটা করে যাবার চেষ্টা করেছি। দুঃসময় মধ্যেও রাতভর চেয়ে অনন্ত বিপ্লবকে আমরা খুঁজে বেড়াই। পৃথিবীর এই অসুখের স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিলাম আর-কি! লিটল ম্যাগাজিন কি? নতুন লেখক, চিন্তা, স্পর্ধা, সৃজনশীল মনের জন্ম দেয়। কিন্তু আমি যখন লাইব্রেরী শুরু করেছি দিনরাত অপেক্ষা আমাকে করতে হয়েছে। আমিও বিশ্বাস হারাতে পারতাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল এখানে আসতে হবেই পাঠককে। ম্যাগাজিন শব্দটার দিকে যদি তাকাই তাহলে এর সঙ্গে আমরা কার্তুজের মিল পাব। .১৭৩৪ সালে এডওয়ার্ড টীম ইংল্যান্ডে প্রথম এই শব্দটি নিয়ে এলেন তার “জেন্টলম্যান ম্যাগাজিন”-এ। এর আগে রিভিউ জার্নাল ইত্যাদি শব্দ থাকলেও ম্যাগাজিন শব্দটা পপুলার হয়ে গেল। বন্দুকে গুলি রাখার বাক্স কে ম্যাগাজিন বলা হচ্ছে তাই তো কাগজের অনেকগুলো পৃষ্ঠায় যদি গল্প কবিতাকে ঠুসে ঠুসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে তা ম্যাগাজিনের রূপ ধারণ করে। আসলে লিটল ম্যাগাজিন বাণিজ্যিক প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে একটা বহমান লড়াই যে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সৃজনশীল লেখা কে তুলে আনা হয়। আমার জয় এখানেই যখন দেখি দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পড়ুয়াদের ভিড় এই পাঠাগারে লেগেই রয়েছে, সে তারা কেন আসছে সেটা তখন গৌণ হয়ে যায়। আসাম থেকে, গোয়াহাটি থেকে, জেএনইউ থেকে, লন্ডন থেকে, ডাচ ইউনিভার্সিটি থেকে, চায়না থেকে, ইউরোপ থেকে পাঠক আসে তখন বুঝতে পারি কোথাও একটা ঐতিহাসিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, এমন একটি জায়গায় যেখানে মণিমুক্তো আছে, রত্ন খুঁজলেও পাওয়া যাবে।
রো ♦ হাংরি আন্দোলন বা নকশাল আন্দোলনের প্রভাব কি আপনার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী তৈরিতে পড়েছিল ?
সঃ দঃ একটা সময় কালো টাকা সাদা করতে অনেকে প্রযোজক হয়ে যাচ্ছিলেন।বিভিন্ন হলে এমনকি পেশাদারি রঙ্গমঞ্চগুলোতে ক্যাবারে নাচ ভরে যাচ্ছিল।সংস্কৃতির এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নকশালরা প্রতিবাদ করেছিল।এই প্রতিবাদ হয়ত আমার অবচেতনেও ঢুকে পড়েছিল। একজন ৩০ টাকা মাইনের সামান্য চাকর উত্তরের চা বাগান করঞ্জি এলাকা থেকে এসে এখানে তিলোত্তমা বলে একটি কাগজ বের করেছিল।তখন আমার মনে হয়েছিল ও যদি পারে তাহলে আমি কেন করব না? উনিশ শতকে অনেক প্রতিষ্ঠান হয়েছিল।বিশ শতকের শুরুর দিকেও কিছু হয়েছে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানে সরকারি মদত থাকে।কিন্তু এই লাইব্রেরী কোনও মদতে নয় তাগিদে হয়েছে। ১৯৮৬ সালে এই লাইব্রেরী Registered হয়। নাম হয় লিটল ম্যাগ লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র। কলিকাতা শব্দটা যুক্ত হয় ১৯৯৬ সালে।
রো ♦ আপনার সাথে আলাপচারীতায় Space শব্দটা বারবার ফিরে এসেছে। এই লাইব্রেরী এর স্পেস বা পরিসর খোঁজার ভাবনা নিয়ে যদি কিছু বলেন।
সঃ দঃ Space এটা একটা অদ্ভত শব্দ।বাংলায় জায়গা বা অবস্থান। জীবন যাপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করি। কাজের মধ্যে,জীবনের মধ্যে, লেখার মধ্যে, চলচিত্রের মধ্যেও স্পেস চাই। নীরবতা ও সরবতা দুই-ই থাকতে হবে। এই লাইব্রেরী শুরু হল আমার নিজের বাড়িরই একটা ঘর থেকে। তারপর আস্তে আস্তে যত পত্রিকা বেড়েছে জায়গা কমেছে। পেরেক, ক্যালেন্ডার পুঁতে যেন আমি নিজেই নিজের বাড়িকে দখল করেছি। আমি নিজেই যেন সাম্রাজ্যবাদী। আসলে স্পেস কেউ দেয় নি বা দেয় না।নিজেকে তৈরী করে নিতে হয়। অনেক বাধাপ্রাপ্ত হলে জীবনে দুটোর মধ্যে কোনও একটা তোমাকে বেছে নিতে হবে হয় তুমি ছেড়ে দাও বা লড়াই কর নিজের বিশ্বাস নিয়ে স্বপ্নের জন্যে।এই লড়াই কারোর বিরুধ্যে নয়।যারা বলেছিল লিটল ম্যাগাজিন করে কিছু হয় না।আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তে প্রদর্শনী ও সেমিনার করেছি।তাদের ডেকেছি।এটা আসলে আমার নয় লিটল ম্যাগাজিনের জয়।আমার মন্ত্র ধৈর্য-বিশ্বাস-ধারাবাহিকতা।
রো ♦ এই ভাইরাল সভ্যতা বা কারেন্সি সভ্যতার যুগের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আপনার এই যে উলম্ব যাপন বা দ্রোহ তাঁর জন্যে আপানকে কুর্নিশ। আপনি কি বিশ্বাস করেন এই কাউন্টার কালচারটাই একমাত্র উত্তর। কিন্তু কজন পাঠক লিটল ম্যাগাজিন থেকে খুঁজে বের করে প্রবন্ধ বা কবিতা পড়ছেন না পড়বেন?
সঃ দঃ আমার কাছে কিন্তু শান্তিনিকেতান, নৈহাটি, বাঁকুড়া এমনকি সুন্দরবন থেকেও ছাত্র ছাত্রীরা আসছেন। কেউ গবেষণার কাজে আবার কেউ জানতে আসছেন। ১৬ই জুন, ১৯৮১ সালে আনন্দবাজারের কলকাতা কড়চা তে প্রথম লাইব্রেরী সম্পর্কে লেখা বেরোয়।তার আগে কেউ জানত না। এছড়াও আমেরিকার Smithsonian Institute এর ম্যাগাজিনে আমার কাজ আলোচিত হয়েছে। এমনকি Sweden National Library এর “Swedish Bibilothek”এ সুইডিশ ভাষায় আমার কাজের কথা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোই তো প্রাপ্তি। আমার এই লাইব্রেরীতে মহাশ্বেতা দেবী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়,সুনীল গাঙ্গুলি,শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, চিন্ময় গুহ, ব্রাত্য বসু অনেকেই এসেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প আমি ওনাদের খুঁজে দিতে সাহায্য করেছি। একবার মহাশ্বেতা দেবী ফোন করে বললেন, “সন্দীপ ডুবেছি উদ্ধার কর”। ওনাকে ১৫ টা গল্প উদ্ধার করে দিয়েছি।
রো ♦ এই মুহূর্তে প্রবন্ধের অবস্থা কিরকম বলে আপনার মনে হয়?
সঃ দঃ ভাষাগত, বিষয়গত ও বিন্যাসগত ভাবে পাল্টে গেছে। এখন বহুমাত্রিক লেখালেখি হচ্ছে। একসময় সমাজ বিষয়ক লেখা বেশি ছিল। আজ বিশ্বায়ন ঘটে গেছে। সমাজে বহু বিষয় উঠে আসছে যেমন বিকল্প যৌনতা। সেই সঙ্গে অন্তর্ঘাত বেড়েছে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে, পপুলার রাজনীতির চর্চা হচ্ছে যা স্বদেশী রাজনীতির থেকে অনেক আলাদা। এই সবের প্রভাব দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ের প্রবন্ধে। প্রবন্ধ মানে তো প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। এর জন্য জীবন বোধ লাগে, বাঁধুনি লাগে, চেতনা লাগে।
রো ♦ এবার আপনার লাইব্রেরী বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পত্রিকার ব্যাপারে আপনার থেকে কিছু শুনতে চাই।
সঃ দঃ এই লাইব্রেরী তে কয়েকহাজার পত্রিকা রয়েছে। ৭০ টা বিষয় ভিত্তিক ভাগ করে রাখা আছে। দুর্লভ পত্রিকার মধ্যে বঙ্গদর্শন ১৮৭২ এর প্রথম সংখ্যা,ক্যালকাটা পুলিশ জার্নাল ১৯৩৯ এর প্রথম সংখ্যা। প্রবাসী, জিজ্ঞাসা, ভারতবর্ষ অনেক সংখ্যাই আছে।মাসিক বসুমতি সব সংখ্যাই আমার সংগ্রহে আছে। এছাড়াও এক্ষণ, কবি ও কবিতা, পরিচয় এর মত পত্রিকাও আছে।
রো ♦ প্রিন্ট মিডিয়া থেকে হালের ওয়েবজিন এই বদলটা কিভাবে দেখেন? আপনার এই বিপুল সংগ্রহকে Digitisation এর কথা কি ভেবেছেন? কতটা হয়েছে?
সঃ দঃ ২০০৭ সালে IFA (Indian Foundation for Arts) এর থেকে ৫ লাখ টাকা অনুদান পেয়েছি।সেই অনুদানে সাহায্যে ১৪০০ পত্রিকা ডিজিটাইজ করা গেছে।তবে সবটা করার পরিকল্পনা আমার নেই। বিশেষ পত্রিকা বা বিশেষ সংখ্যাগুলোকেই আমি প্রাধান্য দেওয়ার কথা ভেবেছি ডিজিটাইজেশান এর ক্ষেত্রে। একটা খারাপ লাগা আছে সরকারের তরফ থেকে কোনও অনুদান পাইনি।একটা ঘটনা তোমাদের বলি,২০১৮ সালে মালদাতে আমার একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেটি টিভি তে দেখান হয়। টিভি তে দেখে একজন আমাকে ফোন করে নিজের বাড়িতে ডাকেন। শেক্সপিয়ার সরনীতে ওনার বাড়ি গেলাম। লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে ওনার আগ্রহ চোখে পরার মত ছিল। বাড়ি ফেরার সময় উনি আমাকে ২৫,০০০ টাকার চেক দিলেন। আবার আমি খোঁজ পেলাম কালিন্দীতে থাকেন এক ভদ্রলোকের। ওনার কাছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পুরো সেট ছিল। উনি ১২০০ টাকা চাইলেন। আমি ওনাকে আমার পরিচয় দেওয়াতে উনি ৭০০ টাকায় পুরো সেটটি আমাকে দিয়ে দিলেন।সাথে দিলেন বর্ধমান মহারাজার দেওয়া দুর্লভ মহাভারত। ডঃ ঊর্মিলা চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি কলেজে ইংরেজি পড়াতেন, ৫০,০০০ টাকার অনুদান দিয়েছেন।
রো ♦ এই লাইব্রেরীর ভবিষ্যৎ ভাবনা বা উত্তরাধিকার কাকে দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে?
সঃ দঃ আসলে কি বল তো উত্তরাধিকার হয় উত্তরাধিকারী হয় না।যদি ট্রাস্টি করি তাহলেও কিছু হবে না। তবে কবিতা পত্রিকাগুলোকে আলাদা করে রাখার জন্যে পাটুলির কাছে একটা জায়গা বাছা হয়েছে। সেখানে শুধু কবিতা পত্রিকা থাকবে।আগামী অক্টোবর মাসে ওটা শুরু হওয়ার কথা। সপ্তাহে দুদিন ওটা খোলা হবে।আসলে পেশাদারিত্ত্ব না থাকলে কোনও রক্ষণাবেক্ষণই সম্ভব নয়। মানুষ কেই এগিয়ে আসতে হবে নিজের ভাষার জন্যে বাংলার জন্যে লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আমি চেষ্টা করেছি এখনও করে যাচ্ছি। এই প্রক্রিয়াটা চলবে। তবে এই জীবনে আমার “স্বপ্নের চেয়ে বেশি পাওয়া হয়ে গিয়েছে”।
 ঠিকানাঃ ১৮/এম টেমার লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কোল – ৭০০০০৯
ঠিকানাঃ ১৮/এম টেমার লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কোল – ৭০০০০৯