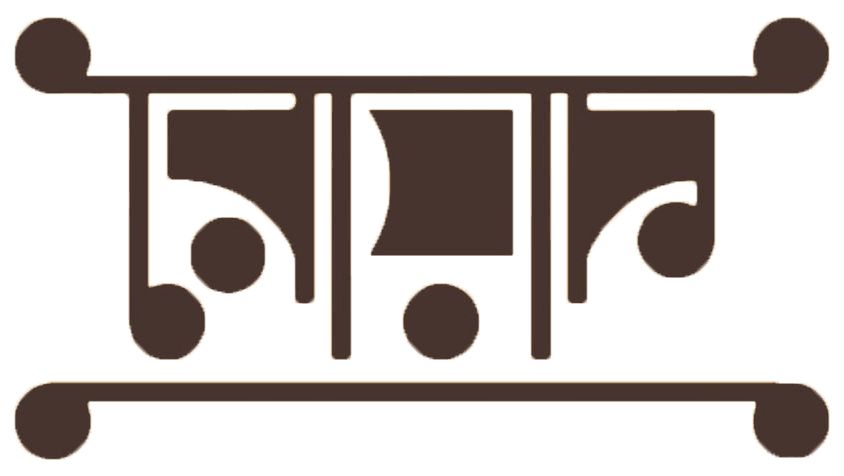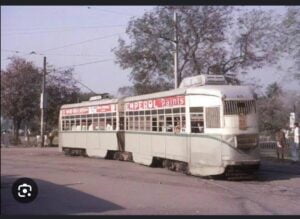তৃতীয় বর্ষ ✦ প্রথম সংখ্যা✦ সাক্ষাৎকার
দেড়শো বছরে কলকাতার ট্রাম…
অঞ্জন দত্তর সাথে কথোপকথনে
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : কলকাতার ট্রামের দেড়শো বছর হল। আপনার কাজে ও জীবনে শহর, অতীত, নস্টালজিয়া, শেকড় নানাভাবে এসেছে। পুরোনো সবকিছুকে নিয়েই আপনি নতুনের দিকে বারবার গেছেন।
অঞ্জন দত্ত : কলকাতা খুবই পুরোনো একটা শহর। যে কোনও পুরোনো শহরের মতই এ শহরেও কিছু কিছু জিনিস খুব জরুরি হয়ে যায়। যেমন, কিছু ঘরবাড়ির স্থাপত্য, রাস্তাঘাট, যানবাহন, এই সবটা মিলে একটা শহরের ঐতিহ্য তৈরি হয়৷ ট্রাম খুব কম শহরে আছে এখনও কিন্তু যেখানে যেখানেই আছে, বেশিরভাগই পুরোনো শহর। এসব শহরের অনেকদিনের একটা ইতিহাস আছে। আমাদের কলকাতার বৈশিষ্ট্যও ট্রাম- যা ভারতের আর কোনও শহরে সম্ভবত নেই। এখনও ট্রামকে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং এই রেখে দেওয়াটা খুব জরুরি একটা ঘটনা আমার কাছে। কারণ এটা অসংখ্য ইতিহাসকেও একই সাথে বয়ে নিয়ে চলেছে। দিল্লিতে যেমন একটা বড় পাড়ার মধ্যে হঠাৎ হুমায়ুন’স টেম্পল! দুটো পাড়ার মধ্যে সেটা রয়ে গেছে। কারণ দিল্লির নেপথ্যে একটা দীর্ঘদিনের মোগল ইতিহাস রয়েছে। আমাদের এখানে সেভাবেই ট্রামটা দেড়শো বছর ধরে চলছে। এতে হয়ত রাস্তাঘাটে বাকি গাড়িঘোড়ার চলতে একটু অসুবিধেও হচ্ছে। কিন্তু এ অসুবিধেটা হবে এবং সেটাকে মেনে নিতেই হবে। কিছুদিন আগে ট্রাম নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকা হয়। সেখানে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে আরও লোকজন আসেন। তো, সেখানে জার্মান, অস্ট্রেলিয়ান কিছু সাহেবও ছিলেন। তারা বললেন, সরকারের সিদ্ধান্ত কিছু কিছু শহরে তারা ট্রামটাকে চালাবেন। বাকি বেশিরভাগ জায়গাতেই তারা পারছে না চালাতে। কারণ রাস্তাঘাটের বহু জায়গাতেই খারাপ অবস্থা। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় চলবে। সেখানে পরিবহণ মন্ত্রী আরও বললেন, বেড়াবার কথা মাথায় রেখে কিছু কিছু জায়গায় ট্রামটা চালানো হবে এ শহরে। এসপ্ল্যানেড থেকে ময়দান হয়ে সেটা নানাদিকে যাবে। যেমন টয়ট্রেনটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে ‘জয় রাইড’ হিসেবে। দার্জিলিংয়ে যারা বেড়াতে যাবে, নামার সময়ে অনেকটা এগিয়ে নামা যাবে এই রাইডে। কিন্তু মূলত পর্যটনের বিষয় হিসেবেই ট্রামকে দেখছি কেন আমরা! আমার মত, তার পাশেই ট্রাম রোজকার যানবাহন হিসেবেও থাকুক। ঠিকই, ট্রাম হয়ত ধীরে চলবে কিন্তু বাসের তুলনায় ভিড়টাও তো কম হবে! আর কিছু মানুষ তো একটু ধীর প্রকৃতিরও। একটু ধীরে গেলেও তাদের সুবিধেই হবে হয়তো। ভাড়াও কম ট্রামে। তাঁদের জন্য ট্রামটাকে যদি আমরা রোজের জীবনে ঢুকিয়ে আনতে পারি, আমার ভালোলাগবে।
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : আপনার বাড়ির একদম কাছেই নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো…
অঞ্জন দত্ত : হ্যাঁ, তবে আমাদের বাড়ির কাছে এই মধ্য কলকাতার নোনাপুকুর ট্রামটা আদৌ থাকবে কি না, জানি না। এবং এটার জন্যে এই এলাকায় ট্রাফিক জ্যামও বাড়বে। কারণ এলিয়ট রোডে ট্রাম চললে জ্যাম বাড়বে আরও। কিন্তু এ রাস্তা দিয়ে সোজা ওদিকে গড়িয়াহাট আর এদিকে রাজাবাজার ছাড়িয়ে যদি ট্রামরাস্তাটা রাখা যায়, তাহলে চমৎকার লাগবে আমার। আর, ডালহৌসি এলাকাতেও যদি ট্রাম চলে তাহলে শুধু শো-পিস হয়ে যাবে না ট্রামটা, রোজকার যানবাহন হিসেবেই থাকতে পারবে। যেমন, শিলিগুড়ি থেকে টয়ট্রেন চাপার বদলে এখন সবাই তাড়াতাড়ি গাড়ি চেপে চলে যাচ্ছে দার্জিলিং। কার্সিয়ং হয়ে কেউ আর কাজের সূত্রে আসছে না, ফিরছেও না। কিন্তু কিছুলোক যদি এই টয়ট্রেন কাজের জন্য ব্যবহার করে, তাহলে টয়ট্রেন বা ট্রামের মূল্যটা থেকে যাবে। এই যে অনেকক্ষণ ধরে সে উঠছে, এতে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতেও তো সুবিধে! হয়ত এই ট্রেন চলায় পাহাড়ের ক্ষতি হবে…কিন্তু একশো বছরের ওষুধের দোকান বা মিষ্টির দোকান বা মদের দোকান থেকেই তো তারা এখনও জিনিস কিনছে।
তাহলে কেনোএই পুরোনো যানবাহনগুলোকে চালানো যাবে না? তবে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ কর্পোরেশানের কাছে তারা এখনও হাজার সমস্যার পরেও ট্রামটা রেখেছেন। জল জমা রাস্তা থেকে ট্রামের তাড় জড়িয়ে যাওয়া—কম তো সমস্যা হয় না! কিন্তু তারা রেখেছেন ট্রামটা এরপরেও…কারণ ট্রাম চলা মানে একটা সময়ের কলকাতা সচল থাকা…আমি কলকাতার ট্রামের এই ১৫০ বছর দেখে যেতে পারলাম, এ তো আমারও সৌভাগ্য!
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : বাদল সরকারের কাছে আপনি যখন অভিনয় শিখতে যান, তিনি আপনাকে ট্রাম ও এ শহর ঘিরে কিছু কথা বলেছিলেন…
অঞ্জন দত্ত : হ্যাঁ। উনি আমাকে বলেছিলেন, একটা শহরের স্থাপত্য-যানবাহন তাঁর মানসিকতা তৈরি করে। সে সুবাদেই তিনি ট্রামটাকে দেখিয়েছিলেন দূর থেকে.. কারণ ট্রামটায় উঠতে বা নামতে আমাকে তো লাফাতে হবে! কিন্তু ভেতরে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ ধীরে চলার ব্যপার। তো, এই গতিটা কিন্তু আমার শরীরে ঢুকে যাবে। এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু নিউ ইয়র্কে পাব না! কারণ সেখানে অনেক ডায়নামিক লোকজন..উঁচু উঁচু বাড়ি। আর, আমাদের এই ধীর গতির জন্যেই আমরা অনেকবেশি সেনসেটিভ…প্রত্যেকটা শহরের মানুষের কিছু জোরের জায়গা আর কিছু ভিজিবিলিটি থাকে। আমাদের স্ট্রেন্থ এটাই, আমরা সব ব্যাপারে একটু বেশি সংবেদনশীল। এ শহরে রাস্তায় গরু বসে পড়েছে…কত কুকুর-বেড়াল-পায়রা পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে, এটা অন্য শহরে সম্ভব না। এই মানসিকতাটাকে বাঁচিয়ে রাখে এ ধরণের পুরোনো জিনিস। রাস্তার নাম হোক বা ট্রাম তাই আমার কাছে খুবই জরুরি। এগুলো বদলে গেলে খুবই অসুবিধে হয়। যেমন ল্যান্সডাউন রোড কি অসুবিধে হচ্ছিল খুব? যে এজিসি বোস রোড করতে হল? বা, কর্নোওয়ালিশের স্ট্যাচুটা সরিয়ে অরবিন্দ বসালে কি খুব দেশজ হয়ে যাচ্ছি রাতারাতি? মোটেই না। আরো বরং সাম্রাজ্যবাদ বাড়ছে কারণ আরও ৩৬টা কদাকার শপিংমল তৈরি হবে এরপর। অথচ ওই মূর্তিটা তো আমার ইতিহাসের অংশ ছিল, সেটা তো আমাকে ধরে মারছে না! স্ট্যাচু হয়ে আছে সেটা…অজান্তেই আমার ভেতরে ভেতরে কাজ করে চলেছে সেটা…রাস্তার নাম গ্রে স্ট্রিট, অসুবিধে কোথায়? ইউরোপ কি এসব বদলে দেয়? সম্ভবত না। তুরস্কে একটা পার্ক দুম করে বন্ধ করা যাবে না। কিছুদিন আগে পার্ক বন্ধ করার জন্যে প্রায় একটা জনযুদ্ধ পরিস্থিতি হল সেখানে। আমার কাছেও আমার শহরের নানা জায়গার আগের নামগুলো জরুরি, এগুলো বদলে গেলে আমার খারাপ লাগে।
ট্রামের নিয়ম হল, ট্রামলাইনের সামনে যদি কেউ চলে আসে, ট্রাম কিন্তু থামে না। কারণ ট্রামের ব্রেক দিতে সময় লাগে। ট্রেনের ক্ষেত্রেও তাই। ইদানিং দেখি, ট্রামলাইনে এখন লোকে গাড়ি তুলে দেয় কারণ সে ভাবছে ট্রাম তো ধীরে আসবে…কিন্তু এটা করাটা উচিত না। তবে সেদিন শুটিং করতে গিয়ে দেখলাম, রাসবেহারী এভিনিউ থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত ট্রামটা যাচ্ছে। এটা দেখে সত্যি ভালোলাগল। এই ট্রামকে সেলিব্রেট করাই তো উচিত আমাদের…এ কথাটাই সেদিন জার্মান কনস্যুলেটের অন্যতম একজন বলছিলেন যে, সরকারের কাছে একটাই কথা বলার, সরকর যা নিজের জন্য রাখছেন, সাধারণের জন্য তা খুলে দেওয়া হোক। কারণ কিছু মানুষের রোজগারও তো জড়িয়ে। এটা আমারও কথা।
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : মৃণাল সেনের ছবির সূত্রেও আপনার সাথে জড়িয়ে আছে ট্রাম…
অঞ্জন দত্ত : হ্যাঁ, চালচিত্রের প্রথম দিনের শুটিংটাই হয়েছিল ট্রামে। এ ছাড়াও উনি বারবার ট্রামকে ব্যবহার করেছেন ছবিতে। তাই আমিও ওঁকে নিয়ে ছবি বানাতে গিয়ে অজস্র টাকা খরচা হলেও ট্রামই রাখলাম। অনেকে বলছিল, বাস করে দিতে ট্রামের বদলে। কিন্তু ছবিতে যেমন ছিল সেভাবেই পুরোনো ট্রাম রাখা হল। কারণ, কিছু জিনিস বদলানো যায় না। বদলালে মজা থাকে না। সে মতই আমার বাড়ির কাছের ট্রাম কর্তাদের সাথে কথা বললাম। ওঁরা খুবই সাহায্যও করল। এবং অন্যদের তুলনায় অল্প টাকাতেও করে দিল। শুটিংয়ের সময় আমাদের ট্রামটাকে বের করে এনে আবার গুমটিতে ঢোকাতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছিল। তবে ট্রামে চরিত্রদের ওঠাটা ধরার ইচ্ছে ছিল। ধরতে পারিনি, কারণ এ এলাকায় কোনও স্টপেজ নেই। তবে এ ছবিটা করতে গিয়েই টের পেলাম, আশির দশক এবং আজকের কলকাতার মধ্যে প্রবল ফারাক। তবু, চট করে ক্যামেরায় তা ধরা পড়ছে না। অর্থাৎ, কোথাও এখনও কোনায় কোনায় হয়ত কিছু ছোটখাটো জিনিস রয়ে গেছে একই ভাবে। বদলায়নি। তাই বদলটা চট করে চোখে পড়ছে না। মনে পড়ছে, ভিয়েতনামের একটি শহরের কথা যেখানে সমস্ত কিছুই একশো বছর পুরোনো। আমাদের শহরেরও বয়স হল। ট্রামের তো হবেই। তিনশতাধিক বছর পরেও তাই আমার গর্ব হয় এ শহরের জন্য। ট্রামকে তাই গানে-সিনেমায় বারবার সেলিব্রেট করা উচিত।
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : আপনার কাজে বারবার আপনি এ শহরের হলুদ ট্যাক্সির কথাও বলেছেন…
অঞ্জন দত্ত : হ্যাঁ, এম্বাস্যাডর গাড়ি উঠে যাওয়াটা সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি আসলে। হেভিওয়েট গাড়ি সেগুলো। আজ আমরা যে গাড়ি কিনছি, তা বড়জোর ১০ বছরের মধ্যে খারাপ হচ্ছে। আবার আমাকে গাড়ি কিনতে হচ্ছে। অর্থাৎ এই পুঁজি ব্যবস্থা সচেতন ভাবে বিক্রি বাড়াতে মানুষের প্যাটার্নটাকে গুলিয়ে দিচ্ছে। জ্যাগুয়ার কলকাতায় কেন প্রয়োজন? সে গাড়িটা কি কলকাতার জন্য তৈরি করা? এ গাড়িটা গ্যারেজ করবে কোথায়! এ শহরের রাস্তায় কি সেটা চলতে পারবে? এগুলো কি আমরা ভাবছি? না স্রেফ ভাবছি নিজের উন্নতি নিয়ে! কারণ, তাঁর মানসিকতাটা সেভাবে তৈরি হয়েছে আসলে, শুধু নিজের আরামের কথা ভেবে ভেবে! হিন্দুস্তান মোটরও তো বন্ধ হয়ে গেল! এমবাসাডরের মত গাড়ি কেন আমরা রাখতে পারলাম না? কেন?
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : শহর বদলাচ্ছে। আমাদের বয়স বাড়ছে। এই বদলকে আপনি বারবার আপনার কাজে ধরে রেছেন। ট্রামও তো আসলে একটা সময়ের প্রতিভূ…আপনার কাজও যেমন একটা নির্দিষ্ট সময়ের শহর বা কিছু চরিত্রের কথা বলে…যা আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় একই সাথে।
অঞ্জন দত্ত : আমি কিন্তু খুব ভেবে কিছু করিনি। কোনও কোনও গবেষক বলছেন, আমার গান নাকি গবেষণার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই যে ম্যাকলয়েড স্ট্রিট বা ডাক্তার লেন-এগুলো কিন্তু আমি ভেবে কিছু করিনি। ন্যাচারালি এসেছে। আমি যে শহরে বড় হয়েছি, সেটাকে ধরতে গিয়েই এসেছে এ নামগুলো। কারণ, নিউ ইয়র্ক সিটি ব্লুজ বললে আমার কাছে স্পষ্ট হয় যায় কি বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে বা মোগলাই পরোটা মানেই আমার কাছে অনাদি কেবিন! তাই এমন নয় যে নেপালি সম্প্রদায়কে নিয়ে গান লিখব বলে বা দাস কেবিনকে ধরে রাখা দরকার বলে সেগুলো গানে আসছে…এবং যেহেতু আমি ইতিহাসটা বহন করছি তাই এটা ঘটছে। সিনেমায় যেমন ‘নুন শো, ম্যাটিনি শো’ ইত্যাদি এগুলো আমার গানে রয়েছে। জোর করে এটা আসেনি। যে গান আমি শুনে বড়ো হয়েছি সেখানেও লন্ডনের বা আমেরিকার রাস্তা বা প্রতিবেশীরা ঢুকে পড়েছে। গ্রাম নিয়ে আমি যেমন গান লিখতে বা সিনেমা বানাতে পারব না৷ আমি যে পাড়ায় বড়ো হয়েছি কলকাতার, সেটা স্রেফ হিন্দু এলাকা না।
আমার পাড়ায় পার্সিরা আছেন, আর্মেনিয়ানরা আছেন, চিনেরা আছেন, এংলো আছেন, পাঞ্জাবি আছেন-কিছুতেই কলকাতা সেখানে এক ধরণের মানুষের না। বব দাসকে নিয়ে যেমন আমি একটা গান লিখেছিলাম জনাথান দে নাম দিয়ে, যিনি সিনেমার জন্য নাচ শেখান। গানটা শুনে সুচিত্রা সেনের ভালোলাগে, তিনি মুনমুন সেন মারফত আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি তো গানটা সচেতন ভাবে লিখিনি, স্বাভাবিক ভাবে চলে এসছে। যেমন কেউ কফি হাউস নিয়ে লিখেছে, আমি আধা -গোয়ান একজনকে নিয়ে লিখেছি। কারণ আমার কলকাতা সব সময়েই কসমোপলিটন ছিল। এখনও ক্যামেরা নিয়ে বেরলে সেই সেই জায়গাগুলো আমি খুঁজে বের করবই। সারাক্ষণ মুখার্জি-ব্যানার্জিদের নিয়ে পারব না আমি, ওড়িয়া-বিহারীদেরকেও আমি বের করব। যেমন একজন নিউ ইয়র্কের লেখক বা সংরাইটারের লেখায় বারেবারেই গ্যাংস্টার, সমকামী, পাকিস্তানী, চিনে লোক ঢুকবেই, শুধু থমসন আর উইলিয়ামসনরা আসবে না। মুম্বইতেও যেমন কোলাবা সাইডে তাও কিছুটা পার্সিরা আছে এখনও কিন্তু অন্যদিকে ওশিওয়াড়ার পর সবটাই মারাঠি এলাকা। আর, কলকাতার এই কসমোপলিটন চরিত্রটা ছিল বলেই কিন্তু ব্রিটিশরা এখানে রাজধানী করেছিল। কারণ বর্ডারের পাশে বসে কিন্তু দেশভাগ এতটা সোজা ছিল না। কফি হাউস কিন্তু আজও রয়েছে, দুনিয়ার সেরা কফি না তৈরি হলেও, একটা কলেজ পাড়ায় এই কফি হাউস, সেখানেই বই কিনতে আমাকে যেতে হবে…এই যে পাড়া অনুযায়ী আলাদা আলাদা জিনিস, কোথাও বই কোথাও মাংসের দোকান কোথাও সিনেমা দেখতে যাওয়া বা কোথাও বেশ্যাপল্লি..এটা খুব জরুরি আমার কাছে। পাড়ায় পাড়ায় তো চিড়িয়াখানা বা মিউজিয়াম হতে পারে না! এই বৈচিত্রটা নষ্ট হয়ে গেলে খারাপ লাগবে। প্রত্যেকটা পাড়া এক রকম তো হতে পারে না। গড়িয়াহাট বাজার বা এন্টালি বা জগুবাবুর বাজার আমার কাছে তো আলাদা আলাদা দরকারেই যেতে হবে।
এই যে এখন সিঙ্গেল স্ক্রিন তুলে দেওয়া হল, কেউ ভাবল না, সিনেমা দেখাটা যে একটা আউটিং…মধ্যবিত্তর থেকে এই তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কাট অফ হয়ে গেল হলগুলো। তারা উজ্জ্বলাতে সিনেমা দেখতে গিয়ে পাশের দোকানের চানাচুর খেত, এখন মাল্টিপ্লেক্সে আর যেতে পারছে না তারা। দুনিয়ার অন্য শহরে কিন্তু মাল্টিপ্লেক্স অনেক ভেবে এসেছে। তাই গ্যারিক থিয়েটার আজও রয়েছে মাল্টিপ্লেক্স এলেও। আমরা দামী গাড়ি কিনলেই যেখানে সেখানে গাড়ি রেখে দিচ্ছি, বিদেশে বেশ কিছু জায়গায় এটা করা যায় না।
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় : সত্যি শহর অনেক বদলেছে, আপনার প্রিয় রেস্তোরাঁ ফ্লুরিস তো এখন পাড়ায় পাড়ায়…
অঞ্জন দত্ত : হ্যাঁ, কারণ তারাও এই বদলে ইউরোপিয়ান ব্যবস্থা থেকে আমেরিকান ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে। আমার কিন্তু স্রেফ প্রিয় ওদের পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁর জানলাটা…থিয়েটার বা সিনেমা বা ট্রাম-যাই বলো এগুলোকে বাঁচাতে তো আমাদেরও কিছু এফোর্ট নিতে হবে! সবকিছুই কি বাড়িতে বসে পেয়ে যাব নাকি! কোথাও অন্যায়ের প্রতিবাদে সমস্ত থিয়েটারের লোকেরা এসে দাঁড়িয়ে যায় অথচ হাতিবাগান থেকে যখন থিয়েটার হলগুলো একে একে উঠে যায়, কেউ তারা প্রতিবাদ করে না! কেন করে না? ‘বিশ্বরূপা, রঙ্গনা তোলা যাবে না’ কি আমরা বললাম! না। ‘বো ব্যারাক ফরেভার’ করার সময় আমি তো জানতাম না এত জনপ্রিয় হবে জায়গাটা…মনে হয়েছিল এই স্পেসটাকে আমি সিনেমায় ধরে রাখি। একটা সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকায় আস্ত ক্রিশ্চান পাড়া, ক্রিসমাসে নাচছে টাচছে, চেয়েছিলাম সেটাকে ধরে রাখতে। সেভাবেই আজ আরও মনে হয়, ট্রামের এই দেড়শো বছরে প্রত্যেকটা স্কুলে যদি আমরা ছেলেমেয়েদের ট্রাম নিয়ে বলতাম! ওদের নিয়ে ট্রামে ঘুরতাম! কিন্তু তাদের শিক্ষকরা কি সেই দায়িত্ব নিচ্ছে? আমি বো-ব্যারাক নিয়ে ছবি করেছি কারণ সত্যজিৎবাবু মহানগর ছবিটি বানিয়েছিলেন। আজকের ছেলেমেয়েরা কি দেখছে? নতুন কিছু কি তারা সত্যিই পাচ্ছে ভালো? আমি শুধু পার্ক স্ট্রিট নিয়ে গান লিখিনি। আমার গানে হরিপদ কেরানি থেকে লোকাল ট্রেনের হকার- সবাই আছে। এইসব নতুন আইডিয়া সত্যিই কি ইন্ডাস্ট্রি চায়? না হয়তো। কেন চায় না? কারণ অবাঙালিয়ানার একটা উদযাপন অলিখিভাবে চায় ইন্ডাস্ট্রি। সে জন্যেই আজ বাঙালি বলতে ব্যোমকেশের এই হাল! অথচ বাঙালির নামে আস্ত একটা সমুদ্র আছে, অন্য কাদের নামে আছে? এত সংখ্যায় নোবেল লরেট হোক বা সাম্রাজ্য বিস্তারে পাল বংশ বা, আমাদের জাতির নামে একটা দেশ! একজন সুভাষ চন্দ্র নামের বাঙালি আস্ত একটা সৈন্যবাহিনী তৈরি করেছে! কিংবা প্রেসিডেন্সির দু’জন বাঙালি ছাত্রই প্রথম আইন্সটাইনের তত্ত্বকে মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করেছেন…. একজন গীতিকারের লেখা সাহিত্যপদবাচ্য করে সম্মান জানিয়ে নোবেল দিতে বাধ্য হয়েছে ওরা, আজও দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক সম্মান জানিয়েছে সাংস্কৃতিক ফেস্টিভ্যাল হিসেবে, সারা দুনিয়ায় এত বৈচিত্র আর কোন জাতির আছে! ট্রাম তো সে আস্ত জাতিটার একটা চলমান ইতিহাসমালা! তাই এই দেড়শো বছরে তাকে তো আমি সম্মান জানাবোই।
(সাক্ষাৎকারটির পূর্ব প্রকাশক পুরশ্রী পত্রিকা। লেখকের সম্মতিক্রমে রোয়াক ওয়েবজিনে পুনঃপ্রকাশিত)