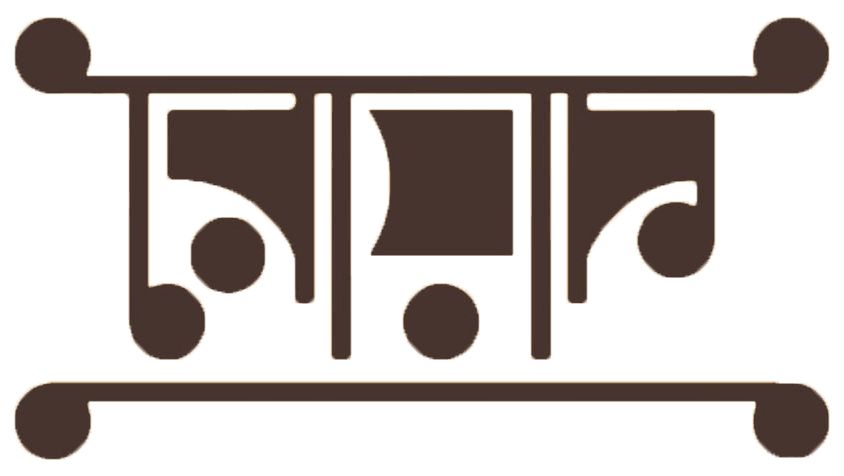তৃতীয় বর্ষ ✦ প্রথম সংখ্যা ✦ গদ্য
এই তো সময়
সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবনে একটা কাজই আমি পারি। হাঁটতে। রাস্তা হাঁটতে। কত চেনা যে অচেনা হয়ে উঠল, কত অচেনাকে যে চিনতে পারলাম এই হাঁটতে হাঁটতে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু নিজের ছোট্ট দরজা খুলে বিরাট পৃথিবীর দিকে হেঁটে যাওয়া কি সহজ খুব! ওই মহামহিম প্রকৃতি আর মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া কি সহজ! গলিঘুঁজি থেকে বড়ো রাস্তা, শহর থেকে মফস্বল, পাহাড় থেকে সমুদ্র যে অসংখ্য রাস্তা ছড়ানো রয়েছে, তাদের কথা ভাবলে আমার রোমাঞ্চ জাগে।
এরকমই এক বৈশাখের জ্বলন্ত দিনে হাঁটতে হাঁটতে, রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা দুটো যখন গলতে শুরু করেছে, আচমকা মনে পড়ে গেল পৃথিবীবিখ্যাত এক চিত্রপরিচালকের কথা- ‘It is the time for a new direction’। তারাকভ্স্কি এই জন্যই আমার প্রিয় শিল্পী। শোনা যায়, এটাই ছিল মৃত্যুর আগে তাঁর বলা শেষ কথা। মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তেও কেউ এভাবে কথা বলতে পারে? এই তো সময়! কীসের সময়?নতুন কোনও দিক নির্দেশের?নতুন কোনও নির্মাণের?নতুন কোনও গান লেখবার?যখন তোমার জঠর থেকে উঠছে ধোঁয়া?পোড়া গন্ধ আর নিমতেঁতো ছালগুলো ঝুলে আছে স্বপ্নে তোমার?এই তো সময়- আমরা কি জবাব চাইব তার কাছে?কেনো আমাদের পৃথিবীটা বারে বারে রক্তস্নান করছে? অন্তত এই যুদ্ধোন্মাদনাকে অনায়াসে মেনে নেবনা, কারণ মেনে নিলে আমাদের আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার হয়। এই তো সময়- প্রশ্ন তোলবার। পৃথিবীকে যারা লুঠ করে গুটিকয় প্রাসাদ বানিয়েছে, বিদ্বেষ আর ঘৃণা দিয়ে যারা রচনা করতে চাইছে নতুন শতাব্দীর বর্ণমালা, বরং তাদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার সময়। আমাদের সম্পৃতির ঐতিহ্যকে আমরা ভুলে যাব কেনো? এই তো সেই সময়, যখন মনে করব, অনেক রক্তক্ষরণ আর ক্ষয়ক্ষতির পরেও জীবন আসলে সুন্দর।
যেমন সুন্দর আমাদের কবিতার দিকে চলে যাওয়ার রাস্তাও। কোন কবিতা?কোন কবিতা তবে সার্থক আমাদের রোদ-বৃষ্টি-আলো-আঁধারের অনন্ত জীবনে? দেবারতিদির সঙ্গে আমার দেখা হয় নি বহুদিন। অথচ এই বিচলিত মূহুর্তে ওঁর কবিতার ঘরটিকে মনে পড়ল। চারদিকে সংঘাত, সংঘর্ষ বেশিরভাগ সময়েই ওঁর কবিতায় সরাসরি আসতো না। যে নিজেকে মনে করত কোনও আলাদা ব্যক্তি হিসেবে নয়, এই বয়ে যাওয়া সময়স্রোতের একটা অংশ হিসেবে। চারপাশের অন্যায়ের কোনও সমাধান খুঁজে না পেয়ে যার অস্বস্তি হত। এঁরাই তো ভাবতে পারেন- ‘কবি যদি তাঁর ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে অনেকখানিই ভুলে থাকেন, তবে কি তিনি সার্থক কবিতা লিখতে পারেন?’ পাঠকের মন কি সত্যি আর দোলাচলে থাকে এরপর? বোধহয় কোনও কোনও সময় আমাদের সংশয়ের মধ্যেই থাকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সত্যের উন্মোচন।
এই তো সময়- আমাদের সার্থক কবিতাদের খুঁজে নেওয়ার। না-হলে আত্মবিনাশের পথ পরিষ্কার হবে। যে যেখানে আছে, প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে কোনো না কোনো আয়ুধ। কোথাও তা সক্রিয় সচেতনতা, রাস্তায় রাস্তায় গড়ে তোলা ব্যারিকেড। কোথাও তা স্থিতপ্রজ্ঞ কলম। যে কলম প্রতিক্রিয়ায় ঝলসে ওঠে, বিক্ষত হতে হতে ছোট ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জমা করে মহাকালের মহাফেজখানায়।
দিনের রাস্তা আর রাতের রাস্তায় আকাশপাতাল তফাৎ। দিনের বেলা রাস্তা যেমন ক্ষুরধার, জ্বলন্ত, প্রকট; রাত্রিবেলা তারা ততটাই সর্পিল, অস্পষ্ট, জটিল। ঠিক যেমন আমাদের সম্পর্কগুলো। যেখানে বেঁধে বেঁধে থাকার কথা, সেখানে অনর্থক দূরত্ব। যেখানে থাকার কথা সহজাত মমত্ব, সেখানে খুনখারাপি লাল। সন্ধের পর রাস্তায় রাস্তায় চায়ের দোকানের আলো ভেসে ওঠে। চায়ের দোকান শতাব্দীর এক সৃজনশীল আখড়া। কারণ চায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রাচীনতম আড্ডার পরম্পরা। এক একটা চায়ের দোকান তাই রাস্তার সম্পদ। আমি ‘ধূলো খাই যদি প্রেম পাই’ বলতে বলতে রোজই চায়ের দোকানের আড্ডায় এসে বসি। ঠাট্টা ইয়ার্কির সঙ্গে এখানে উঠে আসে সময়ের নৈতিকতার হাল হকিকত। এ শতাব্দীর অসুখ লেগে আছে আমাদের ‘সম্পর্ক’ নামক সংবেদনশীল আত্মায়। কেন এত যোগাযোগের উপকরণ সত্ত্বেও আমরা একা হয়ে যাচ্ছি! শুধু একা হয়ে যাচ্ছি তাই নয়। একা হওয়াকে জাস্টিফাই করছি! এ এক নতুন দার্শনিকতা। প্রচারে আর বিজ্ঞাপনে কেবলই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রচার। সম্পর্কের যে দিকটা ঝঞ্ঝাটের, সেইটাই এইসব প্রচারের কাছে তুরুপের তাস। একা থাকলেই ভালো থাকা যায়, এবং তোমার জীবন আবর্তিত হোক শুধুই ‘একা তুমি’-কে নিয়ে। অবক্ষয়ী ধনতন্ত্র মানুষের ইতিহাসকেই গুলিয়ে দিতে চায়। আর অবক্ষয়ী বলেই বিচ্ছিন্নতার দর্শনকে এরা চ্যাম্পিয়ন করে। তো, চায়ের দোকানের আড্ডা এর উলটো পথে চলে। প্রতিদিন এসে জড়ো হওয়া আর কথায় কথায় গড়িয়ে চলে সন্ধেগুলো ভাঙা ভাঙা স্বপ্নদের জোড়া দিতে দিতে। এই-ই তো সময়- যখন চেনা দুঃখ চেনা সুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে অচেনা আতঙ্ক অচেনা ভয়। আর মহাকাল দেখে, কতগুলো মানুষ হাত নেড়ে পা নেড়ে কী একটা যৌথ-যাপনের ঘোর বুনে চলে!
রাস্তা তো ক্ষুরের ফলার মতো। ‘Live dangerously until the end’- এর মতো কথা কৈশোরেই শুনে ফেলেছি। বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে শেখা। শিখতেই হবে আমাদের। পুঁজিবাদের বুলডোজারের নীচে পিষে যেতে যেতে আমাদের পাওনাগুলো বুঝে নিতে হবে। এছাড়া আর কী-ই করার আছে মানুষের? যুগ যুগ ধরে পৃথিবী যুদ্ধ দেখেছে। রক্তক্ষয় দেখেছে। জমি নিয়ে, দেশ নিয়ে কামড়াকামড়ি দেখেছে। আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। সভ্যতার পরিহাসে আজও গাজায় প্রতিদিন গণহত্যা ঘটে চলেছে, শিশুহত্যা ঘটে চলেছে। ধর্ম নিয়ে, জমির অধিকার নিয়ে যুদ্ধ চলছে মাসের পর মাস। হাজার হাজার শিশুর মৃত্যুতে লাল হয়ে যাচ্ছে সময়। আকাশে উড়ছে বোমারু বিমান, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে একটা দেশ-জাতি-সংস্কৃতি। এই তো সময়- মনে করে সারা পৃথিবীতে এর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠছে মানুষ। অথচ কী আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের দেশ এখনও নিশ্চিন্তে সান্ধ্য আসর কিংবা ব্যক্তিগত মনোরঞ্জনে বুঁদ হয়ে আছে। এই-ই কি সময় নয়, ইতিহাসের দিকে, জীবনের দিকে, বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকানোর? আমাদের শহরের ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ মানে শাড়ি-গয়নার ডিস্কাউন্ট। অথচ প্রতি তিন মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। ক্ষমতাবান ধর্ষকের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে রাষ্ট্র।
এসে দাঁড়িয়েছি একটা মোড়ে। চারদিকে রাস্তা চলে গেছে। আমি, আমার মতো আরও অনেকে, হাঁটতে হাঁটতে আজ রাস্তার এই জটপাকানো প্রশ্নচিহ্নে দাঁড়িয়েছি। কোন্দিকে শান্তি, কোন্দিকে মানুষের সভ্যতার গতিমুখ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এই অন্ধকার বার বার এসে আহত করে দিয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভারতবর্ষ। এখানে স্বপ্নের সমাজ গড়ার পথে যেতে যেতে কতজন হারিয়ে গেছে। কতজন ফিরে আসতে চেয়েও আর ফিরতে পারেনি। ছিন্ন সত্তা নিয়ে তারা উন্মাদ হয়ে গেছে। এখানে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেছে স্বপ্নহীনতা। অবক্ষয় বিভ্রান্ত করেছে। ব্যক্তিগত সুখ খোঁজার দিকে ঠেলে দিয়েছে আমাদের। বানিয়ে তোলা শ্রেণী, ধর্ম, জাতপাত, বর্ণের বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা। আর মানুষের ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে।
আবার এওতো সত্যি যে কত কবি লিখে চলেছে সময়ের বিরোধীতার কূটাভাস। প্রতিরোধের গান গাইছে। ব্রেখট যেমন বলেছেন, তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- এই অন্ধকার সময়ে কি গান হবে?হ্যাঁ হবে- অন্ধকারের গান, বলেছিলেন তিনি। অন্ধকারের গান মানে প্রতিস্রোতের গান। কালচেতনার কবিতা। আমাদের আর কী করার আছে বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে শেখা ছাড়া?নিজের নিজের হকের পাওনা বুঝে নেওয়ার রাস্তায় যাওয়া ছাড়া?মুক্তির আর কোন্ পথ খোলা আছে আমাদের সামনে?
এই তো সময়- যখন আমরা কোনও কিছুই আর ভুলে যাব না। ভুলে যাব না প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ। ভুলে যাব না জীবিকার অনিশ্চয়তা। ভুলে যাব না একা একা বাঁচার সংস্কৃতি এক মারণফাঁদ। ভুলে যাব না কবিরা প্রশ্ন করে বলে রাষ্ট্র থেকে তারা বিতাড়িত হয়। অথচ কবিরা তো সামান্য ক’টা কথা বলে গেছে বারবার- ‘অনায়াসে সম্মতি দিও না’… বলে গেছে ‘অস্থির হোয়োনা শুধু প্রস্তুত হও’… বলে গেছে-‘বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে শেখো’… বলে গেছে-‘এটাই সময়…’।
রাস্তার পর রাস্তা এই ভেবে ভেবে হেঁটে আসছে মানুষ। পারহীন সংশয় কুয়াশার মতো ঘিরে ধরেছে বারবার। এ কি রাত্রিশেষের ইঙ্গিত, না কি আরও কোনও ভয়াবহ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে নামবে? সংশয়ের দীর্ঘ রাস্তায় ছায়া ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। ঘুরতে ঘুরতে বেঁকে যাচ্ছি যে যার গন্তব্যে। ভার্জিনিয়া উলফ্ যেমন বলেন, মেয়েদের একটা নিজস্ব ঘর চাই- যেখানে বসে তারা লিখবে। এ এক স্বাধীনতার জন্য স্বপ্ন দেখা। ঘর কই? আমার ঘর কোথায়?যেখানে বসে নতুন একটা কবিতা লিখব? যদিও আমি বিশ্বাস করি আমি যখন লিখি না, তখনও আমি লিখি। তবু। এই তো সময়- যখন মনে হচ্ছে সত্যিই একটা নিজস্ব ঘর চাই মেয়েদের।
বঙ্কুবাবুর গল্প
বিবস্বান দত্ত
নয় নয় করে বঙ্কুবাবু কাঁকুরগাছি প্রাইমারি স্কুলে দশ বছর পড়িয়ে ফেললেন। বঙ্কু বাবু দেখেছেন বাচ্চাদের সিংহভাগ সমস্যাই আসলে বাচ্চাদের সমস্যা নয়। পরিবার সূত্রে পাওয়া। সামন্ততন্ত্র চলে গেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনও অধিকাংশ পরিবার তাঁদের যৌথ অবচেতনে সামন্ততন্ত্র বয়ে নিয়ে চলে।
পরিবারতন্ত্র আসলে এমন এক ক্ষমতাকাঠামো যা আমাদের সবার চোখের সামনে থাকে। অথচ আমরা তাকে দেখতে পাইনা। পাইনা কারণ এই ক্ষমতা কাঠামোর বাইরেটা সাজানো থাকে কিছু প্রাচীন আবেগ সর্বস্বতায়। যে আবেগের বেলুনের ভেতরে আসলে হাওয়া না জল তা আমরা খুঁজতেই যাই না কখনও। কারণ আমাদের শেখানো হয় পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা মহাপাপ।
বঙ্কু বাবু নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, ভালো সন্তানের ছাঁচে ঢালা বাচ্চা, যে নিজের জীবনে সাফল্যের অনেকগুলো সিঁড়িই ভেঙে ফেলেছে, প্রথাগত ভালোত্বের মাপকাঠি পুরোপুরি পূরণ করার পরেও সে যদি সেই পারিবারিক ক্ষমতা কাঠামোর দিকে প্রশ্ন তোলে , এক ঝটকায় সে হয়ে যায় রেবেল! অতি পাকা। অথচ বিপ্লবের জন্মের বীজ তো লুকিয়ে ছিল ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেই। কোথাও একটা ক্ষমতা কেন্দ্র তৈরি হলে সেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোকে শোনা হবে না। কারণ বাচ্চা যে বড়ো হয়ে যায়, সে যে হয়ে ওঠে স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট এক আত্মনির্ভর মানুষ, পরিবার তন্ত্র সে কথা মানতেই চায় না। বয়স যতই হোক, যতই সে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করুক, সে চিরকাল বাচ্চা হয়েই থাকে। তাকে একজন “বড়ো মানুষ” বলে ভাবার শিক্ষাটাই অধিকাংশ মানুষ পায় না।
কিন্তু এই পরিবারতন্ত্র বয়ে চলে যারা তারা অধিকাংশ সময়েই ভালো মানুষ। শিশুর ক্ষতি করার মানসিকতা তাদের নেই। তারা ভালোই করতে চায়। কিন্তু এই ভালো করার আজীবন চেষ্টায় তারা শিশুকে প্রায় কখনোই বড়ো হতে দেয় না। অনেকেই এই পারিবারিক অবদমন সামলে নেয়। কিন্তু শিক্ষক বঙ্কুবাবু দেখেন এমন কোনও কোনও মানুষ থাকে যে এই অবদমন মানিয়ে নিতে পারে নি। সে আজীবন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে। কারণ তার পরিবার কোনও দিন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয় নি। বলেনি, ঠিক হোক, ভুল হোক তোমার সিদ্ধান্ত তোমার। এর ভালো কিংবা মন্দ এর সবটুকু দায় তোমার একার!
ফলে তারা দায়িত্ব নিতে ভয় পেয়ে গেছে চিরকাল। নিজেকে সন্দেহ করেছে! এবং এক আশ্চর্য ভবিষ্যতে নিজেই গড়ে তুলেছে আরেক পরিবার তন্ত্র। আরেক শোষণ কল।
অথচ পরিবার তো ছিল এক আশ্চর্য মায়া। যেখানে মানুষ ফিরে আসত সমস্ত যুদ্ধের শেষে। তার ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগত। সে নিজের জীবনীটুকু সংগ্রহ করে নিত অনন্ত তৃষায়। এবং সে নিজেও পেত শুশ্রূষা হয়ে ওঠার বিশ্বাস। সে দেখত তাকেও নির্ভর করছে মানুষ।
আমরা যেদিন বুঝতে পরব নির্ভরশীলতা একটি পারস্পরিক প্রক্রিয়া সেইদিনই বোধ হয় পরিবারের শেষ থেকে তন্ত্র শব্দটা খসে যাবে। অন্য সমাজের কথা ততটা জানি না, তবে ভারতীয় পারিবারিক কাঠামোয় , যেখানে পিতৃতন্ত্র নিশ্বাস নেওয়ার মতোই সহজ আর স্বাভাবিক, যেখানে ‘বুড়ো খোকা’ শব্দবন্ধ ট্র্যাজেডি নয়, কমেডি, সেইখানে কি এতকিছু সম্ভব? বড়ো বেশিই চেয়ে ফেলছি আমরা।