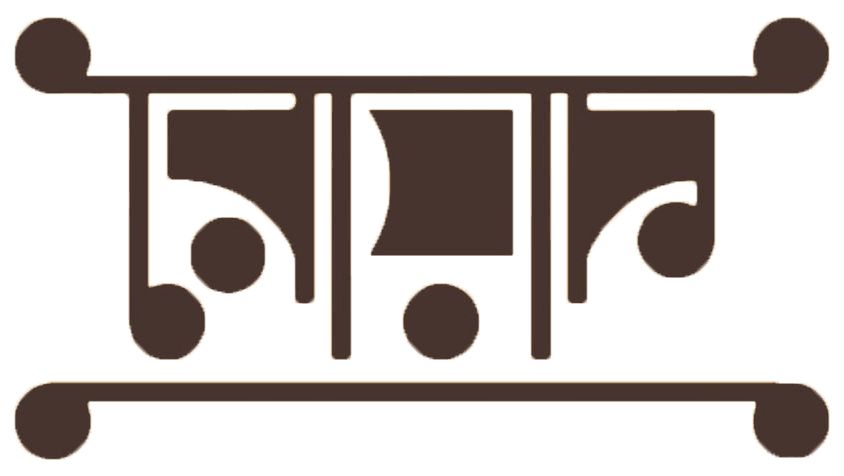তৃতীয় বর্ষ ✦ দ্বিতীয় সংখ্যা ✦ গদ্য/প্রবন্ধ
ফিচার ছবি : অনুস্কা সেনগুপ্ত
একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপকথা
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে সবার দিঠি এড়িয়ে এক তরুণী চলে গেলেন শ্মশানের দিকে, পানিহাটীতে। এরকম অসামান্য যাত্রা আমরা শেষ কবে দেখেছি? সে রাত্রে যখন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শব নিথর হয়ে পড়ে আছে শবাগারে, তখনই সেই তরুণী ৩৬ ঘন্টা হাড়ভাঙা খাটুনির পর গিয়েছিলেন বিশ্রাম নিতে। তারপরের চিত্রনাট্য অতীব দক্ষতায় রচিত। উইলিয়ম শেক্সপিয়রের মত প্রতিভাধর না হলে এমন চিত্রনাট্য লেখা মুশকিল। আমার মনে পড়ছে হ্যামলেটের সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ ‘How now, Horatio! You tremble and look pale./Is not this something more than fantasy?’ আসলে ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত লোকেরা হয়ত ভেবেছিলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণে যে উদ্বেল জনতার শোকোচ্ছ্বাস দেখা যাবে, সেই জনতা খেয়ালই করবে না শহরের অন্য এক প্রান্তে আরেকটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ফলে চিত্রনাট্যে কিছুটা অসঙ্গতি থেকে গেলে ক্ষতি নেই, শুটিং ফ্লোরে সামলে নেওয়া যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতা সেরকমই বলে। তবে মহাকবিদেরও ভুল হয়। হ্যামলেট নাটকের দৃশ্যে যেমন মধ্যরাতে মোরগ ডেকে উঠেছিল। আর জি করেও তেমন কিছু কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল। সেই ভুলের ফাঁক দিয়েই জনতা কখনো কখনো উঁকি মারার সুযোগ পায়।
যেমন তারা উঁকি মেরেছিল ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই, বাস্তিল দুর্গের সামনে। সেটা অরাজনৈতিক ছিল কিনা আমি জানি না। টিপু সুলতান জ্যাকোবিন সংঘের সদস্যপদ চেয়েছিলেন। জ্যাকোবিন সংঘ অরাজনৈতিক ছিল কিনা তাও বলতে পারব না। রুশ বিপ্লব অরাজনৈতিক ছিল কিনা বলতে পারব না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এমনকি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বদানকালেও, অরাজনৈতিক ছিল কিনা বলতে পারব না। কিন্তু আমাদের আজকের কলকাতায় বুদ্ধিজীবী বলেন, যে মিছিল অরাজনৈতিক না হলে তিনি যেতে পারবেন না। আর আমার আবার মনে পড়ে শার্ল বোদলেয়ার আর সেই তুচ্ছ বেশ্যার গল্প। কবি তখন স্তব্ধপ্রায় ল্যুভর চিত্রশালার সামনে। সেই রূপোপজীবিনী তাঁকে শুধোয় ‘ছি ছি! এই উলঙ্গ ছবিগুলো দেখাতে ওদের লজ্জা করে না!’
সত্যিই তো। লজ্জা করা উচিত। একজন ধর্ষিত নারীর ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখাতে লজ্জা করা উচিত। আমাদের অবশ্য লজ্জা করে না। কারণ আমরা জানি, আমরা সকলেই প্লেটোনিক প্রেমের পরিণামে জন্মেছি এবং লিখছি, নাটক করছি, ছবি করছি অথবা গান গাইছি। আমাদের সকলেরই যিশুখ্রিস্টের মত ‘immaculate conception’। তার মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই। কোনো যৌন মিলনও নেই। ‘আমরা সব নিরালম্ব, বায়ুভূত’ – সুবর্ণরেখা ছবিতে হরপ্রসাদ বলেছিল। আমার কলকাতায় থাকতে কষ্ট হয়, কেননা আমি দেখি আমাদের অকুস্থল কত সংবেদনহীন হয়ে গেছে। আমরা ধারাবাহিক spectacle-এর মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমরা সাজুগুজু করে মিছিলে আছি না ঘামে ভিজে মিছিলে আছি সেটা বড় কথা নয়। আমাদের ছবি উঠছে, আমরা পদযাত্রায় আছি, আমরা প্রতিবাদ করছি। আমরা জানি যে এই প্রতিবাদের আগে এবং পরে আমাদের খাদ্য, পানীয়, গ্লুকোজ লেভেল – সবই ঠিক থাকবে। পৃথিবীর কোথাও একটি পাতাও বিনা কারণে চ্যুত হবে না। শুধু আমাদের একটি মেয়ে মরে গেল। মরে গেল তো গেল। ‘জন্মিলে মরিতে হবে,/অমর কে কোথা কবে’ – মহাকবি মধুসূদন তো বলেই গেছেন। সুতরাং কী কাজ মিছিলে? কী কাজ প্রতিবাদ করে?
গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ থাকলে বলতেন এটি একটি পূর্বনির্ধারিত হত্যার ধারাবিবরণী। আমরা বলতে পারব না। কারণ আমরা আমাদের ছোট্ট রাজ্যের ছোট্ট ছোট্ট পুরস্কার, অনুদান – এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকব এবং ক্রমশই আমাদের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। বিকেল শেষ হয়ে এল, এবার সন্ধ্যা। ‘যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,/সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া’, তবু আমরা বিচিত্রানুষ্ঠানে মিলিত হব। সমস্ত কলকাতা শহরই আজ একটা বিচিত্রানুষ্ঠান। ‘ঈশ্বর, আমারে একবার কইলকাতায় নিয়া যাবা?’ আমি জানি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জিপিএস দেখে বলতে পারব কিনা কলকাতা কোথায়। কলকাতা তো একসময় বীণা দাসের, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের, কল্পনা দত্তের ছিল। আজ আমাদের, কাজেই জিপিএসও হয়ত ভুল করবে। তবে আজকের সমাজে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কোনোটাই শকিং নয়, সবই বাস্তবানুগ। এই বাস্তববাদের আতঙ্ক থেকে আমরা কবে মুক্তি পাব?
আরো পড়ুন কর্মস্থলে যৌন হেনস্থার জন্য ভারতে কমছে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা।
খুব সহজে জনপ্রিয় লব্জে বলতে পারতাম ‘মাস্টারমশাই, আপনি কিছুই দেখেননি।’ কিন্তু সমস্যা হল, মাস্টারমশাই সবকিছুই দেখেছেন। অয়দিপাউসের একটা সুবিধা ছিল – সে জেনেশুনে মাতৃগমন করেনি। আমরা সকলেই সজ্ঞানে, সচেতনভাবে এবং সুচতুরভাবে মাতৃধর্ষণ সম্পন্ন করেছি। আমাদের হাতে অয়দিপাউস এষণার ফাঁকিটুকুও আর রইল না। ধন্যবাদ, কলকাতা। বের্টোল্ট ব্রেশটের আরটুরো উই এবার নাটকের পাতা থেকে উঠে এসে শারদোৎসবের প্রধান অতিথি হোন। আমরা সকলেই করজোড়ে বলব ‘মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর’ মহোজ্জ্বল আজ হে।’
(লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে পুনর্মুদ্রিত)
বাংলার সাম্প্রতিক আর জি কর গণঅভ্যুত্থানকে আমি যেভাবে দেখছি
দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়
১/
গতকাল রাতে একটা ইতিহাস তৈরি হল। তৈরি করলাম আমরা, বাংলার মানুষরা।
নবারুণ অনেকদিন আগেই লিখেছিলেন, পেট্রল দিয়ে আগুন নেভাতে চাইলে তার ফল উলটো হয়। গতকাল রাতেও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার মানুষের প্রতিবাদের এই বিরল চিত্র সে কথাকেই ফিরিয়ে দিল। অবশ্যই, নকশাল আন্দোলনা বা নন্দীগ্রামের সত্তর হাজারের মিছিল আমাদের স্মৃতিতে আছে। কিন্তু গতকালের রেকর্ড কেন-যেন-মনে হল, সবকিছুকে টেক্কা দিতে পারে…পরিচিত এত মানুষ, এত আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, শিল্পীকে শেষ কবে কোনও মিছিলে দেখেছি, মনে পড়ছে না…
মানুষের স্রোত জমতে জমতে কখন কাল এইট বি মোড়টা মহাসমুদ্র হয়ে গেল খেয়াল করিনি! চারদিকে শুধু মানুষ মানুষ আর মানুষ…কেউ রাস্তার ধারে বসে তো কেউ হেঁটে চলেছেন ঝড়জলে…কোথাও ঘিরে জমায়েত তো কোথাও পরিবারের লোকেরা জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে…
গতকালের এই স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েত হয়ত আরও অর্গানাইজড হতে পারত। হয়নি। ছড়িয়ে গেছে। টিয়ার গ্যাস চলেছে নানা জায়গায়। থানা ঘেরাও হয়েছে। তবু এই ছড়ানোকে আটকানো যায়নি। আটকানো যায় না।
এবং এই প্রতিবাদ স্রেফ একটা ঘটনাকে ঘিরে ঘটেনি। এর পেছনে রয়েছে, নন্দীগ্রাম পরবর্তী গত দশ বারো বছরের সরকারের থেকে বাংলার মানুষের প্রত্যাশা এবং তা পূরণ না হওয়াত বিশ্বাসঘাতকতার রাগ। যে রাগ এখনও পর্যন্ত হয়ত প্রতিবাদে থেমে থাকলেও এরপর জনযুদ্ধে পরিণত হতে দেরি করবে না…যে রাগের জন্য কোনও বুদ্ধিজীবীর দরকার নেই। মানুষ নিজেই নিজের হিরো এবারে…
সকলে মিলে কাল সারারাত আমরা জেগেছি। সকলে মিলেই একটা ইতিহাসও গড়ে তুলেছি। একবাক্যে আজ সে ইতিহাসের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে লেখা হবে, বাংলা এ হেন প্রতিবাদের চিত্র আগে দেখেনি। তারপরেও হয়ত রাতারাতি সরকার বদল হবে না। কিন্তু চাপ তৈরি হবে। হবেই। যে চাপ আর বাংলার মানুষ তৈরি করতে পারবে না ভেবেছিল। আমরা অজান্তেই হেরে গেছিলাম। আবার অজান্তেই কাল জিতে গেলাম….জেগে উঠলাম…এটাই বাংলা!
গতকাল রাতের পর অদ্ভুত এক স্তব্ধতা গ্রাস করেছে। ঠিক কি অভিজ্ঞতা দিয়ে গেলাম, এখনও ভেবে যাচ্ছি। সময় লাগবে বুঝতে। তবে আমরা যারা বিদ্রোহ বা বিপ্লব আর এ জীবনে কখনও দেখতে পারব না ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম দুর্গাপুজোয় রাত জাগাই সর্বোচ্চ বিপ্লব, তারা আচমকা একটা আস্ত টর্নেডোর সামনে যে পড়ে গেছি সন্দেহ নেই….এবারে সেটা কোনদিকে আমাদের নিয়ে যাবে, সেটা সময় বলবে।
সংহতি অবসাদ মুছে দেয়। মানুষের সংহতি। কাল ফিরতে ফিরতে আমারই পরিবারের দুই নবীনাকে বলছিলাম কথাটা। তাঁরা সদ্য কলেজ পাশ করেছেন। এ হেন গণবিদ্রোহ দেখে তাঁরাও থতমত। তাঁরা সত্যি বিশ্বাস করল তারপর, অনেক মানুষ একজোট হলে যে কোনও রোগ সেরে যেতে পারে। কারণ তখন আর মানুষের ভয় করে না…কারণ, একজোট হওয়াই আসলে উৎসব। মানুষের উৎসব…
গতকালের ভোর থেকেই যেমন শুরু হল, আসল মহালয়া…

২/
বলতে দ্বিধা নেই, যে সব “শিল্পী’রা এখন রাস্তায় নামছেন, এদের অনেকের পেছনেই সরকার বা বড় প্রযোজনা সংস্থার বড় হাত আছে। এদের অনেকেই সরকারের বিরুদ্ধে একটা কথা বলেননি সারা জীবন বরং গুছিয়ে খেয়েছেন এতদিন। এখন কাঁদছেন, কুমিরের কান্না। এদের এখন মানুষ চিনে গেছে। তাই এইসব হাস্যকর মিছিলগুলোকে মানুষ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। কারণ, তারা জেনে গেছে, এসবই ভণ্ডামি। এ জিনিস দশ বছর আগেও ছিল না। মানুষ একজোট হয়ে যে প্রতিবাদটা জানাতেন, তা জেনুইন ছিল। এখন প্রতিবাদেও দেখছি কি নিপুণ মিথ্যে ঢুকে পড়েছে। শাবাশ, শিল্পীকুল, আপনারা চালিয়ে যান। এইসব হাততালি, ড্রেসকোড, স্লোগানে এক বর্ণ সত্যি নেই। ন্যাকামি আর মিথ্যে আছে। ফেসবুক জমানায় আপনাদের রোজকার ডিটেল মানুষ রেকর্ডে রেখেছে। মিছিল থেকে আপনি যখন স্ত্রীকে নিয়ে আর্বানার বিলাসবহুল আবাসনে ফিরতে ফিরতে বলবেন, ‘যাক বাবা, এ বার যে সরকারই আসুক, আর চাপ নেই…’ সেটাও জেনে গেছে মানুষ। তারা আপনাদের এসব সার্কাস দেখে হাসছে। কারণ এরপর যখন জনযুদ্ধ লাগবে, আপনারাও ছাড় পাবেন না।

৩/
মিছিলগুলো সব একত্রে হচ্ছে না কেন? এইভাবে বিচ্ছিন্ন মিছিল কিছু কিছু ফেস্টিভিটি বা কার্নিভ্যাল হয়ে উঠছে না? অথচ একইসঙ্গে বহুমানুষ আবার একত্রে মিছিলের ডাকও দিচ্ছেন…
কথাগুলো অনেকেই বলছেন, লিখছেন। এরই মধ্যে সেদিন একটি ভিডিওতে দেখলাম, ভিড় বাসের জনতা রীতিমত ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিচ্ছে একজনকে কারণ সে বারবার বলছিল, এইসব মিছিল করে রাস্তা অবরোধ করে কি হবে! বোঝাই যাচ্ছে যে শাসকদলের ঘনিষ্ট…
আমাদের পাড়ায় একটি মিছিলের ডাক দিয়েছেন কিছু মুক্ত চিন্তার মানুষ। সামনের হপ্তায় সে মিছিল হবে। কেউ আসতে চাইলে আসতে পারেন।

৪/
রাত দখল চলছে। কিন্তু তা বলে ধর্ষণও থেমে নেই। সমানতালেই জারি আছে। আজ হরিপাল তো কাল প্রেমের প্রত্যাখ্যানে কুপিয়ে খুন। রাত দখল চলছে। ধর্ষণও চলছে সমানতালে।
যেমন চলছে আজ গণেশ পুজো। রাস্তায় বেরিয়ে ভিড়ের চোটে এগোতে পারছিলাম না। অথচ ক দিন আগেই মা-হাতিকে বাচ্চ-সহ আক্রমণ করলাম আমরা!
সমাজ পচে গেছে। মনে হয়না, রাতারাতি কিছু বদলাবে। কামদুনির মত আর জি করের ঘটনাতেও দোষিদের ক মাস পর আদালত ছাড় দিয়ে দিলেও অবাক হব না।
শুধু একটাই আশা, এবারের প্রতিবাদ করছেন মূলত অল্প বয়সীরা। তারা ফেসবুকে পোস্টার পোস্ট করে এলাকায় লোক জড়ো করছেন। কবে কে নকশাল আন্দোলনে বোমা ছুঁড়েছিলেন বা অগ্নিযুগের বিপ্লবী দাদা কি বলছেন, তারা জানতে চান না।
তারা শুধু জানেন আগামী মাসগুলোতে এই রাত দখলকে আরও জোরদার করতে হবে। হ্যাঁ পুজো বা ক্রিসমাসে হয়তো ভিড় অল্প হলেও ফাটবে। তবু বিদ্রোহ থামবেনা। আবার তারপর মানুষ রাস্তায় জড়ো হবে। তারপর অনন্তকাল ধরে প্রশাসনের মাথাদের ঘিরে চলবে রাত দখল। আমরণ অনশন।
একটা হেস্তনেস্ত এবার হবেই। একমাস বা এক বছর বা দশ বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু আর ছাড় নেই…এখানেই আগামীর যাবতীয় আশা
৫/
দুর্গাপুজো @ তিলোত্তমা
সরস্বতী: মা, এবারে কি যাওয়া ঠিক হবে?
লক্ষ্মী: হ্যাঁ, মা, আমারও মনে হয়, এবারে যাওয়াটা ঠিক হবেনা…
দুর্গা: তোদের বাবা কি বলছেন? উনি তো অবশ্য সারাক্ষণই ট্রিপ করছেন…
শিব: (গাঁজা খতে খেতে থমকে উঠে)…এ আঘাতটা তো একেবারে আমার মেয়েদের ওপর, তোমার ওপরও…আমরা গেলে স্রেফ লুকিয়ে চুরিয়ে রাত দখলে যাব…উৎসব-ফুতসবে না…
গণেশ: ওরা তো আমার একটা বাচ্চাকেও মা-সহ মেরেছে…মা হাতিটাও কাঁদছে…
কার্তিক: কিন্তু এতকিছুর পরেও কেনাকাটা থেমে থাকছে না…ফুর্তিও পুরোদমে…পুজোর পর বিদেশ ট্রিপের টিকিটও কাটা সবার…কিছু কিছু মিছিল (অবশ্যই সব মিছিল না) দেখে তো মনে হচ্ছে রীতিমত মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, ডিনার করে গিটার হাতে চলে গেলেই হয়…
সরস্বতী: একটা রায় এখনও পর্যন্ত এলো না ঠিকঠাক..
দুর্গা: তিলোত্তমার মা কি বলেছেন রে?
লক্ষ্মী: বলেছেন, ওনার ঘরে তো দুর্গার আলো জ্বলবে না আর, কেউ যদি ইচ্ছে করে আনন্দ করতে পারে অবশ্য…
অসুর: ওই সন্দীপ ঘোষ ব্যাটাকে না ধরলে আমরা এবার যাবই না
মহিষাসুর: আমারও তাই মত।
দুর্গা: তাহলে কি আমরা চুপিচুপি এবারে গড়িয়াহাট বা শ্যামবাজারের রাত দখলে যেতে পারি? যদ্দিন না জাস্টিস আসছে? তদ্দিন?
শিব: সেটাই বেটার..
সবাই সমস্বরে: হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে ভালো…
শিব: তবে, তার আগে, সবাইমিলে একবার..
সবাই আবারও সমস্বরে: জাস্টিস ফর, আর জি কর…
হাম দেখেঙ্গে..
ডাঃ বিস্ময় মন্ডল
হিসেব মতো শ্রাবণ শেষ!তবু আজকাল আকাশ ভেঙে পড়ছে।তিলোত্তমার খানা খন্দ গুলো ঢেকে দিয়েছে মানুষের কার্পেট।চারদিকে ছিটকে পড়ছে জনসমুদ্রের সাহসচিহ্নের ঢেউফেনা! অজস্র মোমবাতি, আর মশালকুচির শেষ আলোটুকু জোনাকির মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে আপামর মানুষ । বৃষ্টির জলের মতন এদের কোনো রঙ নেই, আছে গণসঙ্গীতের সপ্তক, আছে প্রতিরোধের প্রবণতা আর আছে প্রতিকারের অদম্য ইচ্ছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়?
গল্পটা সবাই জানে। দু’হাজার চব্বিশ।নয়ই অগাস্ট। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ধর্ষণের রগরগে খবর ভাইরাসের থেকেও দ্রত সংক্রমিত হয়!
আমার প্রাক্তন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেছিলেন এটি নিছক দুর্ঘটনা। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে নিকট অতীতে এমন আত্মহত্যার ঘটনা বিরল নয়। অমন একটু আধটু পড়াশোনা জানা মেয়েছেলে দের সাথে হয় বাপু!তবে নিজেই নিজেকে ধর্ষণ করে খুন !এইখানেই গরমিল!
টনক নড়ে কলকাতা পুলিশের থুরি হাসপাতালের ছেলেপুলের!
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এমন “বিছিন্ন””ছোটো” ঘটনার FIR প্রয়োজনবোধ করবেননা সেটাই স্বাভাবিক।মেয়েটির কন্যাদায়গ্রস্ত অভাগা বাপ মা শেষ বেলায় FIR করেন। তড়িঘড়ি পঞ্চভূতে মিশে যায় তিলোত্তমা আর যাবতীয় প্রমান।পোস্ট মর্টেম ,এক্স রে বাদ থেকে থেকে যায়। বাদ থেকে যায় অনেক কিছুই। সেসব থাক।
কোলকাতা পুলিশ কাউন্টার এটাকে ঝটতি আক্রমণে নিজেদের মধ্যে ওয়ান টু খেলে এক গোলে এগিয়ে যায়। আর কিছুক্ষণ পর ডিফেন্সচেরা পাসে আবার গোল কোলকাতা পুলিশের । হেডফোন কানেক্ট করে কমিশনার সাহেব জানিয়ে দেন দোষী কে? ধনঞ্জয় এর মাসতুতো ভাই সঞ্জয় !
তবে সে কম নয়। হারকিউলিসের মতন যাবতীয় দায়ভার কাঁধে নিয়ে নেয় অবলীলায়। শোনা যায় কেরালার বন্যার দায়ভার নিতেও রাজি ছিলেন সঞ্জয়। তবে দুর্ভাগ্য এই যে হেডফোন কানেক্ট হলো বটে.. বোকার হদ্দ মানুষ গুলো এই গল্প টার সাথে কানেক্ট করতে পারলনা!
এরপর বল পাস হয় সিবিআইয়ের দিকে! হাতুড়ির আর ক্ষমতার বারবার ঠোক্করে চুরমার হয়ে যায় বক্ষবিভাগের সেমিনার রুম সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রুম। ব্যাস, দুষ্টু ঘর, দুষ্টু দেওয়াল ভ্যানিশ!
মিছিলের ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়ায় সেই খাঁকি আর সাদা উর্দির সরকারি কাঠপুতুল !
চরমতম কড়া ডিফেন্সের মুখে পরে সাধারণ মানুষ তথা জুনিয়র ডাক্তাররা। কড়া ট্যাকেলে রক্তারক্তি হয় কিছু। রেফারীর মুখ তখনও “বিনীত”ভাবে অন্য দিকে।
দর্শক আসনের আম জনতা ততদিনে বুঝে গেছে জলাতঙ্কের মতন প্রতিষেধক নেই এই ধর্ষণ-রোগের। কিন্তু শিরদাঁড়া সেতো মাতৃগর্ভে তৃতীয় চতুর্থ সপ্তাহে তৈরী হতে শুরু হয়। তার দায় নিতেই লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্যোৎস্না হয়ে ঝরে পরে শহরতলির রাজপথে। মোবাইল ওয়ালপেপারে স্বাধীনতার তারিখ আসতে না আসতেই হল্লারাজার সেনারা ব্যারিকেড কুচিয়ে ঢুকে পড়ে তিলোত্তমার হাসপাতালের ভেতর। খালি হাতে হাসপাতালে ঢুকে কোনো অদৃশ্য জাদুবলে পেয়ে যায় স্টিলের রড। গুঁড়িয়ে দেয় ইমার্জেন্সি, তার ওপরের ফ্লোর। নষ্ট হয় লক্ষাধিক টাকার ওষুধ। ফ্লোর গুনতে ভুল হয় তাদের। আসলে সব দোষ আগের সরকারের ! এত দেরিতে ইনজিরি সেখানোর ফল!
কলকাতা পুলিশ এইবার চুপ !নার্সদিদিদের টয়লেটে লুকিয়ে ১০৮ বার হনুমান চল্লিশা পড়ে বিপদ থেকে রেহাই পায়। রেফারি গোল দেয়। ওন গোল।
এসব দেখে ভিমরি খেয়ে যায় আম আদমি। আসলে এমন ম্যাজিকে অভ্যেস নেই তো মানুষের। একেমন ম্যাচ চলছে। কিছু বুঝতে না বুঝতেই রেফারির বাঁশি। ম্যাচ শেষ।
শুরু হয় জনবিস্ফোরণ। সত্যির জন্যে।সত্যি লোকানোর জন্যে।
প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের ৯৯% ভাগ হাসপাতালে ইমার্জেন্সি আর ওপিডি এর পরেও খোলা থাকে। রোগী দেখেন সিনিয়র ডাক্তাররা।আমরা জুনিয়র ডাক্তাররা আর সাধারণ মানুষ গাঁটছড়া বেঁধে নামি আন্দোলনে। কারণ তিলোত্তমা আমাদের কারোর বান্ধবী, কারোর বোন, কারোর দিদি। ১০ লাখের তোড়া ছুঁড়ে ফেলে মেরুদন্ড বিক্রি নেই বলে বিস্ফোরক হন ওঁর মা বাবা।
এমতাবস্থায় আরো দায়িত্বভার গড়ায় সিবিআইয়ের হাতে। শেষ চার বছরের সাদাকালো খেরোরখাতা নিয়ে মুখোমুখি বসেন ঘোষবাবু। বল ততক্ষণে সুপ্রিম কোর্টের হাতে। এই মন্দার বাজারে ডবল ডবল চাকরি পেয়ে ঘোষবাবু প্রমান করেন পচ্ছিমবঙ্গ মোটেও পিছিয়ে নেই!
যারা চাকরি নেই বলে দু গ্রাস ভাত বেশি খায় তারা সব ষড়যন্ত্রী আর নেহাত ছেলেমানুষ!
দশটা পাঁচটার এটেন্ডেন্স শুরু হয় সিজিও কমপ্লেক্সে।
একটা একটা করে মশাল নিভতে শুরু হয়! অনিশ্চয়তায়।
আমরা ধুঁকি কিন্তু অনড় থাকি ।কারণ,
আমরা স্পষ্টতই মনে করি শেষ তিনচার বছর ধরে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কিম্বা স্বনামধন্য উত্তরবঙ্গীয় লবির যে দুষ্ট চক্র তৈরী হয়েছে তার মদতেই এই ঘটনা। এই যে যা-ইচ্ছে-তাই করলেও পার পাওয়া যায় এই সাহসটা কে বা কারা জুগিয়েছে? এই তথ্য ভ্যানিশের দায় কার? আসল দোষী কে বা কারা? এত কিসের ভয় যেখানে বাঙালির আবেগ ডার্বিকেও নিরাপত্তার জন্য বন্ধ করে বিরাট পুলিশবাহিনী, র্যাফ নামিয়ে লাঠি চার্জ করতে হয়? পুরোটাই
ম্যাচ ফিক্সিং ?
এখনো অব্ধি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কমিশনার সাহেব কেউ-ই কোনো ঘটনার দায়ভার নেয়নি। সবেধন সঞ্জয় ছাড়া আর কোনো সন্দেহভাজনের জন্ম হয়নি। সবার সব ক্ষমতা বহাল, পরিবর্তন বলতে কিছু ইধার কা মাল উধার হয়েছে
মেয়েটার নাম কাটা গেছে ডিউটি রোস্টার থেকে।এক জোড়া বাপমার জীবনটা নরক হয়ে গেছে !
“বরি বরি শাহেরোমে ছোটি মোটি বাতে “
বলিউডি সিনেমায় বেশ লাগে
আমরা ঋত্বিক ঘটকের দ্যাশের লোক !
আমরা অযান্ত্রিক কিছু রক্তমাংসের মানুষ!
তাই যে স্বপ্ন রক্ত দিয়ে শেষ হয়েছে তার জন্যে
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব। কথা দিলাম।
বাঙালী পারে! এখনও পারে!
মধ্যরাত্রি , একদিন চিঠির দোনলা
মানস ব্যানার্জি
কী লিখব । কেমন করে লিখব । এইরকম একটি ঘটনা বারংবার ঘন্টা নাড়িয়ে বলে দিয়ে যায় , আমরা অসহায়। এমনিতেই সিস্টেম । যা আমাদের পরিচালনা করে। বলে এই এই ভাবে বেঁচে থাকতে হবে। নিয়মাবলী। কিন্তু সেখানেই দেখা যায় প্রচুর সংবিধান বহির্ভূত কাজ। আর সেটার কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। তুমি কি গরিব , সাধারণ হয়ে বেঁচে থাকবে ? যদি তা না চাও , চুপচাপ মেনে নাও। সফল হও। সফলতার মানদণ্ড যদি এই হয়। তাহলে আর সঠিক পথে হাঁটাহাটি করে ক্লান্ত হবেন কেন ? তার থেকে চলুন সবাইমিলে হইচই করি আনন্দ করি। এও এক মাস্ হিপনোটিজম। গণ – সম্মোহন। ভুলভাল যাকিছু সব একসাথে । ন্যায় অন্যায় বলে কিছু থাকবে না। হাসতে হাসতে আমি আপনি আমরা সবাই এই জগতে যা করা যায় না। যা করা উচিত না। গণতন্ত্র সমাজ তাদের নিজস্ব কিছু নিয়মাবলী আছে। সেইসব ভেঙে দেব। বর্তমান সময়ে এই কঠিন বৃত্তের মধ্যে আমরা অসহায় ঠকঠক করে কাঁপছি। এই মেয়েটির ক্ষমতা আছে। সে জীবনের পরোয়া না করেও লড়াই করেছে। এবং ভয়ানক মৃত্যু বরণ করেছে। যথারীতি রাষ্ট্রশক্তি অপরাধ প্রবণতা থেখিয়ে ফেলেছে। আইনের বাইরে গিয়ে আইন মানানোর চেষ্টা করে চলেছে।
পুলিশ …
শব্দটি একজন নয়
বহুবচন
আমাদের বাবা মা ভাইবোন জাতীয় নেতৃত্বস্থানীয়
আইন । আপেক্ষিক হয়ে যাচ্ছে ইদানিং খুব বেশি।
এই দেশ , এই বেঁচে থাকা , অধিকার নেই আমাদের ?
তবে কেন এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ? যদি তা সুরক্ষাই না দিতে পারে আমাদের ?
সবাই খুব হোমড়াচোমড়া হতে পারে না সমাজের। খুব সাধারণ দীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মানুষজন দিন শেষে ফিরে আসেন গৃহে। শান্তি চান। যাহোক। পাড়ার নানূটু শানটুদের রঙবাজি । চুপচাপ বয়ে যায়। নালা অলিতে গলিতে ধাববান ইতিহাস।
পুলিশ। নাগরিক সমাজ কেন তৈরি করেছিলেন এই উর্দির ? রক্ষার নিমিত্তে। কাদের রক্ষার ?
সংবিধান। চিন্তা করুন। চিন্তা করুন। আইন প্রণয়ন।
আমি ঠিক এটাই চাইছিলাম। গর্জন চাইছিলাম। চাএর দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে এসে দেখি , লোকে লোকারণ্য। মানুষটার জন্য ভিড় করেছে মানুষ। যে দেশে, যে রাজ্যে , রক্ষক ভক্ষকের কাজ করে সেখানে অভ্যুত্থান না হলে বেঁচে থাকা যায় না। লড়াই তো অনেক দূর নিশ্বাস নিতে গেলেও মনে হয় অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না। শ্যামবাজারের মোড়ে ততক্ষণে নানাভাবে প্রবল হৃৎস্পন্দন বেজে উঠেছে সকলের। গান , নাচ। এত কিছুর মধ্যেও মনে হচ্ছে খুব শীত করছে। প্রচন্ড আওয়াজ আসছে কোথা থেকে যেন। হাত খুলে ফেলেছেন আপনারা। এখন লড়াই সম্মুখ। আজ শুনলাম নৈহাটিতে সমস্যা হয়েছে। এসব তো হবেই। ব্যাটনটা অবশ্যই অল্প বয়সের হাতে থাকুক। বড়রা অভিজ্ঞতা দিন। উপদেশ দিন। চুলচেরা বিশ্লষণ দিন রাস্তার। বিচার ব্যবস্থা একদিন সুদিন নিশ্চয়ই দেখাবে। তবে সমাজ অনেকরকম দুর্নীতিতে ভরা। পেঁয়াজের খোসার মতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের। রাত প্রবল হচ্ছে। প্রচুর জনসমাগম। পাশাপাশি খাবারের দোকানগুলি আজ বোধহয় বন্ধ হবে না। একটা বিষয় নতুন দেখছি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষেরও তুমুল উপস্থিতি। আসলে ওরাও আর শাসকদলের চোখরাঙানি মানছে না। ওদেরকেই তো ব্ল্যাকমেল করা সহজ। কিন্তু জনগণের এই যে প্রবল জোয়ার সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন অনেক রাত। পরতে পরতে অন্ধকারে মানুষ মিশে যাচ্ছে একে অপরের অভ্যন্তরে। এ অভ্যন্তর যেন প্রাণের খেলা। পুব দিকে আর একটু পরেই সূর্য উঠবে। মানুষ মনে হয় এখনও ক্লান্ত নয়। দোকানদার তারাও বোধহয় নতুন করে সরঞ্জাম যোগাড় করছে। চওড়া হচ্ছে বিটি রোড। একদিকে ভুপেন বোস এভিনিউ। একদিকে বিধান সরণি। এত সকালে দেখছি কোথা থেকে পিলপিল করে মানুষ আসছে। আন্দোলন উদ্ভাসিত। আ’কাচা পোশাকের নীচেও আ’কাচা শরীর নিয়ে মানুষ। রোদ্দুর পোয়াচ্ছে। চেনা মানুষ যেন আরও চেনা আরও চেনা আরও আরও …
যেচে জ্ঞান দেওয়াটা আমার বদভ্যাস। মানে জ্ঞান তো নেই। তবুও কুড়িয়ে কাড়িয়ে এই অভ্যাস বজায় রাখার চেষ্টা করি। ঝাপাটাও খাই। আর এটা দেখছি , যত বয়স হচ্ছে , তত বাড়ছে। কোথাও একটা ধারণা তৈরী হচ্ছে যে অভিজ্ঞতা বুঝি একটা মার দিয়া কেল্লা গোছের কিছু। কিন্তু সত্যিই আমার অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু ? লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানুষের মতো বেঁচে থাকা টুকু নিয়ে রাত্রিবেলা রুটি চিবোই। শান্ত পৃথিবীর ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনি। হ্যাঁ। দু একটা বাংলা বই পড়েছি। তা সে এমন কি আর ! বাংলা বই এখন আর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলাভাষাও নয়। এক একবার মনে করি । ভাই দিন তো গুটিয়েই এনেছি। আর ক’টা দিন কোনওরকমে চলে গেলেই হল। না হলেও বা কী হবে ? কত বিখ্যাত মানুষ সমান্তরাল কষ্ট পেয়ে শেষ করেছে জীবন। আমি তো সাধারণ। অতি সাধারণ। তাহলে আমিও যদি ল্যালব্যাল করতে করতে চলে যাই। তো যাব ! কিন্তু অন্য আর একজনের কথা ভাবি। তখনই বিদ্রোহ থমকে যায়। শান্ত শিশুটি বাড়ি যায়। হাতে জলের বোতল ছুড়ে দিয়ে । সে যেন এখনও কিছুই জানে না এই পৃথিবীর। গোবেচারা পৃথিবী। তার নির্মল আকাশ। এখন আকাশেও খেলা হয় না পতঙ্গ হাভেলি। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে এই একমাস আকাশ জুড়ে ঝর্ণার মতো ঘুড়ি কেটে এসে পড়ত এখানে সেখানে চলন্ত রাস্তায় অফুরন্ত মানুষের মধ্যিখানে। স্বপ্নের মধ্যে এখনও যেন দেখি বৃষ্টি খেলছি। এক আকাশ বৃষ্টি। তোমার বাড়ির ছাদ। আমার বাড়ির। কেউ কোথ্থাও নেই দুপুরবেলা। ঠাকুমা পাঠ করছেন পাঁচালি। গহন অরণ্যের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছি। মাটিগুলো দেখছি কালো। আর কালো যেন এদিকটা কোনওদিন আসেনি কেউ। আমি এসেছি । হাঁটতে হাঁটতে চলেছি এক গহন অন্ধকারে। কিছুটা দূর যাওয়ার পর দেখলাম একটা বিরাট চাতাল। সেই চাতাল পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশপথ। কিছুটা ভেতরেই একটা চলমান যন্ত্র ওপরে উঠে যাওয়ার। আসেপাশেই কোথাও সিঁড়ি আছে বোধহয়। আমি কিন্তু যন্ত্রের ভেতরেই প্রবেশ করলাম। আর তক্ষুনি দেখলাম শুরু হয়ে গেল যন্ত্রের ওপরে উঠে যাওয়ার। কোনও ভয় লাগছে না আমার। এ যেন কোনও বিষয় নয়। আমি যেন পরিচিত এই যন্ত্রের। পূর্বেও এসেছি কী তবে আমি ? যাইহোক যখন থামল এই যন্ত্র। তখন দেখি দুইশত তল। স্বয়ংক্রিয় নিজস্ব জানানপ্রক্রিয়া। বেরিয়ে এলাম। তারপর কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে সোজা খোলা আকাশ। বিকেলের নিভু নিভু আলো। আর এ যেন এক বিশাল ময়দান । কেউ নেই । সীমা নেই । আগলদার নেই। চলাচল নেই। শুধু থেমে থাকাটুকু উত্তেজনায় ছটফট করছে আমার মন। ভাবছি , আমিও কি সঠিক আমার অস্তিত্ব ? কিন্তু চিমটি কেটে বুঝলাম আমি ঠিক আছি। ঠিক আছে অস্তিত্ব। হাঁটতে শুরু করলাম। কংক্রিটের সিমেন্ট। এই উপরিতলার ময়দান যাকে ছাদ বলা হয় সভ্য সমাজে। হাঁটছি হাঁটছি। কখনও থামছি। এক ঘন্টা , দু ঘন্টা , একটু বসে যাচ্ছি , জিরিয়ে নিচ্ছি রাত্রির খুব কাছে এই নিশ্বাস। এই অনুভব যেন কখনও আসেনি। আমি কখনও বিস্তৃত পৃথিবীর মাথার ওপর দিয়ে এইভাবে চলাচল করিনি। এ কোনও মহাকাশ নয়। এ তবে কোথায় ? আর আমি একাই বা কেন ? কার জন্য অপেক্ষায় থেকেছিল এরা বর্তমানে? অতীতেও বা কে এসেছিল এখানে ? কেউ কি এসেছিল এখানে কোনওদিন ? যারা বানিয়েছিল তারাই বা কে ? মানে শিল্পী সংসদের কথা বলছি আরকি । অথবা ইঞ্জিনিয়ার। লেবার। আবার হাঁটছি পথ । আর দুই ঘন্টা পর পথ বুঝি শেষ হল। দেখতে পেলাম উপরিতলের শেষে নেমে যাওয়ার স্পষ্ট নিশান। সেইরকমই যন্ত্র। এবং সেই যন্ত্রের ভেতরে পুনরায় প্রবেশ করলাম।
অভয়ারূপেণা সংস্থিতা
শুভজিৎ গুপ্ত
১
৯ আগস্ট ২০২৪। হতেই পারতো বাঙালির গণ আত্মার আরেকটি হাহাকারদিন।প্রাথমিক সুকুমার দিনগুলো সেরকমই ইঙ্গিত রাখছিল। কেননা এ সময় মনিপুর, পার্ক স্ট্রিট,কামদুনি,ইরম শর্মিলা চানুর অনশন থেকে নার্গিস মোহাম্মদীর কারারুদ্ধ থেকে যাওয়া সবেতেই পলিতকেশ বৃদ্ধের মত উত্তেজিত হয়েছে। তারপর উত্তেজনাবশত উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হাড় -পাঁজরের যন্ত্রণাকাতর হয়ে রিয়েলিটি শো দেখতে বসেছে। কিন্তু এই শ্রাবণ মাস অন্যরকম হলো। প্রথাগত শ্রাবণের বাবাযাত্রা ছেড়ে নারী নামলো রাতপথ দখলে। শ্রী- অনুপ্রেরণা- ভান্ডার প্রথার নিচে চাপা পড়ে থাকা স্হাণু আত্মা জেগে উঠে বললো— উই ওয়ান্ট জাস্টিস।
১৪ আগস্ট মধ্যরাত।বাঙালির ঘুমিয়ে পড়া ভাঙাচোরা আত্মা স্বাধীন হলো। কেননা আজো তরুণ প্রাণেরা স্বপ্ন দেখে, দ্রোহ করে, শাদাকে শাদা আর হাওয়াই চটিকে মিথ্যেবাদী, প্রতারক বলতে পারে। রাজনীতি আফিমনেশা তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে না। অতএব—
“ওরা ভেবেছিল আমরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম
আমরা দাঁড়ালাম
ভাঙাকে জোড়া দেওয়া এই সুদূরপ্রসারী মিছিলে।
ওরা ভেবেছিল আর আমাদের কিছুই থাকলো না।
মুঠো করতেই
খালি হাত গুলো আমাদের ভরে গেল। “
(এই মিছিল এই রাস্তা, কাল মধুমাস—সুভাষ মুখোপাধ্যায়)
ইতিহাসের কথা থাক। ২০২৩ সেপ্টেম্বর পোশাকবিধি না মানায় কুর্দি তরুণী মাসা আমিনিকে রাজধানী তেহরানে আটক করে নীতিপুলিশ। পুলিশী হেফাজতে মাসার মৃত্যু দেশজুড়ে প্রতিবাদ ছড়ায়। মাসা হিজাব খুলেছিলেন। অভয়া খুলেছেন রাজ্য রাজনীতির মুখোশ। মাসার মত অত্যাচারিতা হয়ে, প্রাণ দিয়ে। এখানেই মাসা- অভয়ারা পুরাণ মোটিফের শ্রদ্ধারূপেনা সংস্থিতা হয়ে উঠেছেন।আমরা যারা এ সমাজে মার্কিন শিল্পী ওয়ারহলের ব্যাখ্যাত ১৫ মিনিটের সেলিব্রিটি হতে উন্মুখ, আমাদের বর্তমান শৈশব রিল ও রিয়েল বিভেদ ভোলা, আমাদের বর্তমান যৌবন রাজনীতি ও ধর্মের আইটেম সঙ শুনতে শুনতে দিশাহারা, প্রবাসী, আমাদের বুদ্ধিজীবিকা চটিচাটা, চটিচাটা, চটিচাটা সংগীত মগ্ন।
২
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। (মুন্ডক উপনিষদ ৩/১ ,শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/৬)
হতেই পারতো নারী-পুরুষ উপনিষদের দুটি সুপর্ণ। চরাচরে সংসারবৃক্ষে, জীবনপ্রমিতিতে সকাম ও নিষ্কামকে ধারণ করে আছে। কিন্তু হায় ঈদৃশ পৃথিবীতে, অধিকন্তু মানববিশ্বে কখনও তা হয় নি। অতএব পুরুষ প্রধান ও ভোক্তা হয়েছে। কিন্তু সে নামটি পেয়েছিল অন্য অর্থে। পৃ(=পুরণ করা)+উষ—>পুর(যিনি অন্যের অভাব পূরণ করেন)+উষ। পুরুষের স্ত্রীবাচক শব্দ নেই। আছে নারী।
“বেদের ভাষার মধ্যে যাহা যাহা প্রাচীনতম সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল ‘নারী’; এই নারী শব্দ ‘নর’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় নাই।সে যুগে নর শব্দটি ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য নারী শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী।… পারিবারিক নেত্রী তিনি ভোগ-বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না।”
( বিজয় চন্দ্র মজুমদার, ভারতী, আশ্বিন ১৩২০)
‘মেয়ে’ শব্দটি জন্মেছিল মাতৃকা- মা+ ইআ> মাইয়া>মায়্যা>মেয়ে। মাতৃজাতি। সমাজের পুরুষশক্তি মাতৃমর্যাদা নয় বেছে নিলো মেয়েমানুষ, মেয়েছেলে ,মহিলা (ভদ্ররমণী), রমণী ( রমণ বা সম্ভোগে তৃপ্তকারিনী, এমনকী কাশীদাসী মহাভারতের ভাষ্যেও—” জননী রমণী হয়, রমণী জননী।”) কামিনী, ললনা( বিলাসকারিণী),বামা
(অশুভসূচক ,প্রতিকূল),ভামিনী (ভাম বা কোপযুক্ত)প্রমদাজন, ইত্যাদি। প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠলো নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পটবদল চিহ্নিত হলো— অন্তঃপুরিকা পুরনারী, পুরলক্ষ্মী,পুরাঙ্গনা,পুরস্ত্রী, পুরবালা, ইত্যাদিতে। নারীপুরুষ ভেদ সুস্পষ্ট হল—মেয়েমানুষ, মেয়েমহল, নারীজাতি, স্ত্রীজাতি, নারীসম্প্রদায়, প্রমীলাজগৎ শব্দাদিতে। ভুটিয়ানীদের শ্রমশক্তি দেখে —>বেগম রোকেয়া ‘কূপমন্ডুকের হিমালয় দর্শন’ রচনায় রচনায় সুস্পষ্ট লিখলেন—
“মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্পর্কে একবার লিখিয়াছিলেন যে “রমণীজাতি দুর্বল বলিয়া তাহাদের নাম অবলা; জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানীরাও ঐ অবলা জাতির অন্তর্গত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষদের প্রত্যাশী নহে, সমভাবে উপার্জন করে।”
৩.
যে জাতি মাতৃবন্দনায় পুস্পকরজোড়ে উচ্চারণ করে-“কুচুযুগশোভিত মুক্তাহারে”, এত সহজে তার পৌরস লালসার ঘোর কাটবে না। বরং ধীরে ধীরে দুর্গা -লক্ষ্মী -নির্ভয়া -অভয়া -তিলোত্তমা- উমাদের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ দাউদাউ অগ্নিমন্ত্রে পুড়ে যেতে দেখাটাই তার নিয়তি হবে। এই দান -অনুদান -সেবক-করসেবক -উৎসব সিন্ডিকেটময় সমাজের চিৎশক্তিরূপে জাগ্রত হয়েছে অভয়া ।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “শিল্পী” গল্পের মদন তাঁতির মত একক অবিচল ।শক্তিরূপেণা সংস্থিতা। মনে মনে জানতেন মৃত্যু স্থির। কায়িক মৃত্যু ।মাথা নত করে দাও হে বলে আত্মিক মৃত্যুর পথ বেছে না নিয়ে তাঁর এই স্মৃতিরূপেণা সংস্থিতা হয়ে ওঠায় অনেকদিন পর ইতিহাস বইয়ের বাইরে বাঙালির মনে পড়ে গেছে প্রীতিলতা, বীণা দাস ননীবালা, চুনিবালা ,মাতঙ্গিনীদের নাম।
মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী মেঝেন কে মনে পড়ে? পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে। জমিদার -জোতদার -মজুমদারের বিরোধিতা রাষ্ট্রদ্রোহই বটে । সেনানায়ক সিপাহীদের আদেশ দেয়, আমার জন্য বানিয়ে দাও ।তারপর কাপড় খোলা হয় । চার-পাঁচ- ছয় -সাত-তারপর দ্রৌপদী চেতনা হারায় ।জ্ঞান ফিরলে আবারো বানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতে থাকে ।কোনো এক সময় বড়োসাহেবের তাঁবুতে যাবার হুকুম হয় । দ্রৌপদী উঠে পড়ে। টলমল।তারপর শরীর ঢেকে রাখা কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেনানায়ক চমকে উঠে বলে কাপড় কই ওর কাপড়?
” চারিদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশশার্টটিকেই বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে – হেথা কেউ পুরুষ নাই যে লাজ করব ।কাপড় মোরে পরাতে দিব না ।আর কি করবি লে কাঁউটার কর ,লে
কাঁউটার কর ” (দ্রৌপদী – মহাশ্বেতা দেবী)
অভয়ার মৃত্যুও আসলে এনকাউন্টার। প্রতিবাদের এনকাউন্টার ।শক্তিরূপেণী হওয়ার এনকাউন্টার স্থিতিরূপিণী হওয়ার এনকাউন্টার । এই এনকাউন্টার একটা আত্মবিস্মৃত , আধঘুমন্ত জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছে কশেরু ছুঁয়েছে পাইপগান।
সাহেব, পাল্টা দ্যাখো…
দেবাঞ্জন দাস
দুপুর থেকে রাত হতে হতে হেদিয়ে মানুষ সকালের রুটিতে খোসা সহ গম, ময়দা একেবারে নয়। তারপর খালি বা ভরা পেটে ফল সন্ধ্যাকে জাপটে লাল ওয়াইন হৃদয়ের পক্ষে নাকি ভালো। দিনলিপি হয়ে যাওয়া জীবন কখন যে শান্তিতে একটু পেঁদে নেবে, নাহয় অগোচরেই, তার ভাবনার আলে-বালে ঘুরে বেড়ায়।এহেন ঘুরে বেড়ানোই তো ভোর থেকে রাতকে এক এলানো শৃঙ্খলায় বাঁধে। একে গণতন্ত্র বলা যায় না? ১৪ই আগস্টের রাতে তবে কে পথ হেঁটেছিল? কারই বা ঈষৎ লাল আকাশ পয়লার অক্টোবরে গাঢ় লাল হয়েছিল ফিল্টারে?
৯ই আগস্ট ২০২৪ কিছু ভুল বোঝাকে বিদায় জানাতে থমকানো শহর বাঙালী মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়িয়ে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অর্থনীতির সূত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম নিয়োজনের শিল্পায়নে সঠিকার্থে পৌঁছালেও বিকাশের প্রশ্নে জনপরিসর ও জনঅংশগ্রহণ এবং নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে কি ভুল বোঝেননি? তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সমাজ মাধ্যমে আপামর থেকে পৃথক বাবু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিয়ে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-শ্বেতশুভ্র-বৌদ্ধিক চর্চা কি রাজনৈতিক স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের ভুল প্রচেষ্টা নয়?
এর উত্তর খুঁজতে বেরিয়ে এক আলোকপ্রাপ্তির বাঙালী আর্কিটাইপ চরা পড়ে যাওয়া গাঙ্গেয় বন্দরে ঢুঁ মারে। সে আরও অসহায় এক নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে ভদ্রবিত্তে উত্তীর্ণ হওয়া বাঙালী কন্যার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণ ও খুনে। আর জি করে সে অপ্রিয় আয়নার সামনে। ধসকে যাওয়া বিগত গৌরব, বেহাল রাজনীতি-অর্থনীতি, পরিযায়ী শ্রম—সবই তো সয়ে গেছিল! ব্যক্তিগত আশা-নিরাশার পরিসরেও রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান কি তবে আজ সবেধন স্বপ্ন পূরণে অন্তরায়? এই প্রশ্নেই অজস্র অসামঞ্জস্য নিয়েও এক হতে চায় কলকাতা থেকে পুরুলিয়া। ছুঁয়েও ফেলে।
১৪ই আগস্ট ২০২৪-এর রাতে এহেন না-হতে পারা আকাঙ্ক্ষাগুলোই সর্বত্র রাস্তা ছোট করেছিল। দল বহির্ভূত এক রাজনৈতিক আহ্বানে দখল হয়েছিল জাতির মানসপটে এক উদযাপিত “stroke of midnight”। সেখানে রাজনীতি ছিল—ধর্ষণ ও খুনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক অমানবিক প্রতিক্রিয়া ও দম্ভের বিরোধিতা। লিঙ্গ রাজনীতির এক সুস্পষ্ট পরিসর বলতে বলতে ‘রাত দখল’ সার্বিক। ঐ সেই ‘উত্তরণ’-এর আকাঙ্ক্ষা ও তার বিপ্রতীপে রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক বাধার প্রতিবাদ। আর এই প্রশ্নেই ‘রাত দখল’ লিঙ্গ রাজনীতি ও বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের নিরিখে এক দ্বান্দ্বিকতার সূচনা করে। ‘অভয়া’ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সেই দ্বান্দ্বিকতা আজও বহমান।
‘অভয়া’ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ লিঙ্গ রাজনীতিকে অস্বীকার না করেই, পুরুষতন্ত্রের প্রতি, পুরুষতান্ত্রিক দম্ভের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে সামগ্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে চায়। সেখানে ৪২ দিন কর্মবিরতিতে জুনিয়র ডাক্তাররা। ছিল সরকার, সরকারি দলের তাঁবেদার গণমাধ্যম-বুদ্ধিজীবীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও দরিদ্র মানুষের উপায়হীনতা সংক্রান্ত অজস্র অপপ্রচার, কুকথা। তাকে বুড়ো আঙ্গুলে রেখে প্রতিস্পর্ধী জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে একাত্ম সাধারণ মধ্যবিত্ত, ভদ্রবিত্ত মানুষ। এক ঐতিহাসিক অবস্থান স্বাস্থ্য ভবনের সামনে। মানুষের নৈতিক সমর্থন জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিকে। অবস্থানকারী ডাক্তারদের আন্দোলনের খরচের অংশীদারিত্বও। সরকারের পেশাদার আমলাতন্ত্রের সাথে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি আদায়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কৌশল আন্দোলিত করে সামাজিক প্রতিস্পর্ধাকে। অবশ্যই মূলত মধ্যবিত্ত ও ভদ্রবিত্তের পরিসরে।
৯ই আগস্টের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণ ও খুনের পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে আলোড়ন ফেলে দেওয়া দুটি আন্দোলন—‘রাত দখল’ ও জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি—অরাজনৈতিক বলে চিহ্নিত হয়েছে বা চেষ্টা হয়েছে। এই প্রাণান্ত অপচেষ্টা কাদের? ঐ মধ্যবিত্ত ও ভদ্রবিত্তের। এই অপচেষ্টার মূলে চালিকাশক্তি হল শ্রেণিগত জাড্য যাকে শ্রেণিস্বার্থও বলা যায়। এই স্থবিরতা বা সংগ্রাম বিমুখতা পশ্চিমবঙ্গের বুকে বুর্জোয়া প্রভুদের বুনে দেওয়া এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নকশা স্পষ্ট করছে দিন দিন। সেই নকশার কাছে এই প্রবল গণবিক্ষোভকে ‘অরাজনৈতিক’ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই নকশা ভদ্রবিত্তের হাম্বা রবের স্বীকৃতিতে নির্মিত হয়নি। কিন্তু নিজেরই অজান্তে, শ্রেণিগত জাড্যের কারণে নকশায় হাত রেখেছে তারা—গণআন্দোলনের রাজনীতি নির্মাণ না করে বা খণ্ডিত রাজনীতির কথা বলে, সার্বিক ক্ষমতাতন্ত্রকে আঘাত করা থেকে সরে এসে।
কথাটা আর একটু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরে আলোচনা করতে গেলে ঘুরে তাকাতে হবে ‘অভয়া’ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির দিকে। সিপিআই(এম) তথা বামফ্রন্ট, বামফ্রন্ট বহির্ভূত বামপন্থী দলগুলি, জাতীয় কংগ্রেস, বিজেপি—এই সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে খুন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে স্বভাবতই রাস্তায় নেমেছিল। তারা সকলেই জনপথ আন্দোলিত করেছে। এবং নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, লুম্পেনরাজ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মর্যাদা হরণকারী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস তার তাঁবেদারদের নিয়ে একলা পড়ে গেছে। কিন্তু এই ভাষ্যটি যথেষ্ট নয়। এই একলা রাজনৈতিক দলটির ‘সংবিধান স্বীকৃত’ প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল একটি সাম্প্রদায়িক মনুবাদী দল। যাকে আমরা ‘ফ্যাসিস্ত’ বলি। সে নির্বাচনে জয়লাভ করে, উপুর্যপরি তিন বার প্রকৃত প্রস্তাবে সংখ্যালঘু মানুষের ভোটে জিতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছে—এমনই আমাদের গণতন্ত্র ও সংবিধান! এহেন এক ‘কদলী গণতন্ত্র’-এর দেশে “রাজনীতি”-কে “দূর”-এ রাখতে হয়ত বাধ্য হয়েছিল ভদ্রবিত্ত। নাহলে যে ধর্ষণ, খুন ও দাঙ্গার দলটিকে মান্যতা দিতে হয়! অন্যদিকে পার্টির অভ্যন্তরে ‘গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা’র গালভরা মিথ্যা অনুকরণে ‘সুপার স্ট্রাকচার’-এর সাধনা করে “কমিউনিস্ট পার্টি”গুলি। তারা কোন এক লৌহ পুরুষের ছায়ায় ‘দলতন্ত্র’ ও ‘গণতন্ত্র’-এর পার্থক্য করতে নারাজ। এদের কীভাবে মান্যতা দেওয়া যায়! আজও তারা নিজেদের ভুল মানতে নারাজ। জন অংশগ্রহণ ও জনচেতনা বিস্তারের কাজে ‘দলতন্ত্র’ অপেক্ষা ‘বহুস্বর’কে ধারণ করতে পারার অক্ষমতাকে মানতে নারাজ। ভোটের রাজনীতিকে সংগ্রামের চোখে নয় ঐকিক অংকের নিরিখে দেখতে শিখেছে। এগুলো না করেও এক ভিন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রম হয়ত ছিল তা আত্মখননকারী—সর্বোপরি নিজেকে সক্রিয় হতে হয় জনগণের স্বার্থে, জনগণের মাঝে, রাজনৈতিক কার্যকলাপে। এতগুলো নেতি-কে ঐ একটা ‘অরাজনীতি’র ‘অ’ ধরে আছে! সে’কারণে এটা ‘নেতি’-র ‘নেতিকরণ’-এ পৌঁছয় না। মুখ থুবড়ে পড়ে জাড্য ও স্বার্থের চক্করে।
‘ডাক্তার’দের শ্রেণি স্বার্থ ও চরিত্র আরও গোলমেলে। মূল দ্বন্দ্বকে লঘু করে দেওয়ার জন্য পুঁজিবাদী সমাজের সর্বস্তরে গোঁফে তা দিতে দিতে সমাজ ও মেধা বা সমাজ ও ব্যক্তির লোকদেখানো দ্বন্দ্বের উপস্থাপন করা হয়। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ডাক্তারদের মত উচ্চবর্গীয় পেশাজীবীদের মধ্যে। তাদের কাছে মানুষ নিতান্ত সংকটকালে হাজির হয়। এবং বহুক্ষেত্রে সঙ্কটাপন্ন মানুষের সামনে তাদের নির্দয় শাইলক হয়ে উঠতে দেখা যায়। সে’কারণে সাধারণ খেটে খাওয়া দরিদ্র নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ এদের মোটা দাগে ঘৃণা করে। এই ঘৃণাকে শ্রেণি ঘৃণা হিসেবেই দেখা যেতে পারে। মেডিকেল কলেজ, আই আই টি, আই আই এম-এর সব মহত্তমরা ভুলে যান তাদের পেশাদারী উত্তরণে সমাজের অবদান।পেশাদারিত্ব বড় হয়ে যায় মানবিকতার কাছে। সাধারণ মানুষ বহুক্ষেত্রেই ডাক্তারের প্রতি সন্দিহান থাকেন যে যা প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে তা আদৌ জরুরী না কাঙ্ক্ষিত কমিশনের প্রয়োজনে! তবু এ ব্যবস্থা চলছে। কারণ চালাচ্ছে যারা তারা রাষ্ট্রনায়কের প্রভু! যেমন আজকের এই দুর্গা পুজো ও ঈদ নিয়ে কচকচানির জামানায় রেশন দোকানদারের বাড়ির ইষ্ট দেবতার মহোৎসব নিয়ে ভাবা যেতে পারে। সেখানে ইষ্ট দেবতা উপলক্ষ মাত্র। ডাক্তাররা তাদের প্রতি এই প্রচলিত আখ্যানের বিরুদ্ধে এবারের আন্দোলন পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন—‘অভয়া ক্লিনিক’, বন্যা ত্রাণ ও পীড়িত মানুষদের চিকিৎসা। তার ধারাবাহিকতার উত্তর হয়ত ইতিহাসে থাকবে—ত্রাণ বা সেবা ‘জনস্বাস্থ্য আন্দোলন’কে ছুঁতে পারবে কিনা।
অপরদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিবিধ অনুদান পাওয়া নিম্নবিত্ত হাঘরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবস্থান ভদ্রবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের থেকে এতটাই পৃথক যে তাকে সমাজ মাধ্যমের মিমে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক, খেতমজুর, দিনমজুর, গতরখাটিয়ে, নিম্নবিত্ত ব্যবসাদার জনতা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দিনযাপন পর্যায়ক্রমিক ভবে দূরহ হয়ে উঠছে। সরকারি-বেসরকারি কর্মসংস্থান নেই, বাজারে অর্থের যোগানের অভাব, অলাভদায়ক চাষ কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অর্থের যোগানের অভাবে বাজার না থুবড়ে পড়ে। রাষ্ট্র তার অপদার্থতা ঢাকতে অনুদানের মাধ্যমে বাজারে অর্থের যোগান দিচ্ছে, চেষ্টা করছে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করার। এ’সবই নিজ প্রভু—পুঁজিবাদের প্রতি বরকরার সেবা মাত্র। আর তুমি সুমুন্দির পো অনুদান নিয়ে মিম বানাচ্ছ! চেষ্টা হচ্ছে না তো উৎপাদিকা ব্যবস্থার বিকল্প জনমুখী উপায় নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়ার! বিগত দিনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও তার দলতান্ত্রিক উপভোক্তা শ্রেণি নির্মাণের প্রশ্নেই বা ভূমিকা কি ছিল? কোথায় তার আত্মসমালোচনা? সুতরাং নিম্নবিত্ত হাঘরে বোলচাল ও মিমে পটবে কেন? আপাতত এই শ্রেণিগত ভিন্ন অবস্থানেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকল। ভারত রাষ্ট্রের গঠন—জাতি রাষ্ট্রের ধারণার ব্যর্থ অনুবাদ—সংক্রান্ত রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা তোলা থাকল।
এহেন এক টালমাটাল রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐ পূর্বোক্ত খণ্ডিত রাজনীতির দায় জুনিয়র ডাক্তারদের উপর চাপিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছে ভদ্রবিত্ত। জুনিয়র ডাক্তারদের দফা ও দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেও, পশ্চিমবঙ্গের পচে-গলে যাওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত, লোকদেখানো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাক্ষাৎ ভুক্তভোগী মানুষ দ্বিধাহীন ভাবে হয়ত বলতে চাইবে, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন পেশাগত দাবিদাওয়ার ঘেরাটোপে আটকে যায়। সরকারের পেশাজীবী আমলাতন্ত্রের সাথে জুনিয়র ডাক্তারদের দরকষাকষিতে একপ্রকার সন্তুষ্টির স্বাদ হয়ত থাকে। স্বপ্নালু ভদ্রবিত্তের প্রতিস্পর্ধীতার সন্তুষ্টি। কিন্তু এর ব্যাপকতর অন্যথা হতে পারত। এর ফলস্বরূপ ক্ষমতাতন্ত্র আজও চাঁদমারির বাইরে থেকে গেছে। এনকাউন্টার দাওয়াই, ‘রাত্রের সাথী’ ও ‘অপরাজিতা’ তো পুরুষতন্ত্রের একপ্রকার অহমিকা পুনস্থাপনকারী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই ক্ষমতাতন্ত্র টিকে আছে স্বমহিমায়! এখনও শিশ্নকেন্দ্রিক ভাষা ও চেতনার নিগড় অটুট। তাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য ‘রাত দখল’-এর ‘র্যাডিকালিজম’ অপেক্ষা সমানাধিকারের ‘র্যাডিকালিজম’ হয়ত আজও এক বৃহত্তর রাজনীতির পরিসর নির্মাণ করতে পারে। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রের বোলবোলা থামিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ক্ষমতাতন্ত্রের প্রভাবশালী মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব অধিকতর শক্তিশালী প্রায়োগিক রাজনীতির নিরিখে।
কিন্তু সেই রাজনীতি তো কেবল ভদ্রবিত্তের আয়ুধ নয়! তার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মতাদর্শের বয়ানে ‘অপর’ হয়ে পড়ে থাকা ঐ ‘অনুদান নির্ভর’ করে ফেলা মানুষগুলোকে প্রয়োজন। সে যোগাযোগ যদি স্থাপিত না হয় তাহলে ‘অভয়া’ পরবর্তী গণআন্দোলনে সাম্প্রদায়িক, মনুবাদী বিজেপি-কে দূরে রাখতে পারার শ্লাঘা হাতছাড়া হতে পারে। ঐ ‘অপর’, ‘প্রান্তিক’, ‘দরিদ্র’, ‘দিন আনি দিন খাওয়া’, ‘গতর খাটিয়ে’ মানুষগুলোকে বাদ দিয়ে যে ‘গণআন্দোলন’-এর স্বপ্নমিনার গড়া হচ্ছে তা দূরের লাইট হাউসের মতোই একদা হারিয়ে যেতে পারে। উৎপাদিকা শক্তির শোষণ ও প্রাত্যহিক লড়াইতে যে মানুষগুলো প্রতিদিন নাজেহাল, রাষ্ট্র ও সমাজ যাদের ‘অনুদান নির্ভর’ দাগিয়ে মিম বানিয়ে ফেলেছে। অসংখ্য বিশেষণে তারা যে অসম্পৃক্ত থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তাদের উৎপাদিকা শক্তি কেন্দ্রিক লড়াইতে একদিকে রাষ্ট্র আপন প্রভুর মর্জিমাফিক হাত গুটিয়ে নিলো। অন্যদিকে ভদ্রবিত্ত অধ্যুষিত রাজনৈতিক দলগুলি কোন ভূমিকা পালন করল? কেউ ঈদ ও দুর্গা পুজোর বিবাদ উস্কে দিল, কেউ মধ্যসত্বভোগীদের সিন্ডিকেট বানিয়ে অনুদানের রুটির টুকরো ছুঁড়ে দায় সারল আর কেউ অধ্যাপক, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের কৃষক নেতা বানিয়ে এক জগঝম্প নির্মাণ করে হেদিয়ে গেল! পশ্চিমবঙ্গের গতর খাটিয়ে নমঃশূদ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এক ভোটপিন্ড স্বরূপ ভদ্রবিত্ত সমাজ থেকে পৃথক ‘অপর’ অস্তিত্ব হয়ে বাইরে থেকে গেল। কেন থাকবে না? হে ভদ্রবিত্ত সমাজ, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকাগুলিতে হকার উচ্ছেদের নামে যে অরাজকতা, দুর্নীতি ও মাৎস্যন্যায় নির্মাণ করেছে শাসক দল সেখানে কতজন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বা তাদের লড়াইতে সাথী হয়েছেন? বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প ও নাবার্ডের মাধ্যমে যেভাবে পেছন দরজা দিয়ে কর্পোরেট চাষ মাঠের দখল নিচ্ছে তার বিপরীতে জৈব চাষের বাগাড়ম্বর বাদে প্রকৃত জনগ্রাহ্য বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে কতজন কাজ করতে চেষ্টা করেছেন?
এই পার্থক্যের নিরসনই হল রাজনীতি। আর তা না হলে রাজনীতির খণ্ডায়ন থেকে যাবে। নারীবাদ বা লিঙ্গ রাজনীতির সাথে সমানাধিকারের দ্বন্দ্ব থাকবে, সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও মাৎস্যন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ডাক্তারদের স্বার্থ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হবে এবং সম্প্রদায়-জাতি-ধর্ম-এর পার্থক্যের ফাঁকে গোঁফে তা দেবে শ্রীমৎ বাজার মহাশয়। ভদ্রবিত্ত জুনিয়র ডাক্তারদের পেশাগত আন্দোলনকে, লিঙ্গ রাজনীতিকে, ভোটে দ্বিতীয় হয়ে “আটকে যাওয়া” সাম্প্রদায়িক, মনুবাদের পরাজয়ে মুক্তকচ্ছ হবে, সমাজ মাধ্যম গরম করবে যুক্তি-প্রতি যুক্তির শ্লাঘায়। তবু গতর নাড়িয়ে গতর খাটিয়েদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে মূল ক্ষমতাতন্ত্রের বিরোধিতার রাজনীতি নির্মাণ হবে না। ‘অভয়া’র প্রতীকী মূর্তির উপর মাথা রেখে ক্রন্দনরত তার বাবার ছবি ও মহালয়া পরবর্তী সময়ে তার মা’র বাঙ্ময় কান্নার বার্তায় দেবীপক্ষে অসুর বধের আশা শুনিয়ে বিচারের অপেক্ষা থাকবে সেই বিচারালয়ের কাছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সেই অংশীদারের কাছে, যে রাষ্ট্রের সবথেকে বড় শোষণের হাতিয়ার। যার ‘নিরপেক্ষতা’ বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই ‘সুনাগরিক’ হওয়ার অবকাশে এই প্রশ্ন উচ্চকিত হবে না, যে সমাজ একজন মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলতে পারে সেই সমাজে সেই মেয়ের নাম কেন উচ্চারণ করা যাবে না—কেন এই দ্বিচারিতা?
ফিরতি হাওয়া
সোজা করে দেবে
এমনটা সমুদ্র কেন ভাবে না বলে
শুরু করেছিলাম
রাত হয়েছে
মেঘেরা ত্রিপল টাঙ্গাচ্ছে আসমানে
ভাষা ঝরে যাবে
বর্শার আগায় জবান…
বল না, ওকে গা ঘামাতে
অন্যের খিচুড়িতে
টাকরার আওয়াজ বন্ধ করতে
মাংস বেশি হলে
পঙক্তি নিজেই বিসমিল্লা করে
সে দৃশ্যে সন্দেহ একলা বসে
আর কি লিখব না সঙ্গতের কথা?
মেঘের বিদ্যুৎ ঝনঝন করছে না
দু’চারটে শব্দ কি তুলে নেব?
অকারণ লিখে ফেলি এসব
কথার সাথে হুল্লোড় করে দেখা
অকারণ বেশি বাঘবন্দি
স্মৃতির লড়াই
কণিষ্ক ভট্টাচার্য
‘ভয় দেয় উদাসীন জল / মানুষের স্মৃতিও তরল’
শোক বিংশ শতাব্দীতে যে বর্ষকাল ভোগ্য আয়ু নিয়ে জীবিত ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে তার গড় আয়ু নেমে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন হুজুগের আগমনের সময়ের নিরিখে। এমনই দেখা যাচ্ছিল বিগত এক দশক। এমনই প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম আমরা।
তবু সমস্ত হিসেবকে ওলটপালট করে দেয় কোনও কোনও ঘটনার সামাজিক অভিঘাত। তাই তার স্থানানুসার আনুপূর্বিক স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের কাজ। কারণ ক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যক্তির লড়াই আসলে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির লড়াই। ক্ষমতাকাঠামো সবসময় গণবিস্মৃতিকে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে। ভুলিয়ে দিতে চায় ক্ষমতার সমস্ত রক্তপথের ইতিহাস। আমাদের কাজ প্রতিদিননিজের ক্ষতকে খুঁচিয়ে, নিজেরা রক্তাক্ত হয়ে, প্রতিদিন প্রতিটি আক্রমণের যন্ত্রণাকে বারবার অনুভব করা। বেদনাকে ভুলে না যাওয়া। মনে রাখা।
মনে রাখা, অভয়া-তিলোত্তমা কোনও ব্যক্তিনাম নয়।
মনে রাখা, অভয়া-তিলোত্তমা কেবল দেশের আইন বাঁচানো প্রতীকায়িত নাম নয়।
মনে রাখা, অভয়া-তিলোত্তমা কেবল নিজ কর্মক্ষেত্র সরকারি হাসপাতালে ছত্রিশ-ঘণ্টা চিকিৎসা করার পর কোনও ধর্ষিত ও খুন হওয়া একত্রিশ বছরের চিকিৎসক তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উত্তর-স্নাতক ছাত্রী নয়।
মনে রাখা, অভয়া-তিলোত্তমা আমাদের রাজ্যে, গ্রামে-মফস্বলে সরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে, কলকাতা শহরের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে রেফার হওয়া অসংখ্য মানুষের গিজগিজে ভিড়ের মধ্যে, যেখানে পাঁচশো মিটারের মধ্যে আরও চিকিৎসক, নার্স, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যপ্রশাসনের লোক, আয়াদিদিরা, সরকারি পুলিস, ব্ল্যাকশার্ট-ব্রাউনশার্টের মতো সরকারি দলের গেস্টাপো তথা নীলজামা-সবুজজামা, অবাঞ্ছিত দালাল, অগণন রোগী এবং হাসপাতালে রাত্রিবাস করা নিযুত রোগীর পরিজনের মাঝে একশট্টি কেজি ওজনের একজন একত্রিশ বছরের সুস্থসবল মহিলা চিকিৎসক, যিনি ধর্ষিত ও খুন হয়েছেন।
যাঁর শরীরে অসংখ্য ক্ষত ও প্রতিরোধের চিহ্নের কথা সংবাদমাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রকাশিত।
অথচ কেউ নাকি কিছুই জানেন না!
দুমাস কাটল। চার পক্ষকাল। আট সপ্তাহ। ষাট দিন। এক হাজার চারশো চল্লিশ ঘণ্টা।
এক চন্দ্রভুক অমাবস্যার থেকে গৃহত্যাগী জ্যোৎস্নার পূর্ণিমা এবং আরেক চন্দ্রভুক অমাবস্যা পেরিয়ে আরেক পূর্ণিমা আসন্ন। অথচ কেউ কিছুই জানে না। কলকাতা পুলিস, যাকে একসময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হত, সিবিআই যারা দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা — কেউ কিছুই জানে না।
তার পরের ঘটনাক্রমকে হয়তোবা আশ্চর্যজনক বলা যেত।
কী সেই ঘটনাক্রম? সংক্ষেপে বললে, ১. এই ঘটনাকে মৃতার বাবা-মাকে ফোন করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হল। ২. প্রিন্সিপাল ইতরবাক্য বললেন ‘রাতে কেন সেমিনার রুমে…’। ৩. মৃতার বাবামাকে কন্যার দেহ দেখতে দেওয়া হল না। ৪. ময়নাতদন্তের কানুন ভেঙে সূর্যাস্তের পর ময়নাতদন্ত হল। ৫. বাম ছাত্রযুব সংগঠনের নেতৃত্ব গিয়ে দেহ না আটকাল পুনর্বার ময়না তদন্তের জন্য। ৬. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ধর্ষিতা ও নিহতের দেহ দাহ করে দেওয়া হল। ৭. এমনকি শ্মশানের সার্টিফিকেটে মৃতার বাবা মা নিকট আত্মীয় নয়, সই করলেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। ৮. বাবা মা কে টাকার লোভ দেখানো হল প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে। ৯. এক মদ্যপ লম্পট গেস্টাপো, থুড়ি সিভিক ভলান্টিয়ারকে পাকড়াও করে তাকেই একমাত্র দোষী বলে প্রমাণ করতে চাইল কলকাতা পুলিস যাকে নাকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হত। ১০. পরিকল্পিতভাবে ক্রাইম সিন নষ্ট করা হল। ১১. রাত দখলের রাতে কিছু লুম্পেন পাঠিয়ে হাসপাতালের কিছু বিশেষ জায়গায় ভাঙচুর করানো হল, এবং হাসপাতালের নার্সদের বয়ান অনুসারে শৌচাগারে আর ওয়ার্ডে রোগীর কম্বল চেয়ে গাঢাকা দিল কলকাতা পুলিস। ১২. পিডাব্লিউডি হঠাৎই তৎপর হয়ে উঠে ক্রাইম সিনের আসেপাশে ভাঙচুর করে উন্নয়ন করতে লাগল। ১৩. প্রিন্সিপালের পদত্যাগের খবর মিডিয়ায় আসার চারঘণ্টার মধ্যে তার প্রাইজ পোস্টিং হল।
তবু এই সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশীর পরেও আশ্চর্য হলেন না রাজ্যের মানুষ। হলেন না নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, খড়গ্রাম, গেদে, কাকদ্বীপ, কাটোয়া, মধ্যমগ্রাম, রানাঘাট, সিউড়ি, হাঁসখালির একের পর এক নারী নির্যাতনের পরে প্রশাসনের ভূমিকা মানুষ দেখেছে। প্রশাসন ও শাসকদলের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে ভিক্টিম ব্লেমিং ও ইতরবাক্যের বন্যা বয়েছে, আইনি ও বেআইনি পথে ঘটনাগুলো সরাসরি ধামাচাপা দিয়েছে শাসক, তাতে আর নতুন করে আশ্চর্য হলেন না রাজ্যের মানুষ।
এই ঘটনাগুলোর কি প্রতিবাদ হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে। সে প্রতিবাদ সামগ্রিক সামাজিক হয়ে না উঠলেও, হয়েছে। এখানেই এই ঘটনাগুলোর থেকে অভয়া-তিলোত্তমায় এসে পার্থক্য ঘটে গেল মানুষের মনে। মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন কে প্রতিবাদ করবে তার জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই আর। রাত দখলের মতো একটি আর্বান-লিবারেল ডাক শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রান্তিক পরিধির দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেন্দ্রীভূত কোনও নিয়ন্ত্রক শক্তি নেই যার। কেবল একটি ধারণা তাও ছড়িয়ে পড়ল মফস্বলে প্রান্তিক গ্রামে, সমাজ শর্তে যা আর্বান-লিবারেল নয় এমন সব জায়গায়। আমরা দেখলাম নানা পেশাগত ও পরিচিতিগত সত্তায় মানুষ পথে নামলেন। এমনকি শাসক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত মুখও নামতে বাধ্য হল নানা কারণে। মানুষ সংগঠিত হলেন নানা পরিচিতিসত্তায় নির্ভর করে।
অরাজনৈতিক থেকে অদলীয় এই ধারনায় আসতে যে সপ্তাহ ঘুরে গেল আমাদের, তার অন্যতম কারণ সম্ভবত আমাদের বিশ্বাসযোগ্য সিভিল সোসাইটির অভাব। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন সিভিল সোসাইটির মুখ হয়ে উঠে টেলিমিডিয়ায় মুখ দেখানো কিছু মানুষ নিজেদের শাসকের এঁটোকাঁটা আশ্রিত করে তুলেছেন একদশক ধরে। এইখানে ঘটল দ্বিতীয় বদল। মানুষ বিশ্বাসযোগ্য কোনও মুখ পেলেন না বলে কোনও মুখের অপেক্ষায় বসে থাকলেন না, নিজেরাই নিজেদের মতো করে প্রতিবাদে পথে নামলেন।
পেশা আর পরিচিতিসত্তা নির্ভর মিছিল সভা পেরিয়ে একটি বড়ো নাগরিক মিছিল শহর ইতোমধ্যে দেখে ফেলেছে আগস্টের ২৯ তারিখে। সেখানে পেশা বা পরিচিতিকে অস্বীকার করে নয় বরং তাকে অঙ্গীকার করেই নাগরিক মিছিলে যুক্ত হয়েছেন মানুষ। কৃষক রমণীর পরের সারিতে ব্যন্ড মিউজিকের গিটার, আইনজীবীর পোশাকের পাছে যৌনকর্মীর প্ল্যাকার, মাঠের জার্সির পাশে শিল্পীর তুলি, শিক্ষকের পাশে ছাত্রছাত্রী, মিডিয়াকর্মী হাউস থেকে ছুটি নিয়েছেন মিছিলে হাঁটবেন বলে।
এরপরে জুনিয়র চিকিৎসকেরা কলকাতা পুলিস হেডকোয়ার্টার লালবাজার অবরোধ করলেন পুলিস কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে। কারণ ততদিনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা তুলে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সেখানে বলা হয়েছে এই হত্যা প্রাতিষ্ঠানিক ও তার তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। দুদিন টানা অবস্থানে বসে থেকে কলকাতা পুলিস কমিশনারকে প্রতীকী শিরদাঁড়া দিয়ে এসেছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। এরপরে তাঁরা করলেন স্বাস্থ্যভবন অভিযান কারণ পশ্চিমবাংলার সমস্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চলে শাসকদলের হুমকিরাজ, যাকে তাঁরা বললেন #থ্রেটকালচার। স্বাস্থ্যভবন কর্তারাও তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন না। জুনিয়র ডাক্তারেরা রাজপথে অবস্থান কালে তাঁদের রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পাশে এসে দাঁড়ালেন নাগরিক সমাজ। নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ও অর্থে এলো ত্রিপল থেকে চৌকি, শুকনো খাবার আর জলের বোতলের ঢিপি তৈরি হল এত উঁচু যে সোশ্যালমিডিয়ায় জুনিয়র চিকিৎসকদের জানাতে হল আর পাঠাবেন না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে তাঁদের ক্যান্টিনে তৈরি খাবার নিয়ে। এক মা কয়েকটা হাতপাখা নিয়ে এসেছিলেন নিজেই বাতাস করছিলেন ছেলেমেয়েগুলোকে। বঙ্গীয় ভাদ্রের পচা গরমে বইছিল নতুন ইতিহাস লেখার হাওয়া।
সুপ্রিম কোর্টের দোহাই দিয়ে লাইভ স্ত্রিমিং করল না শাসক, অথচ সুপ্রিম কোর্টের বিচার লাইভ স্ত্রিমিং হয় এবং শাসক নিজেই প্রশাসনিক সভা করে লাই স্ত্রিমিং করে। কী এমন প্রশ্ন ছিল পাঁচদফায় যা জনগণের জন্য লাইভে বলতে শাসকের বাধল? শেষ দুটি প্রশ্ন, থ্রেট কালচার ও দুর্নীতি। যে দুটি বিষয়ে পরবর্তী সভাতেও মিনিটস সই হয়নি প্রশাসনের তরফ থেকে।
আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারছি সংবাদমাধ্যমে নিছক ধর্ষণ খুন নয়! সুপ্রিম কোর্ট বলছে বিরাট কিছু ঢাকা দেওয়ার প্রবণতা আছে। কেবল নারী সুরক্ষার প্রশ্ন নয়। কর্মক্ষেত্রে নারী সুরক্ষায় যেমন সরকার দেখাতে চাইল দশদফা এমন নিদান দিয়ে যা আমাদের মতো দেশে নব্বই শতাংশের অধিক নারীপুরুষ যেখানে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে সেখান থেকে নারীদের সরিয়ে দেওয়ার নিদান হয়ে দাঁড়ায়। নারীদের সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি তৈরি করে দিয়ে চায়। এবং স্পষ্ট করে দিয়ে চায় যে, ওই গণ্ডির মধ্যে থাকলেই তবে তার সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের! নচেৎ নয়।
কেন এই মনে রাখা! কেন বারবার হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো!
আমরা এতদিনে একটি আকার অবয়ব পাচ্ছি ধারনার। সব মেডিক্যাল কলেজের যেন হুমকিরাজ, যাকে তাঁরা থ্রেটকালচার বলছেন। তা কি নতুন কিছু? বিগত তেরো বছরে আমরা কি দেখিনি বাঙ্গুর ইন্সটিটিউটের সামনে নেতামন্ত্রীমিডিয়া মিলে হাটুরে জটলায় হতবাক ডাক্তার শ্যামাপদ গড়াইকে কিংবা কিংবা কালীঘাট থানা থেকে দুষ্কৃতি ছাড়িয়ে আনার ঘটনা কি আমরা ভুলে গিয়েছি! উদাসীন জল আমাদের আমাদের ঘর ভাসালেও কি আমরা ভুলে যাই! সেই দুটি ঘটনাই ঘটেছিল প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ থেকেই! তারপরে রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ কে বাইরে এনে পেটানোর ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের ‘ছোটো ছোটো’ ছেলেদের দুষ্টুমি!
থ্রেট কালচারের প্রাতিষ্ঠানিকতা তো সেখানেই।
কেন এই হুমকি রাজ!
আসলে তা কি পারম্পর্যে পৌঁছে দেয় অভয়া তিলোত্তমায়। ওই অমীমাংসিত এবং প্রশাসনের পক্ষে মিনিটস স্বাক্ষর না করা দুটি বিষয় অর্থাৎ থ্রেট কালচার ও দুর্নীতি কি পরস্পর সম্পর্কিত!
তেমন আশঙ্কার কারণ আছে বৈ কি!
এমন এক রাজ্য যেখানে কোনও শিল্প নেই, যাও চেষ্টাচরিত্র করে এসেছিল তাও পাত্তারি গুটিয়েছে। যেখানে সরকারি শিক্ষকের চাকরির পরীক্ষায় দুর্নীতির দায়ে একডজন মন্ত্রী বিধায়ক আমলা জেলে। যেখানে বছরের পর বছর পরীক্ষা হয় না চাকরির। যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ। লেখাপড়া ছাড়ার হার উদ্বেগজনক তা সরাসরি পেশার ক্ষেত্রের লোকজন জানেন, সরকারি কাগজ যাই বলুক না কেন! পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সংখ্যা আনুপাতিকভাবে মেলে না! অথচ আমরা শুনি ‘শ্রী’ প্রকল্পের সাফল্যে ছাত্রী সংখ্যা আশাতীত হারে বেড়েছে। আচ্ছা, মোট পরীক্ষার্থী বাড়েনি অথচ ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে এর অর্থ তো ছাত্র সংখ্যার হ্রাস! প্রাথমিক স্তরের পাটিগণিত তাই-ই বলে! সংবাদপত্রে দেখা যায় উচ্চশিক্ষায় বহু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন খালি পড়ে থাকে। তথাকথিত সাধারণ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নয় বরং জনমানসে যা ‘এলিট’ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিচিত সেখানকার ছবিও খুব ভিন্ন নয়! আমার রাজ্যের শিক্ষার্থী যৌবন তাহলে কোথায়! তাঁরা পড়াশোনায় উৎসাহী নয়, কারণ পড়াশোনা করলেও কাজ নেই বলে। এমনিতেই কাজ নেই তার ওপর কাজ পেতে গেলে নগদ নারায়ণ ব্যতীত ব্যবস্থা আর কোনও উপায় রাখেনি তাঁদের জন্য। জেলায় জেলায় ১৬ থেকে ৪০ বছরের পুরুষ তথাকথিত অর্থে পরিযায়ী অন্য রাজ্যে কাজ খুঁজতে। আন স্কিলড লেবার হিসেবে, জনমজুরি খাটতে। জনস্রোত চলেছে আমার রাজ্য ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হতে। যারা পড়ে থাকছে এই নৈরাজ্যে নেই-রাজ্যে সেই হতাশ নুব্জ যৌবন ভিন্ন পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে পেটের তাগিদে, হয়ত তেমন ভালো পথ নয় তা। ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষমতার বোরে হিসেবে। ‘শ্রী’মণ্ডিত মেয়েদের কী অবস্থা! বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মদিবস পালনের সময় বিদ্যাসাগরের বাংলা মেয়েদের বাল্যবিবাহের হারে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে। বিদ্যাসাগেরর বাংলা অপ্রাপ্তবয়স্ক মাতৃত্বে দেশের সেরা! পাচারে ওপরের দিকে। আমার রাজ্যের যৌবন কোথায়!
যে পারম্পর্যের কথা আমরা বললাম অভয়া তিলোত্তমায় আসার সেটা তো এখানেই! আমাদের রাজ্যে কোনও অর্থনীতি নেই। শিল্প নেই। আমরা শতাধিক আলুচাষির আত্মহত্যার কথা ভুলিনি। কৃষি এমনিতেই অলাভজনক হয়ে উঠেছে বলে বহু জমি ফেলে রাখা হচ্ছে অকর্ষিত। চাষের কাজ করানোর লোক পাওয়া যায় না কারণ কৃষি শ্রমিকের মজুরি নিচের দিকে। মনরেগা থেকে আবাস যোজনা সবেতেই চুরির আখড়া বলে খবর হয় কাগজে। লাভজনক কৃষিহীন, শিল্পহীন ভেঙেপড়া অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা ভালো, এই প্রতিবেদক মনে করেন না যে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের, ধান্দাপুঁজির, কম স্বাক্ষরতার, বেঁচে থাকার সাধনের স্বল্পতার দেশ পূর্ণত দুর্নীতি মুক্ত হবে এমন ভাবা কল্পনাবিলাস। কিন্তু একটা রাজ্যের গোটাগুটি অর্থনীতিটাই হয়ে পড়বে দুর্নীতি মূলক এমন না-ও হতে পারত, না-ও হতে পারে। না-ও হয়। নাগরিকের জীবন-জীবিকাকে পূর্ণত কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নামে দলীয় আনুগত্য অভিমুখী করে তুলে যা হয়েছে তা হল, নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে ‘বার্গেইনিং’ দরাদরির সম্পর্ক ছিল তা সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছে। এবং সেটা করতে গিয়ে গণতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তার ভিত ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রের দিকে তাকালেই দেখবেন স্কুলের এমসি, কলেজের জিবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সিন্ডিকেট সব নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্রকে চুলোর দোরে পাঠিয়ে মনোনীত নিয়োগ হয়েছে। ছাত্র সংসদেও তাই-ই। এটি কেবল উদাহরণ মাত্র। আপনি চেনাশোনা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকান। দেখতে পাবেন ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ। সাধারণ নির্বাচনের ছবি যাঁরা নির্বাচন করাতে যান তাঁরা জানেন, যেমন জেনেছিলেন রায়গঞ্জের রাজকুমার রায়। ভোট লুঠ আটকাতে নিজের প্রাণ দিয়ে। এবং তখনও আত্মহত্যা বলে কেস সাজানো হয়েছিল। এখনই তারিখ পে তারিখ। এই অর্থনীতিহীন দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই, প্রতিটি বুথ জিততে হবে, যেকোনো উপায়ে, এমন মরিয়া প্রয়াস। তার জন্য জনসমক্ষে নেতানেত্রীরা অতিরিক্ত সরকারি টাকা খয়রাতি দেবেন বলে ঘোষিত হয়। সেখানে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আসে সেই #থ্রেটকালাচার। আসে গাঁজা কেস।
এখানেই থাক শ্রেণিগত পাপের স্মারক। আমরা স্বীকার করে নিই অভয়া-তিলোত্তমা আন্দোলনের অগ্রবর্তী অংশ হল আর্বান-লিবারেল-মিডিলক্লাস। চিকিৎসক ও সিভিল সোসাইটি দুটি অংশই এর অন্তর্গত। এই ‘মনে রাখা’র লড়াইয়ের চেষ্টা যাদের— যিনি লিখছেন, যাঁরা পড়বেন, যে মাধ্যমে পড়া হবে, সবই ওই শহুরে-প্রগতিশীল-মধ্যবিত্তের জন্য। অথচ এই স্বাস্থ্য দুর্নীতির সবচেয়ে বড়ো আক্রমণ কিন্তু তাঁদের ওপরে নামেনি এখনও। সবচেয়ে বড়ো শিকার এখনও তাঁরা নন। তাঁরাও হবেন, যখন এই টাকার বিনিময়ে চান্স পাওয়া, পাশ করা, নম্বর বাড়ানো, অনার্স পাওয়া, পিজি পাওয়া ডাক্তারেরা পুরদমে চিকিৎসা পেশায় নেমে পড়বে। এই ছবি তো শুধু চিকিৎসা-শিক্ষায় নয়, অপরাপর বিষয়ের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অভিযোগ নতুন নয়। যেমন যুক্ত হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে লাখে লাখে টাকা শাসকদলে ঘুষ দেওয়া শিক্ষকরা। স্মরণীয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে গণবিশ্বাস তুলে দেওয়ার দায় কিন্তু সরকারের, এখন যা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সঙ্গে করা হচ্ছে। সমাজের দুই আশা-ভরসার ক্ষেত্রকে গণশত্রু বানাতে মিডিয়াও কম সচেষ্ট নয়। অথচ এই দুর্নীতিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুই শিকারের নাম রাজকুমার রায় এবং অভয়া-তিলোত্তমা, একজন শিক্ষক যিনি দুর্নীতিমূলক নির্বাচন ব্যবস্থায় বাধা দিয়েছিলেন, আরেকজন চিকিৎসক পড়ুয়া যার মৃত্যুর সম্পর্কে ইতোমধ্যেই নানা দুর্নীতি জড়িত ব্যক্তিদের ভূমিকার কথা আর গোপন নয়। তবু মনে রাখতে হবে, এই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য থেকে শুরু করে এই গোটা দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থার প্রধান শিকার রাজ্যের দরিদ্র, অস্বচ্ছল, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষ। আর্বান-লিবারেল-মিডলক্লাস কিন্তু কল্যাণকামী রাষ্ট্রের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্যে সরাসরি বাঁচে না, সাধ্যমত বা সাধ্যাতীত চেষ্টা করেন বেসরকারি ক্ষেত্র থাকে এই পরিষেবা ক্রয়ের। কারণ সুচারুভাবে সমাজ মনে এটা গেঁথে দেওয়া গেছে যে, কল্যাণকামী রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য যে দায়িত্ব পালন করে তা খয়রাতি, সে স্বাস্থ্য হোক বা শিক্ষা হোক বা খাদ্য, এবং খয়রাতিতে পাওয়া সবকিছুর গুণগত মাণ খারাপ। তা যে নাগরিকের অর্জিত অধিকার তা আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া গেছে, রাষ্ট্র সেখানে মানের দিক থেকে আপোষ করতে পারে না। আমরা নাগরিকের জন্য ভাতাকে, ব্যবস্থার জন্য সাবসিডিকে ঘৃণ্য শব্দ হিসেবে চিনতে শিখেছি। কিন্তু কর্পোরেটের বেল-আউটকে নয়। এখানেই এই আর্বান-লিবারেল-মিডলক্লাসকে লড়িয়ে দেওয়া হয় আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে। আমরা তথাকথিত সেই শহুরে প্রগতিশীল-মধ্যবিত্ত যারা অনায়াসে আঙুল তুলে ফেলি রাষ্ট্রের ভাতা নেওয়া মানুষদের দিকে। অনায়াসে বলি ‘হাজার টাকার ভিক্ষা…’! ভাতা কল্যাণকামী-রাষ্ট্র দেয় নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে। রাষ্ট্র যে-কাজ দিতে পারেনি, যে রোজগারের উপায় দিতে পারেনি, যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারেনি, তার ক্ষতিপূরণ। এবং সেই টাকা কোনও নেতানেত্রী বা দলের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে আসে না। আসে রাজ্যের মানুষের ট্যাক্সের পয়সায়। এবং একটি সুস্থ অর্থনীতি থাকলে ও পাশাপাশি রাষ্ট্রের সুস্থ ও সুষ্ঠু শিক্ষা-খাদ্য-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাকলে মানুষ নিজেই কাজ করে তা অর্জন করে নিতে পারত। এটা বড়ো দ্বিচারিতা যে আমার শিক্ষার সাবসিডি পবিত্র, আমার মহার্ঘ্যভাতা পবিত্র অথচ পাশের নাগরিকের ‘ভাণ্ডার’ নাম্নী ভাতাটি অপবিত্র। অপবিত্র ভাতাটি নয়, অপবিত্র ওই ভাতার বিনিময়ে মানুষের জীবন জীবিকা বন্ধক রাখা। যা শাসক করছে। রবীন্দ্রনাথ লোকহিত প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘মহাজনকে সুদ দিতে হয়; সে-সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান; — সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।” যে দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থার কথা শোনা যাচ্ছে মিডিয়ায়, সিরিঞ্জসহ মেডিক্যাল বর্জ্যের দুর্নীতি থেকে নকল বা খারাপ মানের ওষুধের দুর্নীতি তার সরাসরি শিকার আমার রাজ্যের আশি শতাংশ মানুষ। তাঁরাই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তাঁরাই সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, সরকারি খাদ্য সুরক্ষার ওপর নির্ভরশীল — এবং স্পষ্টভাবে বলা দরকার সেটা কোনও অপ্রান্ধ তো নয়ই বরং সেটা তাঁদের অর্জিত অধিকার। কেবল সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি করে যারা পকেট ভরাচ্ছেন তাঁরা সরাসরি প্রতারণা করছেন এই আশি শতাংশ মানুষের সঙ্গে। আর তাঁদেরই দোহাই দিয়ে ওই আর্বান-লিবারেল-মিডলক্লাস চিহ্নিত করছেন তাঁদের শত্রু হিসেবে। এই রাষ্ট্রিক ভাবে সর্বাধিক প্রতারিতদের কাছে এই বাস্তবতা তুলে ধরার দায়ও কিন্তু সেই নাগরিক আন্দোলনকারীদের।
অর্থনীতির মাজাভাঙা এই ব্যবস্থার নির্মাণ করাই তো এই জন্য যে শাসক মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়! শিক্ষা ব্যবস্থার ভেঙে পড়ার যে গভীর হতাশাব্যঞ্জক প্রভাব, শিল্পহীনতার কারণে যে কর্মহীন যৌবন তাই তো শাসকের এই দুনীতি নিয়ন্ত্রিত লুঠ ও তোলাবাজি নির্ভর ব্যবস্থার শিরদাঁড়া। স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে যুক্ত হয় হুমকিরাজ, আজকে যাকে জুনিয়র চিকিৎসকরা চিহ্নিত করেছেন #থ্রেটকালচার বলে। সেটি ছাড়া এই দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা চলে না। যার শিকার অভয়া-তিলোত্তমা।
একজন কর্মরতা চিকিৎসক পড়ুয়া কার কর্মক্ষেত্র তথা শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ষিত ও খুন হয়েছে। অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে তত বিশাল, ব্যাপক ও অতিগভীর দুর্নীতির সংবাদ আসছে মাধ্যমে। তা কি কেবল পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সমাধান হবে! এ তো পুঁজির প্রাথমিক শর্তের গল্প, সর্বাধিক লাভের গল্প। তা দুর্নীতি ভিন্ন হবে কী করে! আরও বড়ো প্রশ্ন, তা অদলীয় রাজনীতির মাধ্যমেই বা হবে কী করে! সিভিল সোসাইটি তো গণতন্ত্রে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে ব্যবস্থা তার অভ্যন্তরীণ নয়!
ফলে অভয়া-তিলোত্তমা কোনও ব্যক্তিনাম নয়।
অভয়া-তিলোত্তমা কেবল দেশের আইন বাঁচানো প্রতীকায়িত নাম নয়।
অভয়া-তিলোত্তমা কেবল নিজ কর্মক্ষেত্র সরকারি হাসপাতালে ছত্রিশ-ঘণ্টা চিকিৎসা করার পর কোনও ধর্ষিত ও খুন হওয়া একত্রিশ বছরের চিকিৎসক তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উত্তর-স্নাতক ছাত্রী নয়।
তাই অভয়া-তিলোত্তমা আমার রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যস্থার নাম আজ।
অভয়া-তিলোত্তমা আমার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার নাম আজ।
অভয়া-তিলোত্তমা আমার রাজ্যের খাদ্য ব্যবস্থার নাম আজ।
অভয়া-তিলোত্তমা আমার রাজ্যের অর্থনীতির নাম আজ।
অভয়া-তিলোত্তমা আমার রাজ্যের শিক্ষাহীন, কাজের সুযোগহীন, পরিযায়ী অথবা নিখোঁজ অথবা পাচার হওয়া যৌবনের নাম আজ।
যারা প্রত্যেকে সরকারি ব্যবস্থাপনার অন্দরে যেখানে তাঁদের সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করার কথা সেখানেই ধর্ষিত ও নিহত হয়েছে। এবং সেই ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।
অভয়া-তিলোত্তমা একটি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক হত্যা। একটি সামগ্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রিক দুর্নীতি নির্ভর ব্যবস্থার শিকার। প্রত্যেক নাগরিকের যে সরকারি ব্যবস্থাপনার অন্দরে যেখানে সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করার কথা সেখানেই সেই নাগরিক জীবন ধর্ষিত ও নিহত হচ্ছে। এবং সেই ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভ ব্যবহৃত হচ্ছে। আইনসভা, পুলিস প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন এবং হয়ত বা গণতন্ত্রের আরও কিছু স্তম্ভ যার নাম করলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমার ওপর। গণতন্ত্রের সেই সমস্ত স্তম্ভ দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থার কম্প্রাদোর হয়ে উঠলে, নির্বাচন ‘রাজকুমাররায়’ হয়ে উঠলে সমাজ অ্যানার্কির দিকে যায়। অ্যানার্কি আবার নাগরিক আন্দোলন, গণ আন্দোলন, সিভিল সোসাইটির বিষয় নয়। তার সীমায় থাকে না। ফলে আমার নিশ্চুপ থাকাই ভালো।
এখানে একটা সোশ্যাল-মিডিয়া সম্মত স্মাইলি দিলে বোধহয় ভালো হত।
‘সকলেই আছে বুকজলে / কেউ জানে কেউ বা জানে না’
যাকগে…
হ্যাঁ একটি ব্যর্থ লেখা
সৌরভ চট্টোপাধ্যায়
জানো অনুরাধা- এখন বুঝতেই পারিনা কি লিখব। প্রাথমিক ভাবে কাজ করে লিখে কি হবে এমন একটা ভাবনা! লিখতে এসেছিলাম যখন তখন তো খেলতে এসেছিলাম, ধীরে ধীরে খেলাটা সিরিয়াস হল – বুঝলাম শৈলীর কথা, পরে আরো বুঝলাম নাশৈলীর কথা – তারপর একটা ঘোরতর চুপ! যেন চারপাশ বুঝেই চুপ করে যাওয়া। বহুল হৈ চৈ এর ভিতর নিজের বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া, হল্লা হচ্ছেই যখন – থাক এ ভিড়ে ঢুকব না আর। এ ঠিক সরে যাওয়া নয় – কেমন একটা ভাব – যে – অর্চনা তো লিখছে – বা দেবারতি – সোমঋতা! বেশ এখন না লিখলেও চলে, বা না লিখলেও চলে। তবে কি জানো অনুরাধা লেখা তো চলতেই থাকে ভিতরে। কাজ সেরে ফেরার পথে কোনোদিন ময়ূর দেখে ফেলি রাস্তায় বা বিস্তীর্ণ সর্ষের ক্ষেত দেখে কেমন যেন কিয়ারোস্তামির কথা মনে পড়ে, তখন লেখা চলে। কারোর সাথে ভাগ করতে না চাওয়া লেখা। এ যেন শিশুদের অভিমান! বা আত্মরতি! বা খুবই সংকীর্ণ অস্তিত্বপ্রখরতা। কিংবা
কানে আসে অনেক অনেক খবর, চোখে পড়ে – তবু চুপসজাগ একটা বাঁচা। তবু নালেখা। বইপত্র পড়ি, কিছু কাজের লেখা চলে – তবে যে লেখায় আমি ঠিকরে যায় তেমন লেখায় কেমন একটা অনীহা। আসলে বিশ্বাস একটা অনুশীলন। তুমি যদি ভেবে থাকো – তোমার এ ভাষা স্রোতের ভাষা নয়; তবে তোমায় দায়িত্ব নিতে হবে এ চর্চার। এসব যেন কথার কথা অনুরাধা। ছোটদের কাছে ভারী শরমের বাত।
অথচ অনুরাধা বেঁচেছি তো তুমুল অকূলে। তাহলে সেসব গেল কই? কোথায় গেল সেই ঘোরতর চোখ যা ফেলা ছিল স্বচ্ছ সপাট দুর্জনের দিকে! খানিক বিরতি নিই, ভাবি – সে সব আগুনের দিন আছে গভীর তারার ভেতর, জ্বলজ্বল করে একটু নিবিষ্ট হলে।
স্রেফ এক বাটি ছাই হয়ে গেছ অনুরাধা। বিস্তর তাড়ার ভিতর – সহজ খুনের ভেতর। যেন নামতার মত সরল! এরপর ঠিক হবে রেপ হবে কি না? হবে কি? না থাক! জল খাওয়ার মত সোজা – খুন দিয়েছি করে। গলা টিপে, রেটিনা চটকে দিয়েছি ঘৃণাভয় নিয়ে। তাহলে থাক। টেঁসে যাওয়া মাল লাগাবো আবার! ল্যাদ লাগে বড়! বড় হয়েছিল সে অল্প অল্প জেনে পৃথিবীর কথা, বাপ মা কে চিনেছিল – কিছু শুভার্থী জেনেছিল তাকে। মেধাবী ঋজুতা তার! অনেক অনেক দিন সে ভালোবাসা পায়ে পৃথিবীর কাছে হেঁটেছিল। গেয়েছিল গান- তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল রোগীটার দিকে। চল ছাড় বাঁড়া, ল্যাদ কাটা – কেলিয়ে রয়েছে মাল- লাগা তেড়ে। তোর হাতে পায়ে – বিরল জন্মদাগে, যেসব ভয়ের কথা -,আমাদের না পারা লেখা আছে- সব যাবে কেটে নিমেষে, ফ্রেশ হবি, মালঝোল খাবি, আকাশে চাইবি জলজল চোখে, যেমনটা চেয়েছিলি একদিন – তখনো বালক যায়নি মরে তোর ভিতর শহরে।
কখনো ওভাবে লিখতে পারিনি – যাকে বিষয়ধর্মী বলে। ফলে লেখার প্রথম থেকেই একটা নালেখা কাজ করে। আসলে লেখা তো স্রোতের মত, তুমি জানোই না কখন সে ঢেউ ওঠে, কোন অঘোরের মণিবিন্দু থেকে। যেমনটা জানত না সে – লোকটা – ফোন ধরেছিল সকালের দিকে, ওপারে মহিলা কন্ঠ বলে – কিরে বাঁড়া জানিস না! আর ঠিক দুটো কল পরে বলে দেব তোকে – তোর মেয়ে হয়তো বা টেঁসে গেছে, তুই শালা বুঝে নিবি – সুইসাইড এটা। আর কোনো কথা নয় – সত্ত্বর এসে যাবি – দূর থেকে বডি দেখে বা না দেখেও – কি হবে বডিসডি দেখে চোদু! তোরা বাঁড়া ঠুনকো চোদনা যারা অত মায়ামন দেখানো যায় না রে! এসে যাবি, বসে যাবি – স্যাটস্যাট হয়ে যাবে কাম – আমরা তুখোড় সব – জঞ্জাল সরাতে। একটু কষ্ট হবে! এমন তো কত হয়! চোখের সামনে তোর সব কাজ করে দেব। গাড়ি মালা এনে পিকনিক আকারে সেঁকে দেব আগুনে। বসে থাক বাঁড়া – ছাইটুকু তুলে দেব হাতে রাত্রি গড়ালে।
আমি এই দুটো মানুষের কথা ভেবেছি যখনই – আক্ষরিক অর্থেই চুপ হয়ে গেছি। আমি সে যন্ত্রণার কি ভাষা দেব! কি দেব উপশম! আমার দেশের জুডিসিয়ারির ওপর আমি বিশ্বাস হারিয়েছি। বিশ্বাস হারিয়েছি প্রশাসনের সমস্ত স্তর থেকে। দিল্লীর এক বাসস্টান্ড থেকে আচানাক এক সকালে কোবাড ঘান্ডিকে কিছু লোক তুলে নিয়ে যায় গাড়িতে। সালটা ২০০৯ এর দিকে। তারপর দশবছরের বিচারাধীন বন্দী কোবাড পরবর্তীতে শুনিয়েছেন কিভাবে একের পর এক নতুন কেসে তাকে কারাবন্দী করে রাখা হয়েছিল দশটা বছর। পাঠক ফ্র্যাকচারড ফ্রিডম বইটা পড়ে দেখতে পারেন।
এই ব্যর্থ লেখাটা যখন চলছে একই সময় সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং চলছে আমার ডাক্তারের। আমার স্বজনের – তোমার বন্ধুর।
দ্রোহকাল
ডাঃ ব্রতেশ
আমার ডাক্তারি পড়াশোনা এবং আজকের আমি হয়ে ওঠার যাত্রা অনেকখানি শুরু হয়েছিল আর জি কর থেকেই। ২০১১ সালে। সদ্য স্কুল পেরিয়ে মফস্সলের আস্তানা বদলে মুহূর্তে শহুরে হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। আর জি কর সে বাধ্যবাধকতার মুখে ঠেলেও দেয়নি কোনোদিন। সংস্কৃতি বুঝতে সেসময় বুঝি কলেজের ফেস্ট, ফাংশনে গান, নাটক ইত্যাদি। থ্রেটের যে এক কালচার বা সংস্কৃতি হয়, সে ধারণা তখনও ছিল না। তারপরের-টুকু ধীরে ধীরে এক বোকাসোকা খোকার প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার গল্প। এই পরিণত বয়সে এসে, আর জি কর থেকে বেশ দূরে শিশুদের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে করতেই ভীষণ অপরিণত, ঘৃণ্য এক সমাজের মুখোমুখি হতে হল। আমার সহকর্মী বন্ধুটি ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়েছেন, তাও আজ প্রায় পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত। আমারই এক অর্থে মাতৃভূমি, কিংবা alma mater-এর মাটিতে। ঘটনা যখন ঘটছে, তখনও ঠিক বুঝিনি কী হয়ে গেল, কিংবা কতটা? যখন বুঝলাম, তখন আমার চারপাশে শয়ে শয়ে মানুষ। যে মানুষেরা চিরকাল রান্নাঘরের ঝক্কি সামলে, পরিবারকে ধারণ করে গেলেন, যাঁদের জীবনের দীর্ঘ সময় কেটে গেল পিতৃতন্ত্রের সাথে আপসে; কিংবা যাঁরা রোজকার থোড়-বড়ি-খাড়া অভ্যাসে পেশা আর ঘরে পেষাই হচ্ছিলেন, তাঁরাও পথে নামলেন, স্লোগান দিলেন, বেছে নিলেন সংগ্রাম… তথাকথিত মাটির স্পর্শরহিত, ‘উঁচুতলা’র ডাক্তারদের আন্দোলন হয়ে উঠল সাধারণ ছাপোষা মানুষের গলার স্বর। তার সঙ্গে যুক্ত হল এই লড়াইয়ের কিছু যথোপযুক্ত, বিনীত, মেধাবী মুখ। আমরা সকলে ভাবতে সক্ষম হলাম, এই ছেলেমেয়েগুলো ‘আমাদেরই লোক’… অথচ, ডাক্তারদের আন্দোলন আগেও হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সমাজে ডাক্তারদের ‘পীঠ’স্থানে ‘বাবু’ কথাটি বসে এসেছে। আজও। কিন্তু যাদের প্রতিদিন টিভি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে, তাদের চলন, কথার শৈলী, বলার ধাঁচ, কোথাও গিয়ে এই এলিট সমাজবিচ্ছিন্নতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল, সম্ভবত ইতিহাসে প্রথমবার। কাতারে কাতারে মানুষ ‘আমাদের লোক’ হয়ে উঠলেন। আর তার সঙ্গে যোগ হল পতাকার রং বিসর্জন দেওয়ার ডাক। আসলে আমাদের নির্বিবাদী বাঙালি পরিবারে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সংশয় থেকে বরাবরই বিরোধিতা-বিরুদ্ধ এক সরলরৈখিক যাপনের প্রতি টান। রাজনীতির নেতারা পাঁক ঘাঁটেন, এবং সাধারণ মাছেভাতে বাঙালির কাজ তা থেকে শত হস্ত দূরে থাকা। তারপরেও এত মানুষ!
প্রাথমিকভাবে খুব অবাক লেগেছিল সবারই। এমনও হয়? নিজের কাজের জায়গায় এভাবে দুম করে মরে যাওয়া? অনেকেই ভেবেছিলেন আন্দোলন হয়, হওয়াই উচিত এবং কালের গর্ভে তা স্তিমিতও হয়। তাও হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে দিনের দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মানুষ মিছিলকে খুঁজে গেলেন। এমনকি শাসকের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে সর্বস্তরের মানুষ দাঁড়ালেন রাস্তায়। অনেক প্রবীণেরা পর্যন্ত স্মরণাতীত কালে এমনটা দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না। কিন্তু এত নির্নিমেষ ঢেউ এল কোত্থেকে? কেনই বা? খোদ আর জি করের বুকেই এর আগে (?আত্ম)হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তাহলে? আসলে, অনেকগুলো বিষয় একযোগে একই সাথে ঘটে গেছে বিগত ৯ই আগস্ট। আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার খারাপ লাগবে ভেবে আগাম ক্ষমা চেয়ে একদিন বললেন, এই মৃত্যু একটি মহিলা ডাক্তারের বলেই কি এই আলোড়ন পড়ল সমাজে? এ মৃত্যু কোনও নিচুতলার কর্মীর হলে?
আমি বললাম, কিংবা ডাক্তারি পড়ুয়া, কিন্তু পুরুষ হলে? অথবা মহিলাই, কিন্তু কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে না ঘটলে? অথবা কর্মরত অবস্থায় না হয়ে হাসপাতালের বাইরে, এমনকি তার চত্বরের মধ্যে হোস্টেল বা অন্য কোথাও যদি হত, তাহলে?
প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।
আসলে, এ এক আশ্চর্য সমাপতন।
আজ, থ্রেট কালচার সামনে আসছে, টেন্ডার দুর্নীতি সামনে আসছে, ডাক্তারি শিক্ষার নামে নম্বর বাড়িয়ে শাসকের ধামাধারী কিছু গর্দভ তৈরির কারখানার কথা জানতে পারছি– কিন্তু তারই সঙ্গে খুব অবাক হয়ে দেখছি, এই ঘোরতর অন্যায়কে জাস্টিফাই করার চেষ্টাকে। যেদিন এ ঘটনা ঘটেছিল, তখন মনে হয়েছিল, দলমত নির্বিশেষে এমন অন্যায়কে সকলে সর্বতোভাবে ঘৃণা করবেন। হল উলটোটা। অন্য অনেকের মতোই খুব অবাক হলাম। তবে তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম, এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে, বহু মানুষের বেপরোয়া গলা তোলা দেখে। ১৪ই আগস্ট নৈহাটিতে যে জনজোয়ার দেখেছিলাম, সেই ৮-১০ হাজার মানুষের ভিড়ে ৮-১০ জন ডাক্তারও ছিলেন কি না সন্দেহ। অর্থাৎ, মানুষ পেশা ভুলে, সামাজিক হায়ারার্কি ভেঙে, শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, অভয়ার চোখের রক্তকেই আঁধার রাতের মশাল করে নিল। আসলে আমরা বুঝছি, আমাদের সমাজে এই জঘন্য অপরাধের সমর্থনকারী কিছু ক্ষমতাশালী মানুষও রয়েছে। তাই ‘আমার ঘরের মেয়ের নিরাপত্তা কোথায়’, এই প্রশ্নের উত্তর না মেলার আতঙ্ক যতটা সত্যি, তেমনই এত চূড়ান্ত পৈশাচিকতাকে র্যাশানালাইজ এবং এই ভয়কে ক্যাপিটালাইজ করার মতো আমার ‘সমাজ’-টাও ততোধিক ভয়ংকর সত্য। প্রথম সত্য আমার-আপনার কাছে অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল, কিন্তু এই দ্বিতীয় সত্য খানিক নতুন… কারণ এত তীব্র অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমার সমাজ কীভাবে যায়, এবং রিয়্যাক্ট করে, তা নির্ভয়ার ঘটনার পর সাম্প্রতিক অতীতে আর দেখা যায়নি।
এরপরে আরও ভয় ধরায় শাসক দলের নেতার কোনও এক মেডিকেল কলেজ ঘেরাও করে ‘দেখে’ নেওয়ার হুমকি, কিংবা সাগর দত্তের মতো শহরের উপকণ্ঠে থাকা হাসপাতালে মহিলা ডাক্তার নিগ্রহের মতো ঘটনা। এত কিছুর পরেও! তাহলে কি আমাদের সমস্ত অপরাধ এবং অপরাধমনস্কতাকে, সমস্ত ধর্ষণ এবং ধর্ষকাম মানসিকতাকে র্যাশানালাইজ করতে হবে? তাঁদের জীবন, সম্মান, এমনকি সুরক্ষার কোনও অর্থ এ দেশে নেই, এইটে মেনে নিয়েই কি ডাক্তাররা কাজে ফিরবেন?
এই কাজে ফেরা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত সমাজ, এমনকি ডাক্তাররা নিজেরাও। ডাক্তারদের হাতে মানুষ বাঁচানোর জাদুকাঠি আছে–এই ধারণা থেকেই একটা সময়, ডাক্তারি পড়তে আসত মেধাবী পড়ুয়ারা। কালে কালে মানুষ বুঝল, ডাক্তার হলে বেশ অর্থ লাভ করা যায়… অর্থাৎ, নিরাপত্তা। সেই গ্ল্যামারের টানে ধীরে ধীরে ডাক্তারি পড়তে আসার ধুম বাড়ল। যারা গ্ল্যামার বা অর্থ চেনে, তাদের মেধার বা অধ্যবসায়-এর প্রতি খুব বেশি আনুগত্য থাকে না। ফলে, চলে এল অল্টারনেট মাধ্যম। এই আর্থিক নিরাপত্তার একটি আজীবনের প্যাকেজ কেনার জন্য সেই অর্থেরই দ্বারস্থ হওয়া। বাড়তে থাকল, যেনতেনপ্রকারেন, এ দেশে বা বিদেশে অর্থের বিনিময়ে সন্তানকে ডাক্তারি পড়িয়ে নেওয়ার তথা নিজের সামাজিক স্ট্যাটাস বাড়িয়ে নেওয়ার এক মারাত্মক আত্মঘাতী প্রবণতা। এরই ফসল আজকের কিছু অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ডাক্তাররা, যারা কিছুদিন পর থেকেই আমার-আপনার চিকিৎসা করবে বা ইতিমধ্যেই করছে। ডাক্তারি শিক্ষায় গলদ থাকলে তার খেসারত যেহেতু প্রাণ দিয়ে দিতে হয়, কাজেই কপাল খারাপ থাকলে আমার-আপনার শেষ মুহূর্তগুলোর হেফাজত এই অকর্মণ্য অর্বাচীনদের হাতেই সঁপে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত মেধাবী? তাঁদের ডাক্তারি শিক্ষার চিত্রটা ঠিক কেমন? সেখানেও অজস্র ফাঁকফোকর। নতুন শিক্ষক-চিকিৎসক নিয়োগ নেই, থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে ধামাধারীদেরই দৌরাত্ম্য। ফলে, যাঁরা এই শিক্ষা দেবেন, তাঁরাও কি ঠিক ঠিক শিক্ষিত? যোগ্য এই কাজে? দেখার কেউ নেই। ফলত, এক নতুন চিকিৎসক শ্রেণি তৈরি হবে বা হচ্ছে, যাদের সঠিক দিশা দেখানোর মানুষের তথা প্রকৃত শিক্ষকের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। এমতাবস্থায় সিস্টেমের অভ্যন্তরের এই পচন, ধীরে ধীরে বেআব্রু হচ্ছে– এইটে আরও অনেক কিছুর সাথে এই আন্দোলনের প্রাপ্তি।
চিরকালই ডাক্তারদের আন্দোলনের বা প্রতিরোধের ভাষা হয়ে উঠেছে কর্মবিরতি। কিছু ক্ষেত্রে অনশনও। জরুরি পরিষেবা বলেই, এক্ষেত্রে কর্মবিরতি ঘটলে প্রশাসনকে খানিক নড়েচড়ে বসতে হয়, অন্য কোনও ধরনা-অবস্থানের মতো এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সেই ভাবনা থেকেই, সমস্যার সুরাহা হবে এই আশায় কর্মবিরতির পথ বেছে নেন আন্দোলনকারী ডাক্তারেরা। তার চেয়েও বড় কথা, কেউ যদি নিজের কর্মক্ষেত্রেই বিপন্ন বোধ করেন, তবে সেখানে ফিরতে ত্রস্ত, আশঙ্কিত হওয়াও তো তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তবে, মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেহেতু পার্ট-টাইম জব হতে পারে না, কাজেই কর্মবিরতিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু যে মানুষগুলো নিজের নিরাপত্তা নিয়েই ভীত, তাঁদের কি অন্য মানুষকে সুস্থ করে তোলার মতো স্থৈর্য থাকা সম্ভব? যেহেতু কথাটা আপেক্ষিক, কাজেই ভিন্নমত আসছে। আসবেও।
এর পরিণতি কী হবে জানা নেই, তবে যতটা পথ পেরোনো গেল, তাও কি কম?
মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা সমস্ত না-পারাগুলোতে প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। সে লালবাজার হোক কিংবা স্বাস্থ্যভবন। আমরা একে একে চিনতে শিখলাম প্রতিটি সেক্টরে থাকা সন্দীপ ঘোষদের। বেরিয়ে এল সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকা থ্রেট কালচারের কাহিনি। অনেকের চরিত্রেই খুঁজে পাওয়া গেল হারানো মেরুদণ্ডখানি, কেউ কেউ আবার চূড়ান্ত নীরবতাকে আশ্রয় করে দর্শক রয়ে গেলেন। আসলে অনেক মানুষ চেনা হয়ে গেল এই অল্প কয়েকদিনে।
“মেয়েটার বড়ো জোর রে!” স্বাস্থ্যভবনের জমায়েত-অবস্থান চাক্ষুষ করে, বলেছিল মা। সত্যিই, এত কিছুর পরেও যদি আর কিছু না হয়, তবু এই জোরকে কি কখনও অস্বীকার করতে পারব আমরা?