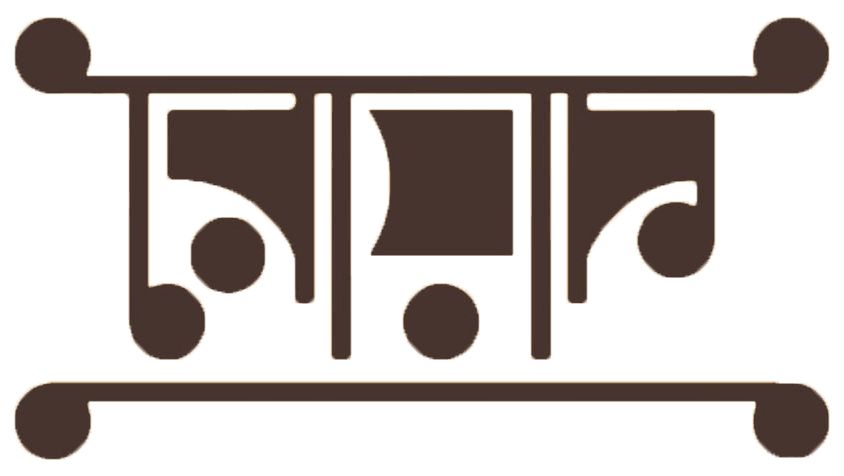চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা – গদ্য
হারানো বুদবুদ
রিয়া চক্রবর্তী
আমার একটা মামাবাড়ি ছিলো। আহ্লাদ ছিলো। কালো বেড়াল ছিলো। বিকেলবেলা বোঁটাওলা মস্ত বেগুনি… একাত্তরে আসা ফুলমাসি… তার জ্যাঠার বিরাট সংসার… শোনপাপড়ি-বুড়ো… বড় বড় ঘরের এখানে সেখানে সিমেন্ট ওঠা মেঝের ভাঁজে নানান আশ্চর্য গল্প…
পুরোনো রাজবাড়িতে কাদের যেন জীর্ণ কাপড় শুকাতো। রাতের বেলা শেয়াল ডাকতো। জং ধরা লোহার সিঁড়ি বেয়ে সারা রাত ওঠানামা করতো কারা। সীম-পুকুরের জলে মায়ের ছেলেবেলা এপার ওপার করতো। দেওয়াল জুড়ে জয়দেব… দেহিপদপল্লবমুদারম্… রাধার কলসির নীচে হাত রাখা কৃষ্ণ ঠাকুর… অন্ধ বিল্বমঙ্গল… ডায়েরির প্রথম পাতায় লেখা – ‘কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব’…
এক বিকেল এসে মুছে নিল সব। পড়ে রইলো ক্যারাম বোর্ড… চাইনিজ চেকার… পৌষমেলার পুতুল… ভূত এসে বসা গাব গাছ… শেষে একদিন গোপাল ঠাকুরও চলে গেলো কোথাও… সঙ্গে নিয়ে গেল ন্যাড়াপোড়া, রঙিন চুড়োওলা বয়াম ভর্তি মঠ…
আমি এখন মাঝে মাঝেই টিকিট কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু মনে করতে পারি না কোথাকার টিকিট কাটবো… ঘন্টার পর ঘন্টা স্টেশনে বসে ঘোষণা শুনি নানা গন্তব্যের… মামাবাড়ির ট্রেন আসে না আর কখনও।
মন্থরতার গদ্য
শতানীক রায়
বছরের শেষ দিনে ক্লান্তি নয়, শুধু মন্থরতা অনুভব করছি। ধীরে হয়ে যাওয়ার গল্প ভাবি। ভাবি আর ভাবি। ভাবি একটু। বলি কি? ভাবনা খানিকটা আরও চলে। দিনের শেষ কি? বছর শেষ অনেকটা দিনের শেষ। শেষ হতে হতে ভাবি। গল্পটা কি বলা হয়? ভাবা হয়। ভাবা ধীরে হয়। ধীর বিষয়টা আরও ধীরে ধীরে চলে। গল্পটা শুরু হয় না তখনও। ঘুমিয়ে পড়ার গল্পটা খানিকটা বেঁচে থাকার মতো। দিন ছোটো এমন অবস্থায় রাত আরও ধীরে গল্প হতে থাকে। গল্পটা আরও খানিকটা ভাবা হয়। এই এতদিন সব জেনে-বুঝে কত কী ভেবে গল্পটা আর হয় না। রাতবিরেতে ভাবা হয়।
কিছুদিন আগে ভাবা হয়। ভাবনাটা খানিকটা কবিতা হয়ে যায়। ভাবনাটা টুকরো বাক্য হয়। কাছে গিয়ে দেখলে যেমন সব অসুন্দর। সেইসব বাক্য কবিতার মতো দেখতে হয়। কবিতার মতো দেখতে বাক্যগুলো আর কথা বলে না। অনুভূতির শরীর হয়ে ওঠে না। বাক্যগুলো ধীরে কোথাও ঝুলে থাকে। দোলনটাও সেসবের ধীরে। মন্থর ট্রেনের থেকেও ধীরে। মন্থর শামুকটার কথা ভুলিনি এখনও। দাদুরবাড়ির পুরোনো ঘরে বাথরুমে উঠে আসা শামুকটা। পুরোনো শামুকটা এত বছরে আরও ধীরে হয়েছে। সেই শামুকটার মতো। চলে যাওয়ার মন্থর দাগের মতো বাক্যগুলো মনে পড়ে। মনে পড়ার অবস্থা থেকে কিছু বাক্য আসে। সেসব শুধু মন্থর দাগ। নরম। আবার কিছুটা পাথরও। অসামঞ্জস্যে ভরা থাকে। আর বছর শেষের দিন শব্দের মন্থরতা থাকে।
*
১) ওগো রক্তপ্রবাহের রক্ত, তুমি কার?
২) যখন শেষ রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্না থাকে আর কিছু মানুষ জেগে থাকে। তারা আগুন ঘিরে জ্যোৎস্নাযাপন করে। গান করে। কখনো গান পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করে। থামে। আবার গান ধরে।
৩) কাকে প্রশ্ন করব আজ— এই জরা কার? ওগো জরা তুমি কার? যেদিন আর বৃষ্টি হয় না। খরাও হয় না, সেদিন মেষশাবকের জন্ম হয়
৪) আর আস্তেধীরে কথা হয় মায়ের সঙ্গে। অনেক ভোরে উঠেছিল বলে মায়ের শরীরে দিনের টান দেখা দিয়েছে।
৫) আর সেসব বলা হয় না। অনেক চুপ। তারপর যাওয়া আসা। ধীর স্থির। মৃত্যুর খবর না। এখন শুধু রাত হওয়ার গল্প। ঘরে ঘরে মানুষের ঘুম আরও একা হয়। একা একটা গান টো টো করে মাঝরাত পর্যন্ত। আর এসব দিনে শেয়ালেরা খেলা করে। মাছের ঘুম আসে আরও
*
বছরের শেষ দিন কাটিয়ে উঠে মনে হচ্ছে। এরকম প্রতি বছর কি মনে হয়। প্রতিটা বছরের স্মৃতি কেন ধরে রাখা হয়নি। কেন নিছকই ওপরের পাঁচটি অনুভূতি কবিতা হয়ে ওঠেনি। আমার প্রশ্নগুলো আসলে প্রশ্নের মতো। আমার উত্তরগুলো আরও উত্তরের মতো। প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে দেখি উত্তরগুলো মন্থর। আরও মন্থরতম উত্তর দিয়ে গাঁথা এইসব দ্রুত উদিত প্রশ্নগুলো। যা প্রশ্নের মতো একটা কিছু ধারণ করে চলে। আমি আজ এরকম একটা মন্থরতম মিনিট মন্থরতম ঘণ্টা আর কত সহ্য করে উঠতে পারব জানি না। কেন রাগ ঘৃণায় দীর্ঘ আক্রান্ত হতে পারি না— কেন দীর্ঘতা আমাকে লম্বা করে না। আমার এই প্রশ্নের মতো অবস্থান কতদিন থাকবে এও জানি না। তবে এই অবস্থা দিয়ে যেতে চাই। একধরনের না-হওয়া অবস্থা। এইটা আমি জানতে পেরেছি অভ্যেস থেকে। অভ্যেসের শরীরকে ঘৃণাও করতেও পারছি না। আমার একসময়ের ঘৃণা নিয়ে আবার উজ্জীবিত হতে পারছি না। আমাকে একটা দীর্ঘ প্রশ্নের মতো অবস্থায় কতক্ষণ কতদিন কতটা কাল থাকতে হবে এও জানি না।
*
আজকের মতো একটি সন্ধ্যাকে আরও আস্তে করে দেওয়া যায়। সামান্য কিছু হাঁটা। কথার ফুল এদিক ওদিক। এমন একটি সন্ধ্যার খোঁজে কেউ আসে না। পথে ফিরতি পশু এই কালো ম্লান আলোর পথে স্লথ হয়ে যায়। পথিকের সংশয়ের ভিতর সবকিছু টানতে টানতে কীভাবে একটি সমগ্রসন্ধ্যা নিশ্চুপ। মানুষের ভিতর চুপচাপ এমন একটি সন্ধ্যা। এমন একটি সময় যখন গাছের পাতাও ধীর স্থির পড়ে। মাটিও তখন বেশ শান্ত মন্থরতা ভোগ করে। সবকিছু আগের মতো হতে না-চাওয়া বিকেল সন্ধ্যা কিছুই বলে না। একরকম ফিরতে না পারার আফশোস না, ক্লান্তিও না, একধরনের ধীর গতি সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। কোথাও একটা আকাঙ্ক্ষা কেবল শরীর ধারণ করে থাকে। সারাটা সন্ধ্যা মন্থরতা গুনতে থাকে। এই রোগ থেকে পাখি পশু পিঁপড়ে মানুষ এত নীচু হতে গিয়ে ক্লান্ত স্লথ দেখায়। কেউ কোথাও যেতে পারে না। এমন সন্ধ্যা বহুদিনের। এমন বহুদিন বহুবছরের কাছে ঋণী। এমন একটা বড়ো ধীর অবস্থা ভালো করে কিছু দেখতে দেয় না। ভাবতে দেয় না। এরকম কি প্রথম ঘটছে? এমনটা কি বহুদিনের রোগ? এতটা দিন ব্যাপারটা মন্থরতার মতো ছিল। এখন যে আরও কিছু। আরও অদ্ভুত দিন আগে কি কখনো এইসব জীবজন্তু উদ্ভিদ দেখেছে? এমনতর অবস্থা কোথাও যেতে দেয় না। আক্রান্ত পথে বেরিয়ে মানুষ চলতে পারে না। পথ তখন বালির মতো অনুভূতিহীন। পৃথিবীর মতো ম্লান। আর সদাজাগ্রত গাছের মতো পূর্ণ। পথই বিরোধ করে। পথই না কি কোথাও এগোতে ভুল করে। পথিক কোথাও যেতে পারে না। এমন একটা সময় যা কিছু থাকে যা কিছু ঘটে যা কিছু ভেঙে যায়— দিনটা এভাবে ভেঙে গিয়ে গৌরী রাগে মেশে।
*
দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার মধ্যে কী যে আছে। এসব ভাবি। শীতের রাত যেমন হয়, জবুথবু, একরোখা, কোনো ফিসফাস না করা রাত। এমন কিছু রাতের মধ্যে পুরোনো কিছু গল্প ফিরে আসে। সেসব তখন আর স্মৃতি উপাদেয় না। খুব বেশি দিন, অনেক দিন বেঁচে থাকা হয়ে গেলে তখন আর স্মৃতি উপাদেয় হয় না। তখন সেইসব মানুষ, তখন কিছু কিছু সময় স্মৃতির মধ্যে গলে পচে গিয়ে আর কিছু থাকে না। খুব বেশিদিন কল্পনাতেও থাকা যায় না। কল্পনার অতি রিক্ত অবস্থা কল্পনাকে ভেঙে দেয়। কল্পনা শরীর থেকে লুপ্ত হয়। আবার থেকেও যায় ধীরে ধীরে অনুভব করা রক্তে। যে-রক্ত প্রতিনিয়ত চলাফেরা করতে গিয়ে কখনো কোনো শীতের রাতে ধীরে হয়ে পড়ে। কেউই কি আচ্ছন্ন অবস্থায় পিছন ফিরে দ্যাখে না। এমন স্মৃতিসন্ত্রাস এমন কল্পনাক্লান্ত অবস্থায় বার বার যাই। বুঝতে পারি এই বুঝি আজকের রাতটাই এমন ধীরে হয়ে যাবে। তখন এত ধীর রাত অজস্র স্থির রাত্রির গল্পটা পেড়ে আনবে। এমনটা কি আজও ঘটবে!
*
কখনো কখনো সেইসব চলে যাওয়া মুহূর্তের স্মৃতি মনে করতে করতে অনেকটা সময় পার হয়ে যায়। সময় পার হওয়ার যন্ত্রণা কাজ করে না। টের পাই সময় পার হওয়ার বোধ না হওয়ার বোধে যেটুকু কষ্ট। শ্রম যেটুকু। কিছু কথা বলতে না পারার ব্যথা। আমি যে কেন যন্ত্রণা শব্দটা দিয়েই যন্ত্রণাসম বোধকে তুলে ধরতে চাইছি। আর এই ধরা ছোঁয়ার বাইরে কী যে আছে, কী যে ছিল। যন্ত্রণার ধীর অবস্থা যা অবস্থাকে ধীরে করে দেয়। জল যেভাবে জল করে দেয় সময়কে। আরও ধীরে তখন আধো কালো দিনে পার হয়ে যেতে চলমানতার এই মন্থরতা, এইরকম সময়। আমি কাউকে আমার গতিময়তা উপহার দিতে ভুল করি। ভুল করে প্রবেশ করি। মুখের কথা যখন আর মুখের থাকে না। দৃশ্য আর দৃশ্য থাকে না। কথা বলা থেকে কত কী। কত কিছু দৃশ্যহীন হয়। দৃশ্যে থাকে না যা। এভাবে দৃশ্যের সঙ্গে যোগাযোগহীন অবস্থা। যেহেতু অবস্থাকে এখন আর ধরা যাচ্ছে না। অতি ধীরে হওয়া জীবনের ভিতর আবেগই-বা কতটুকু। আমি ক্রমাগত কথা বলে যাই। হাঁচি। কাঁদি। চলাফেরা করি। গৃহপথে ফেরার চেষ্টা করি।
*
দিনটা দীর্ঘ হতে পারত কিন্তু হল না। এতে চলাটা দীর্ঘ হয় না। কিছুটা থেমে থেমে চলেও দিনটা দীর্ঘ হল না। কেন দীর্ঘ হল না এর উত্তর হাঁটার চলনের ওপর কি খুব নির্ভর করে, এরকম প্রশ্ন থেকে বিরত থেকে আজ সামান্য একটু এগিয়ে যাওয়া যায়। যখন খুব শান্ত হয়ে আসে দিন। আমার সারাটা দিন যখন একটা ঘরের মধ্যে কাটতে থাকে আর হুহু করে রাত হয়। সারাদিনে বহু বহু সময় স্তব্ধতা থাকলেও আমার এই শরীর স্তব্ধতা পায় না। পায় না খানিকক্ষণের নিশ্চিন্ত ধীর অবস্থা। এক-একটা দিন যেমন কাটে একটা সাদা পৃষ্ঠা ভরানোর মধ্যে। সেই সাদা পৃষ্ঠা অন্তহীন কিছুকে বহন করে যেন। যে-অন্তহীনের টানাপোড়েন আছে। দীর্ঘ অবসর আছে। আছে স্মৃতিটান। অথচ এমন দিনে, আজকের মতো দিনগুলিতে স্মৃতির চোরাটান যখন অনুভূত হয় না কিছুই হয় না যখন। কীভাবে দিনের পর দিন সাদা পৃষ্ঠার দিন কাটে, স্মৃতির টান অনুভব না করা দিন। যেন এখুনি চেয়ার ছেড়ে উঠে যাওয়া মানুষটা সেই চেয়ারের স্থিরচিত্রে ফিরতে পারে না আর।
“তবুও তো চাহিয়া আছো তুমি। দৃষ্টি গিয়াছে তোমার। তোমার ভিতরের সবকিছু বোধহয় পাথর হইয়া গিয়াছে তবুও চেষ্টা চালাইতেছ অন্ধকারে যদি কিছু দেখা যায়।
কারণ নিজেকে তুমি বড়ো ভালোবাসো— নিজের স্মৃতিকে— তুমি আমি আমরা সবাই নিজেকে বড়ো ভালোবাসি— সম্পূর্ণ শেষ হইতে বড় ভয় পাই। বাঁচিয়া থাকিবার দৈনন্দিন জ্বালা লইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে বড়ো ভালোবাসি। এই কথা স্পষ্টভাবে বলে না কেউ।” (‘মৃতকল্প’, ৬ সংখ্যক পরিচ্ছেদ, দিবাকর ভট্টাচার্য)
একসময় আমার অবস্থা একটি মন্থর দিনে স্মৃতিহীন সাদা পৃষ্ঠায় ভরা মানুষের মতো হয়। দিবাকর ভট্টাচার্যর উপন্যাসের এই অংশও একইরকম কথা বলে। একটি অন্ধকার অবস্থা। মন্থর অবস্থা। একটি দাগের মতো।
*
“আইল শান্ত সন্ধ্যা…” গানে কেন রবীন্দ্রনাথ একটা সন্ধ্যাকে এত টেনে লম্বা করলেন? গানটা যেহেতু আজ সন্ধ্যা থেকে টানা শুনছি। হয়তো ৩০ বা ৪০ বা তার চেয়েও বেশি বার শুনেছি। শেষ না হওয়া একটি মন্থর চলার কথা মনে পড়ে যায়। কেন একটানা হেঁটে চলা শরীরের মধ্যে ক্লান্তি আসে না। কেন আসে না কোনো সুপ্তি। বা এ হেন শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে একটানা ক্লান্ত না হওয়া মন্থরতা। এভাবে একটা গান এত কিছু করে দিতে পারে কখনো কি ভেবেছি। ভেবেছি বলেই হয়তো আজ এত ধীরে ভাবতে পারছি। বা ভাবিনি বলেই এত শান্ত অনুভূতি চারপাশকে মন্থর করতে পারছে না। অর্থাৎ একটি শরীর আপনাআপনি নরম না-হওয়া অবস্থা থেকে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলছে। এরকম একটা মন্থরতম মিনিট বা ঘণ্টা অতিক্রম করতে গিয়ে হঠাৎই নিজেই একরকম সময়ের শরীর হয়ে উঠছে। এ-শরীর ধীরে কিছু কথা বলে। কিছু কথা বলতে চায়। এখন আমি কথা বলতে না চাইলেও আমার গতি কথা বলবে। আমার গতি এতই মন্থর যে আমি নিজে অতটা শান্ত ও ধীরে না হলে নিজের মন্থর গতি বুঝতে পারব না। আর এত শান্ত মন্থরতা অনুভব করার মধ্যে আর কিছু থাকছে না। কেবল সময় নিয়ে ভাবনা। খানিকটা আত্মকেন্দ্রিকতা। নরম হওয়া শরীর হাঁটা চলার ভিতর কীভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে আর নিজেরই চলার নিশান বলতে একটি সরু পথের মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা। যেখানে শুধু শরীরটা যেতে চায়।
*
এই কোনো কোনো সময় ধূসর মনে হয়। ঊষরও মনে হতে পারে। বা সফেদ সাদা। প্রান্তরটা এরকমই। কল্পনার প্রান্তর এখন এরকম। আজ অন্যরকম হতে পারত কিন্তু হল না। সকালে ওঠা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত। এত ধীরে যে হয়ে গেছি। সন্দেহ হচ্ছে অলস ভেবে নিজেকে। একটি অলস শরীর আমি। হয়তো আজকের দিনে আমার এমনতর শরীর গুটিয়ে আসছে। তারপর সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই অবস্থা, মনে হল, আমি অলস নই। ক্লান্ত নই। অথচ কেন এত ধীর? আমি সারাটা দুপুর অনুভব করলাম একটি গল্পপাঠের মধ্যে দিয়ে। আমি গল্প যত না অনুভব করেছি তার চেয়ে দুপুর, এই হতভাগা দুপুর কীভাবে কীভাবে যেন নরম খরখরে হয়ে এল। এইসব কল্পনায় দিন যে এত আছে কখনো ভাবিনি। যদি সারাটা দুপুর আমি কাজহীন নিদ্রাহীন শুধু বসে বসে ঊষর স্মৃতি ভাবতাম, এমন দুপুরগুলো অযথা কেন আসে, এত মন্থর কেন, এত দাগে ভরা কেন!
*
উপশম বলতে তো কেবল
বিস্মৃতিকেই বুঝি
এ’ছাড়া যন্ত্রণার আর কী উপায়?
— আলেজান্দ্রাকে, সব্যসাচী সান্যাল
কিছুতেই একটা দীর্ঘ দিনকে বাগে আনতে পারছি না তাই অপেক্ষা করছি, জানছি, বুঝছি, ব্যথাকে উপশম পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। আর উপশম পর্যন্ত কোনো পথ আমি জানি না। এই এত রাতে মনে পড়ে যাচ্ছে কোনো রূপকথা। একসময় প্রতিদিন একটি শিশুর কাছে যেসব মাছেরা দ্যাখা করতে আসত একটা দিন আসে সেদিন থেকে কোনো মাছেরা আর আসে না। আমি অপেক্ষা আর উপশম, এর মধ্যে যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছি। এই সময় তাই এখন দীর্ঘ। এতটা দীর্ঘ, স্লথ।
*
ঠিক কোনো একদিন কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে পুরো দিনটা পুরো মাসটা পুরো বছরটা বা আস্ত জীবনই হয়তো ছোটো হয়ে গুটিয়ে আসতে পারে। ধীর পায়ে। ধীর চলনে জীবনটা তখন মুহূর্তে বন্দি হয়েও মুক্ত। তখন বন্দিমুক্তি মানে কি শুধুই রিকল করা? তা নয়। আস্ত জীবনকে বন্দিমুক্তির মতো খোলার প্রচেষ্টা মোটেই সহজ না। এভাবে সময়টাকে বোঝা যায় না অনুভব করা যায় না। নিঃসাড় অনুভূতি তখন অনুভূতি কি না সন্দেহ হয়। সন্দেহের তির, সন্দেহ কী বস্তু টের পাওয়া যায় না। জীবন একরকম জটিল সময়ে আবদ্ধ। একাধারে তিনটা কালের বাধা অতিক্রম করে এই যে একটু দেখে নেওয়া কোনো একটি মুহূর্তে। সেই তখন সেই মুহূর্তে আবদ্ধ সময় কি মুক্তি পায়? হয়তো কিছুই হয় না। শুধু হেঁটে চলে যাওয়া অনুভব করি একরকম মন্থর অবস্থা দিয়ে। একটা আবছা অবস্থা। আবছা শরীর। আবছা সময়। আবছা রং।
*
এই যে রোমন্থনের প্রক্রিয়াটা কি আমাকে আরও ধীরে করে দিচ্ছে? বালির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথহাঁটার কোনো অভিমুখ নেই। একটি অভিমুখহীন হাঁটার ভিতর দিয়ে পা ফেলারও কোনো অভিমুখ থাকে না। সেই একদম শিশুবেলা থেকে ছোটোবেলা কিশোরবেলা এইসবেতে সেই যে সামনে পেছনে স্মৃতির টান। প্রতিদিন অজস্র হই আমি আর এই অজস্র নিয়ে আমার পথ চলা। আর চলাপথটা বার বার দেখা, তাকিয়ে থাকা আলো পর্যন্ত। আলো পর্যন্তই এইসব তারপর আবার দিন গুনতে বসা। আবার কোনো কোনো দিন “আয় তবে সহচরী…” গান হয়ে ওঠা। এই সামনে পেছনে আসা যাওয়া। তিনকাল দিয়ে। এই তিনকালই সত্য। আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত আছে। অতীতগুলো যখন একই বর্তমান তৈরি করেছে তাহলে বর্তমানগুলো একই ভবিষ্যৎ তৈরি করবে জানি। একটি আলো অন্ধকারে মোড়া ঋতুচক্রে পিশে যাওয়া শরীর যে ক্রমাগত এখন বালির ওপর দিয়ে দীর্ঘ হাঁটা দীর্ঘ পথের ধীর বোধ হওয়া। উভয়েই আমরা একে-অপরকে বুঝতে পারি। উভয়েই মন্থরতা বুঝতে পারি। উভয়েই অপেক্ষা করি “হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিব ঘিরি ঘিরি গাহিব গান”… উভয়েই আমরা পুনরায় মন্থর হই।
THE IDEA OF HOME
SHARMINDRILA
All our lives, we chase a sense of belonging. There’s something deeply comforting about knowing you belong to someone—even if it’s just a part of you. A sliver of your heart, a fragment of your existence tied to another. I was no different. But after many autumns and countless quiet heartbreaks, I’ve come to realise: I belong more to places than people. To moments, memories, and time itself.
People, more often than not, have let me down. Some shocked me, some amused me, and a very few broke me. These days, I don’t feel tethered to any person—not even family or friends. But places? Oh, how they’ve held me! Known and unknown, familiar and strange. Places I visited once, or never returned to. Places that loved me back, quietly and without condition.
Three decades in, my heart still clings to a city I left long ago. Or maybe I never truly left. Maybe it never let me go. That chaotic, nerve-wracking city I once called home—where everything stays the same, yet nothing feels familiar. A paradox I’ve stood in the middle of, often at crossroads, unsure which way to turn. So I waited. Long enough to lose my way.
Whether it’s life or a place, I keep waiting. That’s been my story—waiting for my ever-changing Godot. Waiting to return to an address that doesn’t expect me, a building that’s gone, an alley forgotten, a neighbourhood with no familiar faces, a library that’s shut, a house that feels cold. I wait—for a message that never came, a call that will never come, a festival that’s now more an exhibition of luxury than joy. I wait to feel at home again, even in places I can still physically go back to.
So what defines us? What do we really crave? What is home, anyway? Is it a pair of hands that hold you when you’re falling apart? Eyes that never stop searching for you in a crowd? A smile that blooms when you step out of the airport? A gentle nudge asking you to stay a little longer while you open the car door?
Home is also absence; the road I didn’t take, though I wanted to. A dusty bookshop trying to survive the digital boom. A gramophone store losing to streaming apps. A quiet museum and a cemetery tucked away in the city’s chaos. Home is a person I couldn’t hold on to, a voice I long for before I sleep and after waking. The list goes on.
As I wait to be homebound, I’ve learned that some people will always live in my heart, but not necessarily in my life. You lose countless homes along the way. You ache, and eventually, the pain dulls. But the idea of home lingers—like an old tune in a Durga Puja pandal, twilight at the ghats, a faded photo, a torn school uniform, a dried flower, a moment frozen in memory. People leave, memories stay. And so do places – in its quiet growing onto you. Somewhere between remembering and forgetting, between memory and haunting, still searching for a way back home.
Best Regards,
Sharmindrila
চিঠি- ঘরে ফেরার গান
নাম – নাজমীন মন্ডল
প্রিয় মা,
জানি তুমি অবাক হবে আমি চিঠি লিখেছি দেখে। সব কথা এখন আর মুখে বলতে পারা যায়না। ফোন করলে কুশল বিনিময়ের পর কথার থেকে দীর্ঘশ্বাসের আদান-প্রদান হয় বেশি। বিদেশে চাকরি নিয়েছি বলে, তিন বছর বাড়ি ফিরতে পারিনি বলে তোমার অনেক অভিমান জমে আছে। কি করব বলো উপায় ছিলনা। কঠিন পরিশ্রমের পরেও কিভাবে অযোগ্যদের কাছে হেরে গিয়েছিলাম জানোই তো? তবে এবারের পুজোয় সত্যিই বাড়ি ফিরছি।
এখনো কি শিউলি ফুল কুড়িয়ে আমার টেবিলে রাখো? রতন জেঠুর প্রতিমা গড়া বোধহয় শেষের দিকে। পূজাবার্ষিকী কিনেছ? এবছর টাকা একটু বেশি পাঠালাম। নতুন জামা কিনতে না পারা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে যে!
রিমির বিয়ে ঠিক হয়েছে আগে বলনি কেন? ওইটুকু মেয়ে, এত ভালো পড়াশোনায়। সন্ধ্যা দিদির মতো শ্বশুর বাড়ির যাঁতাকলে স্বপ্নদের পিষে মারতে আর দেওয়া যাবেনা। বাড়ি ফিরেই আমি ওর বিয়ে ভাঙবো। তুমি একটু কাকুকে বোঝাও। প্রতিমার অকালবোধন হোক কিন্তু অকাল বিসর্জন যেন কোনভাবেই না হয়।
ঠিক করেছি এবার চিরকালের জন্যই দেশে ফিরব। জানি ভালো থাকার উপকরণ কম হবে তবু ফিরব। সমস্যার মধ্যে না থাকলে সমস্যার সমাধান করা যায়না। বাধাগুলোকে সর্বোচ্চ চেষ্টার মধ্য দিয়ে সরাতে হবে। যা কিছু চেষ্টায় সফল হবেনা তা প্রার্থনায় থাকবে মায়ের পায়ে।
কেন জানিনা এক মন ভালো করা আলো আমায় জড়িয়ে থাকছে সারাক্ষণ। সকলের মঙ্গল কামনা করতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে এই উৎসবের আলোয় মুছে যাক পৃথিবীর সব অন্ধকার। কাশফুলের মতো সাদা ভাত পৌঁছে যাক সর্বহারাদের ঘরে, সবার ভালো হোক, অভয়ারা বিচার পাক।
ইতি
তোমার খোকা
ঊর্মিতা বিশ্বাস
কোলকাতা
০৬/০৯/২৫
সুপর্ণ,
কেমন আছো তুমি? আমার শেষ চিঠির উত্তর পাইনি অনেক মাস হয়ে গেল। সব ঠিক
আছে তো ওখানে?
জানো, কাল রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখেছি। এখনো সেই ঘোরেই আছি, কাজে মন
নেই।
ষষ্ঠীর সকাল। আমি তোমার পছন্দের ওই স্নিগ্ধ সাদা রঙের কুর্তিটা পরেই রওনা
দিলাম তোমার বাড়ি। তুমি বোধহয়, পুজোয় বাড়ি ফেরার আগেই তোমার সব পুরোনো
ছাত্র-ছাত্রীরা খবর পেয়ে গিয়েছে। পৌঁছে দেখি, ওরা সব তোমার সাথে গল্পে মশগুল।
ওদের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে, ওদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা আর তার সাথে সাথে
পুজো পরিকল্পনা নিয়েও। তোমার ইউনিভার্সিটি, ওখানের ল্যাব, গবেষণা, পেটেন্ট,
ফান্ডিং নিয়ে কত কি যে আলোচনা চলছে! সাথে তোমার দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর
নানান গল্প। সব নিয়ে আসর জমজমাট। আমি তখন সবে পৌঁছেছি, আমায় বসতে বলে
খাবার আনতে গেলে। ওমা! পাঁচ মিনিটে হাজির তুমি। পাড়ার দোকানে নাকি সব বলেই
রেখেছিলে। বিশু দা এসে দিয়ে গেলো নিচে। সবার জন্যে পরোটা আর জম্পেশ আলুর
দম। একে একে ওরা সব বেরিয়ে গেলে তুমি-আমি মিলে বাইকে চেপে বেরোলাম। তুমি
বললে সারপ্রাইজ আছে, প্রশ্ন করিনি। গল্পের স্রোতে ভেসে হঠাৎ দেখি পৌঁছে গিয়েছি
আমার একেবারে ছোট্টবেলার পাড়ায়। সেই বাড়ির সামনের পুজোর প্যান্ডেল, বাইক
থেকে নেমে দাঁড়ালে তুমি। তোমার আঙুল ছুঁয়ে এগিয়ে গেলাম প্যান্ডেলের দিকে…
ভুল টিউবে ভুল কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট দিয়ে ফেলেই হুঁশ ফিরতে বুঝলাম ল্যাবে
এক্সপেরিমেন্টের বারোটা বেজে গিয়েছে।
কোথায় তুমি! তুমি হয়তো এ বছরেও বাড়ি ফিরবেনা পুজোয়। সত্যিই কি আসবেনা?
আর দিন পনেরো পর মহালয়া। এখনো তো সময় আছে সারপ্রাইজ দেওয়ার। জানিনা,
চিঠি কবে পৌঁছবে তোমার কাছে। তবু…
এবার পুজোয় শুনছি নাকি বৃষ্টি হতে পারে। মনে পড়ে উনিশের সেই সপ্তমী? সেই
বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে ঠাকুর দেখা। মায়ের নতুন শাড়ী ভিজে একাকার। বাড়ি ফিরে
সেদিন রাতে আমরা “The Notebook” দেখেছিলাম।
পরের বছরের সেই দুর্ঘটনার পর তুমি আর একবারও বাড়ি ফেরোনি। জানি,
এলোমেলো ঘর, জীবন, এত স্মৃতি, স্নেহ… সেই ঘর আর আগের মতো নেই। তুমি
ফিরলেও ফিরবেনা সেসব আর।
বোনকে ছাড়া ওই ঘর, পুজো কিচ্ছু এক নয় আর। কাকু কাকিমা বারবার বললেও
কখনো জোর করিনি আর তোমায়। ওনারা অপেক্ষা করেন তোমায় অন্ততঃ একবার
দেখার। আর আমার তো সে জোরও নেই বলার।
পুজোর দিনগুলোয় ভীষণ মনে পরে সেই তোমার সাথে অলিগলি ঘুরে ঘুরে শোনা
সেসব জায়গার ইতিহাস, কতশত বছরের বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিবৃত্ত। তুমি বলতে
আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম তোমায়।
ইতিহাস নাহয় তোলা থাক, তুমি এলে দু’দণ্ড বরং বসবো কোথাও নির্জনে। শুনবো, তুমি
যা যা বলতে চাও।
হয়তো তুমি এই চিঠি পাবে পুজোর আগেই। সেইন নদীর পাশে বসে লিখবে আমায়,
“না রে, পুজোয় ঘরে ফেরা হবেনা আমার আর। অন্য কোনো সময়…”।
জানিনা, কবে ফিরবে তুমি। জানিনা আদৌ ফিরবে কিনা…
ভালো থেকো।
ইতি,
মারিয়ানা
বাংলায় পটচিত্রে দেবী আরাধনা
দেবজ্যোতি সিংহ রায়
প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাচীন ধারা বহন করে চলেছে পটচিত্র। ভারতীয় ইতিহাসের গোড়ার দিকে বিভিন্ন অংশের পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক ভট্টাচার্য তাঁর ‘ বাংলার চিত্রকলা ‘ বইতে লিখেছেন ” বুদ্ধদেব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে স্বয়ং যে ‘ চরণচিত্র ‘ -এর প্রশংসা করেছিলেন, তা ছিল পরবর্তীকালের পটচিত্রেরই পূর্বসূরি “। এছাড়াও প্রাচীন পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় বাণভট্ট রচিত ‘ হর্ষচরিত ‘ গ্রন্থে।
পটচিত্র শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই সংস্কৃত শব্দ ‘ পট্ট ‘ থেকে এসেছে, শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো কাপড়। কাপড়ের উপর তুলি দিয়ে রং সহযোগে আঁকাই হল পটচিত্র। এই পটচিত্র যারা আঁকেন তাদের প্রধানত পটুয়া বলেই আখ্যায়িত করা হয় আবার বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে তাদের বিভিন্ন নাম, যেমন-পইটিকা,পট্টীকার,চিত্রকর, পটেরী ইত্যাদি। এই
পটুয়ারা পটচিত্র এঁকে সেই চিত্রের উপর ভিত্তি করে গান রচনা করেন এবং জীবিকা নির্বাহ করেন। শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিকের লেখা ‘ প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা ‘-বইয়ে ‘ পট-পটুয়া পাঁচালী ‘ অংশের বিভিন্ন জায়গায় ধরা দিয়েছে।
পটচিত্রে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে চৈতন্যলীলা, কৃষ্ণলীলা, মহাভারত, রামায়ণ, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গলের কাহিনী। তেমনই একাধারে উঠে এসেছে গাজী পীর এবং তার বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই বিভিন্ন পটচিত্রে উঠে এসেছে লৌকিক অলৌকিক দেব-দেবী, সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী,পশুপাখি ইত্যাদি। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে চোখে পড়ে রামের দুর্গা বন্দনার পটচিত্র।
এই পটচিত্রে আঁকা দেব-দেবী কখনো থেকে গেছেন সৌখিনতার আড়ালে কিংবা মিউজিয়ামে ফ্রেমবন্দী হয়ে আবার কখনো কখনো পটচিত্রের দেবীরাই উপবিষ্ট হয়ে বসেছেন পূজার আসনে। বর্তমান বাংলায় জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গোৎসব থেকে বিভিন্ন পুজোর মাঝেও বিশেষ কয়েকটি মাত্র জায়গায় এখনো পূজিত হন দেবী পটচিত্রে। পটচিত্রের পূজার সম্ভাব্য তিনটি দিক উঠে আসতে পারে। প্রথমত, যখন মূর্তি পূজার চল ছিল না তখন থেকেই পটচিত্রে পূজা হয়ে আসছে এবং বর্তমানেও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। দ্বিতীয়ত, সামর্থের অভাবে মূর্তিপূজার বদলে পটচিত্রে পূজা এবং তৃতীয়ত,প্রচলিত একটি মিথ রয়েছে পটকে পূজা করলে রোগমুক্তি এবং মনস্কামনা দ্রুত পূরণ হয়।
বর্তমান বাংলায় পটচিত্রে দেবী দুর্গা পূজিত হয়ে আসছেন বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গায়। তারমধ্যে অন্যতম এবং উল্লেখযোগ্য বর্ধমান রাজবাড়ি। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে সম্ভবত তৎকালীন রাজা মহাতাব চাঁদ পটেশ্বরী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। পটের দিকে তাকালে চোখে পড়ে দেবীর বাহন সিংহের বদলে ঘোড়ার মুখ। পটেশ্বরী দুর্গা পূজিত হন লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরে। কথিত আছে রাজবাড়ীতে নারায়ণ শিলা থাকার কারণে মূর্তিপূজা করা হতো না, সেই থেকেই পটচিত্রে দেবীর আরাধনা প্রচলিত। রাজবাড়ির পুজোর ভোগেও বিশেষ রীতি আছে, এখানে খিচুড়ির বদলে ছোলা, পুরী এবং হালুয়া দেওয়া হয়।
পটচিত্রে দেবী আরাধনার অন্যতম নিদর্শন হলো জামকুড়ির মহামারী পট। মল্লরাজাদের একাংশ বসবাস করেন বাঁকুড়ার জামকুড়ি রাজবাড়িতে। এখানে দেবী রাজরাজেশ্বরী নামে পরিচিত। দেবীকে প্রতিদিন মৃন্ময়ী রূপে পূজা করা হলেও দুর্গাপূজার সময় দেবী পূজিত হয় পটচিত্রে। সম্ভাব্য রাজা দামোদর সিংহের আমলে কলেরা নামক মহামারী দেখা যায়,রাজা স্বপ্নে দেবীর দর্শন পান। সেই থেকেই পূজিত হয়ে আসছেন জামকুড়ির মহামারী পট। নবমী রাতে বিশেষ রীতি অনুযায়ী লোকচক্ষুর আড়ালে দেবী পূজিত হন। রাজ পরিবারের সদস্য ও ঢাক বাদক ছাড়া সেখানে কেউ উপস্থিত থাকেন না। এই দেবীর প্রসাদ রাজ পরিবারের সদস্য ও মহাযাজক ছাড়া খাওয়ার অধিকার নেই। বর্তমানে রাজ পরিবারের অনুরোধে পটচিত্রটি পুনর্নির্মাণ করেন শিল্পী কৃপাময়ী কর্মকার। এখন এই পটচিত্রেই দেবীর আরাধনা হয়ে চলেছে।
এছাড়াও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে শাঁখারী বাজারের মল্লরাজ পরিবারের কুলোদেবী মৃন্ময়ীর পূজা পটচিত্রে প্রায় হাজার বছর ধরে চলে আসছে। বংশ পরম্পরায় ফৌজদার পরিবার বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ পরিবারের পটচিত্র আঁকেন। তিনটি পট পূজিত হন, তারা যথাক্রমে বড় ঠাকুরানী, মেজ ঠাকুরানী এবং ছোট ঠাকুরানী নামে পরিচিত।
পটচিত্রে দেবী আরাধনার নিদর্শন পাওয়া যায় পঁচেটগড় রাজবাড়ীতেও। প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছরের রীতি মেনে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী। রাজ পরিবার প্রথমে শৈব থাকায় শুরু হয় দেবী আরাধনা, প্রথমে মূর্তিপূজা হলেও পরবর্তীতে রাজপরিবার বৈষ্ণব হয়েছে এবং সাথে সাথে বন্ধ হয় মূর্তিপূজো। তৎকালীন সময় থেকেই শোলা ও পটে আঁকা পটচিত্রে দুর্গাপূজার সূচনা।
এভাবেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্যের দুর্গা পুজোর সাথে মিলেমিশে গেছে প্রাচীন বাংলার আরেক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পটচিত্র।
তথ্যসূত্র –
১. বাংলার চিত্রকলা – অশোক ভট্টাচার্য
২. প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা – শ্রী শ্রীহর্ষ মল্লিক
৩. নগর বর্ধমানের দেবদেবী – নীরদবরণ সরকার
৪. ” জামকুড়ি মহামারী পট ” (পেজ bankura )8- 28 September,2024
৫.”৪৫০ বছর পুরনো রীতি! মূর্তি নয়, পটেই পূজিতা পঁচেটগড় রাজবাড়ির দুর্গা ” (সংবাদ প্রতিদিন.in) – 25 September, 2022
—————————————–