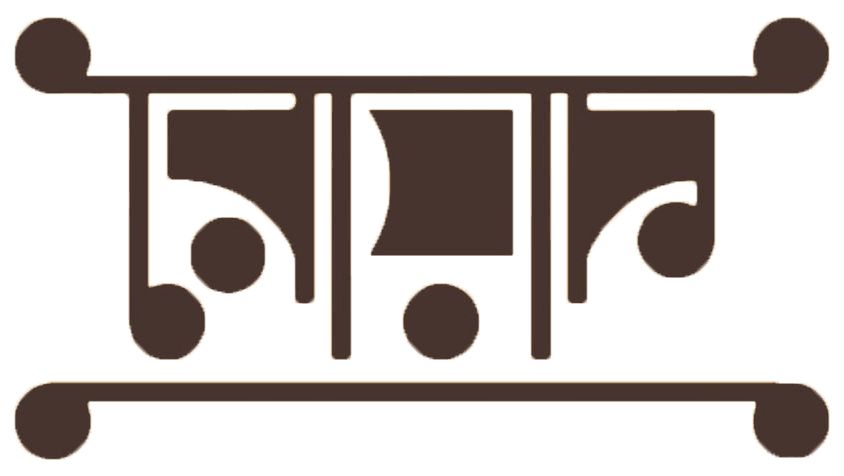দ্বিতীয় বর্ষ ✦ দ্বিতীয় সংখ্যা ✦ সমালোচনা
-
বই
কোনো কিছুই কিছু না – উডি আ্যালেনের আত্ম-জীবনী
শুভদীপ মৈত্র
 বই রিভ্যু নামক জিনিসটা কাঁচা বয়সে করার একটা অহেতুকী উত্তেজনা থাকে, প্রাগ্রসর কোনো লেখকের লেখা নিয়ে নিজের মত সবাইকে জানাচ্ছি ও তার ভাল মন্দের নিয়ামক যেন আমিই এই মজাটা বড় কম নয়, এবং সে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা দরকারিও, যদিও তারপর রিভ্যু করে ব্যর্থ লেখকেরা, তেতোমুখে সাংবাদিক ইত্যাদি ধরনের প্রাণী, আর নয় উপরোধের ঢেঁকি গিলে কেউ – যেমন আমি করছি এখন। বাংলায় পেশাদার সমালোচক হয় না, কালেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লোকে সমালোচক ভাবে, যদিও পেশাদার সমালোচক ব্যাপারটা আলাদা। তা বাংলায় সেটা নেই কেন? এ বিষয়ে আমি খুব জানি তা নয়, জানলেও মুখ খুলব না, মোদ্দা কথা হল সে-সবের অভাবে এই যে লেখাটা লিখছি তা প্রায় কেউই পড়বে না আমি নিশ্চিত। একটা ভাল ব্যাপার হল আমার কোনো লেখাই খুব বেশি লোক পড়েটড়ে না, তবু আশা যদি বা থাকে মেরা নাম্বার আয়েগা অন্য লেখার ক্ষেত্রে –এ রিভ্যুয়ে নেই। তাও সম্পাদক ছোকরা মহা আশা নিয়ে বলেছে, ভেবেছে আমি লিখলে দু-একজন পড়তে পারে, আর আমারও একখান বই সদ্য পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে দু-কথা লিখতে পারব তাই শুরু করে দিলাম। বইটি উডি অ্যালেনের আত্ম-জীবনী – অ্যাপ্রপোস টু নাথিং।
বই রিভ্যু নামক জিনিসটা কাঁচা বয়সে করার একটা অহেতুকী উত্তেজনা থাকে, প্রাগ্রসর কোনো লেখকের লেখা নিয়ে নিজের মত সবাইকে জানাচ্ছি ও তার ভাল মন্দের নিয়ামক যেন আমিই এই মজাটা বড় কম নয়, এবং সে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা দরকারিও, যদিও তারপর রিভ্যু করে ব্যর্থ লেখকেরা, তেতোমুখে সাংবাদিক ইত্যাদি ধরনের প্রাণী, আর নয় উপরোধের ঢেঁকি গিলে কেউ – যেমন আমি করছি এখন। বাংলায় পেশাদার সমালোচক হয় না, কালেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লোকে সমালোচক ভাবে, যদিও পেশাদার সমালোচক ব্যাপারটা আলাদা। তা বাংলায় সেটা নেই কেন? এ বিষয়ে আমি খুব জানি তা নয়, জানলেও মুখ খুলব না, মোদ্দা কথা হল সে-সবের অভাবে এই যে লেখাটা লিখছি তা প্রায় কেউই পড়বে না আমি নিশ্চিত। একটা ভাল ব্যাপার হল আমার কোনো লেখাই খুব বেশি লোক পড়েটড়ে না, তবু আশা যদি বা থাকে মেরা নাম্বার আয়েগা অন্য লেখার ক্ষেত্রে –এ রিভ্যুয়ে নেই। তাও সম্পাদক ছোকরা মহা আশা নিয়ে বলেছে, ভেবেছে আমি লিখলে দু-একজন পড়তে পারে, আর আমারও একখান বই সদ্য পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে দু-কথা লিখতে পারব তাই শুরু করে দিলাম। বইটি উডি অ্যালেনের আত্ম-জীবনী – অ্যাপ্রপোস টু নাথিং।
বার্নার্ড শ একবার লিখেছিলেন সমস্ত আত্মজীবনীই হল ঢপ, অসেচতন ঢপ নয় জেনে বুঝে মিথ্যে কথা লেখা। এখন শ-সাহেবের কথাটা মেনে নিই বা না নিই আত্মজীবনী ব্যাপারটা পড়তে মন্দ লাগে না যদি সে লেখা হয় রসিকের। অবশ্যই আপনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আমার জীবনই আমার বাণী মার্কা যত ছোটদের নিমপাতা গেলানো আত্মজীবনী যদি পড়ে থাকেন তাহলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হতে পারে আত্মজীবনী কেউ ওয়ার্ল্ড কাপে মেসি বনাম রোনাল্ডো বা নতুন বেরনো দীপিকা পাড়ুকোনের সিনেমা ফেলে পড়তে পারে – কিন্তু তা সম্ভব। বিশেষ করে বইটির লেখক যদি হয় উডি অ্যালেন ও লেখার ঢং অননুকরণীয় উডি। তার কারণ উডি অ্যালেন শুধুমাত্র একজন সিনেমা-পরিচালক নন, একজন কমপ্লিট এন্টারটেইনার – এমন একজন চ্যাপলিনের পর আমেরিকায় বিরল। আপনারা যারা উডি অ্যালেনের সিনেমা দেখেছেন তাঁরা জানেন উডি কীভাবে একইসঙ্গে সিরিয়াস কথার সঙ্গে গেঁথে দেন একেবারে ব্যক্তিগত একসেন্ট্রিসিটি, কীভাবে কোনো সিরিয়াস বিষয় হয়ে ওঠে ফ্রিভোলাস, ফ্রিভোলাস হয়ে ওঠে সিরিয়াস, এ ব্যাপারটা সবার হজমের নয় – বিশেষত বাংলায় একে সিরিয়াস শিল্প হিসেবে ধরতে টরতে কেউ পারে না, লেখক-শিল্পী ইত্যাদি মহা স্ট্রাগল করে মরে-টরে না গেলে এবং দাঁতে-দাঁত-চেপা দুঃখ দুর্দশার কথা ও আগামীর বৈপ্লবিক ভোরের কথা না লিখলে তাকে ভাঁড় ছাড়া খুব কিছু ভাবা হয় না, এমনকি মুজতবা আলীর মতো লেখকও তাই রম্য রচনার লেখক হিসবে পরিচিত থাকেন – এ হেন পরিস্থিতিতে উডি অ্যালেন-এর বিশাল সংখ্যক দরদী দর্শক এখানে থাকবে মনে হয় না, যদি বা থাকে তারা বাংলা ভাষা পড়েনটরেন বলে মনে করি না, বাংলা অর্নাস ছাড়া কারাই বা পড়তে যাবে এ-সময়ে, সে যাই হোক যদি উডির সিনেমা-রসিক কেউ এই লেখাটা পড়তে থাকেন তো বলি এ একেবারে কুইটিসেনশিয়াল উডি অ্যালেন। চ্যাপলিনের আত্মজীবনী পড়ে সত্যজিৎ রায়ের ভাল লাগেনি, ওঁর মনে হয়েছিল চ্যাপলিন প্লেইং টু গ্যালারি করছেন শেষের দিকে, যেখানে উনি চ্যাপলিন হয়ে উঠেছেন তারপর শুধু সেই কার সঙ্গে কী কথা হল তার বর্ণনা। কথাটা অমূলক নয়, এবং সেই ফাঁদ থাকেই যে সাফল্যের পর একটা সেলিব্রিটি গোষ্ঠিতে আপনে-আপ লোকজন চলে যায় ও তা নিয়ে কথাও বলেন। উডির ক্ষেত্রে সেটা প্রথম থেকেই হতে পারত, উডি সেটার বাইরেও বেরননি, কিন্তু যেটা করছেন তিনি তার আশপাশের মানুষগুলোকে নিয়ে লিখেছেন যে স্বরে তাঁর প্রতিবিম্বরা সিনেমায় কথা বলে। ফলে সে তাঁর ডায়নি কিটনের সঙ্গে প্রেমই হোক আর প্লে বয়ের মালিক হিউ হেফনারের সঙ্গে যোগাযোগ সবই এত মজার ঢঙে লেখা যে পড়তে পড়তে মনে হয় না যে আপনি যে চরিত্রগুলোর কথা শুনছেন তাঁরা বিশ শতকের দুনিয়া কাঁপানো নাম। কারণ উডির মতে তার কিছু এসে যায় না, যেমন অস্কার পাওয়ার দিন তিনি কোডাক থিয়েটারে না গিয়ে নিজের বাড়িতে বসে কাজ করেন ননচ্যালান্টলি ঠিক তেমনি, ওই যে বইটার নাম দিয়েছেন অ্যাপ্রোপস টু নাথিং।
তার মানে এই নয় যে বইটা স্রেফ ভাঁড়ামো, বরং মার্কিন মুলুকের কমেডি ও তার নানা ধারা উপধারা সম্পর্কে এই বই থেকে আভাস পাওয়া যায়, ফলে উডির সিনেমা-রসিকরা আরেকটু বেশি রিলেট করতে পারবেন তাঁর ছবির নানা চরিত্রের সঙ্গে, তাদের পশ্চাৎপট সম্পর্কে আরেকটু পরিষ্কার ধারণা হবে। জ্যাজ মিউজিকে শখ যাদের রয়েছে তাদের পাঁচের দশকের নিউ ইয়র্কের জ্যাজ ও ব্লুজ সিন সম্পর্কে বেশ কিছু অজানা তথ্য হাতে আসবে বইটা পড়লে। আর অবশ্যই সিনেমার কথা। আমেরিকা ইজ ইক্যুয়ালটু হলিউড যারা মনে করেন না অথচ সারাক্ষণ গ্যোদার-ট্রুফো-ভনট্রায়ার দেখে নখ কামড়াতে চান না তাদের জন্য এ বই অপরিহার্য্য। যারা নিউ ওয়েভের দু-একটা নাম বাদেও এর্যিক রোমার দেখেছেন, যারা সাং-সু-হং দেখে আনন্দ পান উডি অ্যালেন তো তাদের জন্য, তাঁর এই সিনেমা নামক এক খামোখা দৈত্যকে অছেদ্দা, তাঁর চিন্তাশীল ও কৌতূহলী মাথা যা সারাক্ষণ প্রশ্ন করতে থাকে ও সেই সব বিপ্রতীপ ভাবনাকেই কোনো একট শিল্প মাধ্যমে ধরতে চায় – তাই একটা অশেষ কথোপকথন চলে সিনেমায়, টুকরো ভাঙা কথার পিঠে কথা, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারা মানুষের অনেক কথা থাকে, সেগুলোকে ক্যালাইডোস্কোপের মতো নেড়েচেড়ে দেখার নামই শিল্প। না হলিউডি গ্ল্যমার না মাথাটনটনে আর্ট ফিলম – এই দুয়ের হাস্যকর চরমপন্থাকে কখনো ঠুকে, কখনো পাত্তা না দিয়ে, স্রেফ একটা মজলিশি আনন্দে গল্প বলার মজায় উডির মতো মানুষের আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখেন। একুশ শতকে এসে আমরা বুঝে গেছি কোনো বিশাল তত্ত্ব বা আদর্শ নয় বরং আমাদের খণ্ডিত সত্ত্বাই বেশ মাজাদর এবং সে নিয়ে খুশি থাকা ঢের ভাল। ফিডেল কাস্ত্রো, পিনোচেট বা ইদি আমিন কোনোটাই খুব ভাল ব্যাপার নয় এবং সে-সবের বদলে বরং উডির নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, খানিক হ্যালভ্যালে খানিক বিরক্ত নিউ-ইয়র্কার ঢের ভাল এ আমরা বুঝে গেছি যারা এ বই তাদের জন্য। আর সত্যি বলতে কী আমার এই প্রায় হাজার খানেক শব্দ খরচ করে লেখাটা যারা পড়ে ফেললেন, আমার মন বলছে তাঁরা উডির বইটাও কোনো না কোনোদিন ঠিক পড়বেন। যদি বা নাও পড়েন ক্ষতি নেই এই লেখা থেকে গোল গোল করে বলে দিলে আপনি বইটা পড়েছেন আপনার আঁতেল বন্ধুরা ধরে নেবে।
-
সিনেমা
বায়োস্কোপ
গৌরব রায়
সিনেমা – “অনন্ত”
পরিচালক -অভিনন্দন দত্ত
অভিনয় -ঋত্বিক, সোহিনী, আমিত, অনিন্দ্য , কৌশিক
‘অনন্ত’ সিনেমা আসলে এক দৃশ্যকাব্য।Poetry in motion।এই চলচ্চিত্রের শুভ (ঋত্বিক) একজন লিরিক্যাল মানুষ।এই ছবি আসলে একটা মুহূর্তকথন ,একটা অভিজ্ঞতা।এই ছবির ট্রিটমেন্ট আপনাকে মনে করিয়ে দেবে “আসা যাওয়ার মাঝে” বা ওং কার অয়াই এর In the Mood for Love বা কিম কি দুকের Three Iron” এর পরাবাস্তব লাইন It’s hard to tell that the world we live in is either reality or a dream”
এই ছবি অপেক্ষার কথা বলে।শুভ কে যখন তার বন্ধু জিগ্যেস করে সারাদিন বাড়িতে বসে কি করিস বল তো? তখন সে বলে অপেক্ষা সময়ের অপেক্ষা।এই শুভ অপরাহ্ণের কমলা আলোর জন্যে অপেক্ষা করে।সেই আলোপথ জুড়ে মিষ্টু (সোহিনী) হেঁটে আসে গলি দিয়ে।সেও একবার অফিস যাওয়ার পথে চোখ তুলে তাকাবে তখনই শুভ চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াবে।কখনও দেখা হবে কখনও হবে না।
একটা ঘোরানো সিঁড়ি নেমে যাবে যেদিন ওদের দেখা হবে সেদিন আলোটা খানিক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।মিষ্টুর ঠিকানা জানতে চাইলে
সে বলবে রোরো নদী।শুভ বলবে সেটা কোথায় মিষ্টু বলবে খুঁজলেই ঠিক পাওয়া যাবে সেই প্রিয় পিনকোড।শুভ তার মায়ের মারা যাওয়ার পর একাকিত্ত্বে ভোগে সেখান থেকে মুক্তি খোঁজে।আর মিষ্টু তার মাতাল বাবার ভাতের থালা দিনের পর দিন সাজিয়ে অফিস যাওয়ার ক্লান্তি থেকে মুক্তি অপেক্ষায় থাকে।শুভর সংলাপ আসলে একাকিত্ত্বের সাথে,চায়ের কাপ,কেটলি,গাছেদের সাথে।মায়ের শাড়ির আঁচলের জলের দু এক ফোঁটা কখন তার নিজের চোখের জল হয়ে গড়িয়ে যায়।এই ছবিতে চায়ের কাপ,বিকেলের আলো,জানলা,ট্রেনের শব্দ,ট্রামের শব্দ,ঘরের মেঝে এগুলোও যেন শুভ মানে ঋত্বিক এর পার্শ্বচরিত্র হয়ে ওঠে।
এই ছবি আসলে অপেক্ষার চিত্রকল্প।যে অপেক্ষা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি।যেন “Waiting for Godot” সময়ের রঙ সুর ছন্দের সিম্ফনির নির্মাণ ও বিনির্মাণ চলে সারা ছবি জুড়ে।এক ফালি আলো ফেড ইন আর ফেড আউট বা কখনও কিয়ারোস্কুরো (Chiaroscuro) ব্যবহার আলাদা মন্তাজ তৈরি করেছে সারা ছবিতে। নিজের মত করে মুক্তি খোঁজার পাসওয়ার্ড এই ছবি।
তবে এই ছবি Target Audience আলাদা।মাঝে মধ্যে স্লো মোশন ক্যামেরা আপনার ধৈর্যর পরীক্ষা নেবে।আর মাত্র কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহেই ছবিটি চলেছে এই ছবি।“বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান” বলার মত সময়ে অভিনন্দন বাবু যে এই ছবি বানিয়েছেন তাঁর জন্যে সত্যি তাঁকে অভিনন্দন ও কুর্নিশ।
“আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়/দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার… আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভরে গেছে” তাদের এই ছবি।এই ছবি আসলে উত্তর কলকাতার গলি,নক্সা কাটা জানলা,আহিরিটোলা ঘাট,চক্ররেল স্টেশন আর মনকেমনকে;যারা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি যারা Moonstruck তাদের লেখা চিঠি।